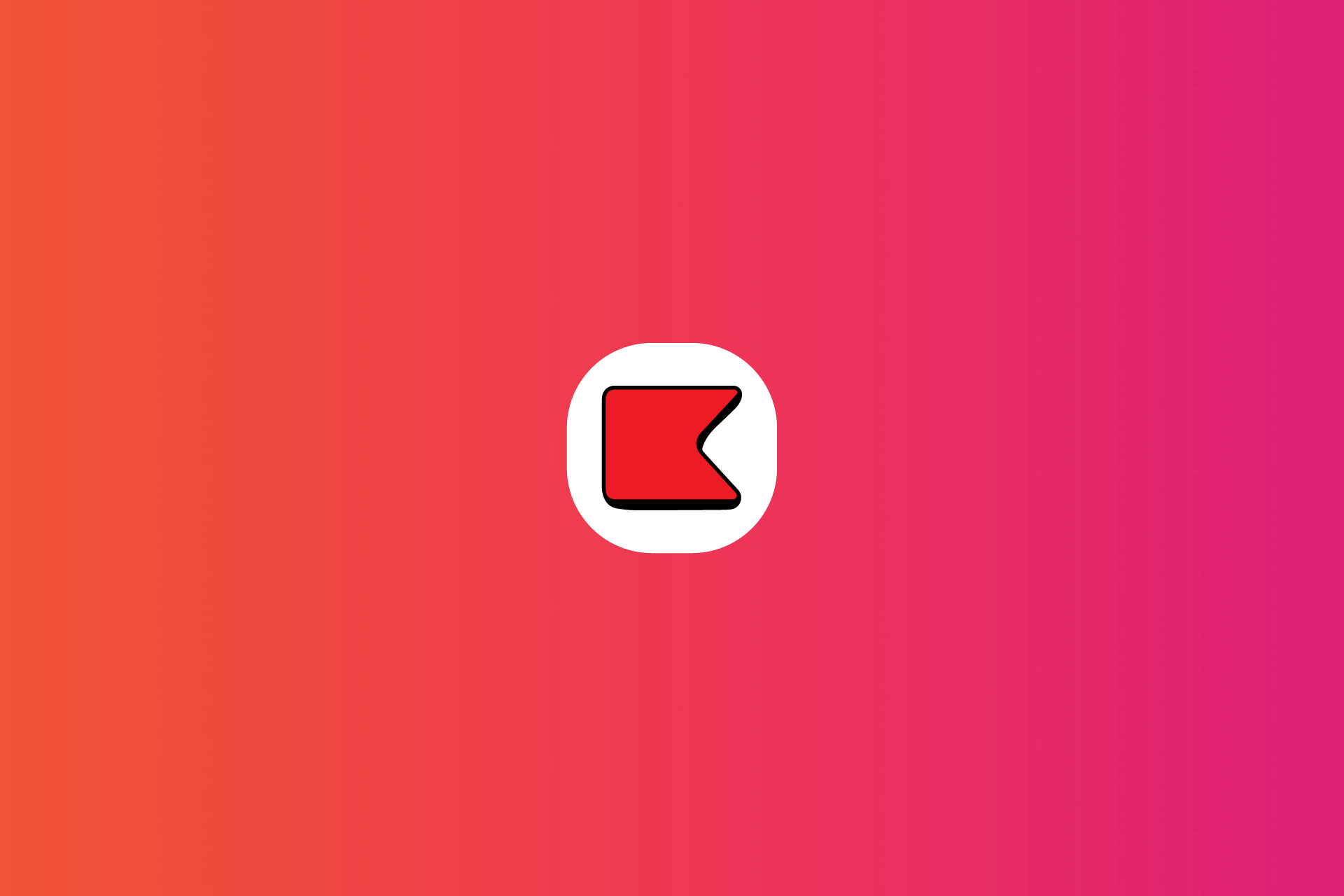book
-
সম্পাদকমহাশয়-সমীপেষু–
ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারি না, আপনারা এখনো লিখিতে শিখেন নাই। অমন মৃদুসম্ভাষণে কাজ চলে না। গলায় গামছা দিয়া লোক টানিতে হইবে। কিন্তু উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ বলিয়া আমাদের এজেন্সি আপিস হইতে একটা লেখার নমুনা পাঠাইতেছি। পছন্দ হইলে ছাপাইবেন, দাম দিতে ভুলিবেন না। যিনি লিখিয়াছেন তিনি সাহিত্যসংসারে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। বাঙ্গালার ভূগোলে সাহিত্যসংসার কোথায় আছে ঠিক জানি না ; এই পর্যন্ত জানি, আমাদের বিখ্যাত লেখককে তাঁহার ঘরের লোক ছাড়া আর কেহই চেনেন না। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, সাহিত্যসংসার বলিতে তিনি, তাঁহার বিধবা পিসি, তাঁহার স্ত্রী এবং দুই বিবাহযোগ্যা কন্যা বুঝায়। এই ক্ষুদ্র সাহিত্যসংসারটির জীবিকা
-
১প্রাচীন ভারতে গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ওঅক্সিজেন বাষ্পের কী নাম ছিল
বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে একেবারেই এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ছিল না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। প্রকৃত কথা, আধুনিক ভারতে অনুসন্ধান ও গবেষণার নিতান্ত অভাব। বর্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠকেরা দেখিবেন, আমাদের অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই এবং তাহাতে যথেষ্ট ফললাভও হইয়াছে।
প্রাচীন ভারতে গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কী নাম ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার পূর্বে কীট্টকভট্ট ও পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের জীবিতকাল নির্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক।
প্রথমত, কীট্টকভট্ট কোন্ রাজার
-
দেখো দেখো, পিঁপড়ে দেখো! খুদে খুদে রাঙা রাঙা সরু সরু সব আনাগোনা করছে—ওরা সব পিঁপড়ে, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্ছি ডেঞে, সমুচ্চ ডাঁইবংশসম্ভূত, ঐ পিঁপড়েগুলোকে দেখলে আমার অত্যন্ত হাসি আসে।
হা হা হা, রকম দেখো, চলছে দেখো, যেন ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে; আমি যখন দাঁড়াই তখন আমার মাথা আকাশে ঠেকে! সূর্য যদি মিছরির টুকরো হ ' ত আমার মনে হয় আমি দাঁড়া বাড়িয়ে ভেঙে ভেঙে এনে আমার বাসায় জমিয়ে রাখতে পারতুম। উঃ, আমি এত বড়ো একটা খড় এতখানি রাস্তা টেনে এনেছি, আর ওরা দেখো কী করছে–একটা মরা ফড়িং নিয়ে তিন জনে মিলে টানাটানি করছে। আমাদের মধ্যে এত ভয়ানক
-
আর কিছুই নয়, মাসিক পত্রে একটা ভারি মজার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পড়িয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তো হাসিয়াছিলই, আবার শত্রুপক্ষও খুব হাসিতেছে।
অষ্টপাইকা, সাপ্টিবারি ও টাঙ্গাইল হইতে তিন জন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন প্রবন্ধটির অর্থ কী। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভদ্রতা করিয়া অনুমান করিয়াছেন ইহাতে ছাপাখানার গলদ আছে; আর-এক জন অনাবশ্যক সহৃদয়তাবশত লেখকের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে উৎকন্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন; তৃতীয় ব্যক্তি অনুমান এবং আশঙ্কার অতীত অবস্থায় উত্তীর্ণ, বস্তুত আমিই তাঁহার জন্য উৎকন্ঠিত।
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি পাল হবিগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন—
‘গোবিন্দবাবুর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কী? ইহাতে কি ফরাসডাঙার তাঁতিদের দুঃখ ঘুচিবে? দেশে যে এত লোককে খেপা কুকুর কামড়াইতেছে এ প্রবন্ধে কি তাহার কোনো প্রতিকার কল্পিত হইয়াছে?’
-
“আমার জীবনই আমার সাহিত্য।”—তুর্গিয়েনে
যে সমস্ত প্রতিভাধর সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারে রুশ জাতীয় সংস্কৃতির গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তুর্গিয়েনেফ। লেনিন এঁকে “স্বনামধন্য রুশ লেখক” বলে অভিহিত করেছেন।
সামন্ত-ভূমিদাস প্রথা থেকে বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে এক বিরাট পটপরিবর্তন হল, সেই এক সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের রুশ জনজীবনের সার্থক প্রতিফলন দেখা যায় তুর্গিয়েনেফ-এর রচনায়। এই বিরাট শিল্পী-রিয়ালিস্ট রুশ সমাজ-আন্দোলনের যে সব উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন তাদের সঞ্চারকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ‘ছাত্র-চক্র’ থেকে শুরু করে ১৮৭৪-১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ‘জনগণের কাছে যাও’ আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ৷
গভীর স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তুর্গিয়েনেফ, এবং তারই উদ্দেশে পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন আপন শিল্পক্ষমতাকে। তিনি বলতেন, “স্বদেশ
-
আমার বিশ্বাস, অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন এমন ব্যক্তির পক্ষে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে যাওয়া নানাকারণেই ঠিক নয়।
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা প্রথমে বিবেচনা করা যাক। মেথোডলজির (Methodological) দিক থেকে, মনে হয়, জ্যোতির্বিদ্যা ও অর্থনীতির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, উভয় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকগণ সন্নিবিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কারের জন্য সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য এমন কতগুলো সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, যাতে বিষয়টা যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু পদ্ধতিগত পার্থক্য থেকেই যায়। পর্যবেক্ষিত অর্থনৈতিক ঘটনাবলী প্রায়শই এমন কতগুলো কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত, যেগুলোর পৃথক পৃথক মূল্যায়ণ প্রায় অসম্ভব। এমন ক্ষেত্রে অর্থনীতির সাধারণ সূত্রাবলীর আবিষ্কার কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, মানব-ইতিহাসের তথাকথিত
-
মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত, কাইয়ুম চৌধুরির আঁকা প্রচ্ছদের এই আত্মজীবনীটি আমাকে একদম শুষে নেবে ভেতরের দিকে, অতোটা আশা করিনি। প্রচ্ছদটি দেখে আমার মন কাড়েনি। কিন্তু ভেতরে যা আছে, তা আমাকে এক অন্যরকম পৃথিবী দেখিয়েছে। একজন নারীর শৈশব, যিনি দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যিনি দেখেছেন সাতচল্লিশের দেশভাগ। যার শৈশব কৈশোর জুড়ে রয়েছে, যশোরের চুড়িপট্টি। নানান বঞ্চনা, গঞ্জনা, অ্যাডভেঞ্চার, আর শেকল ভাঙার নানান ব্যর্থ চেষ্টাসমৃদ্ধ একটা শিশু জীবন।
যে শিশু জীবন দেখেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, হিন্দু বাঙালির দেশ ছাড়ার মিছিল। বাঁশের সাঁকোর মতো নড়বড়ে একটা শৈশব-কৈশোর, ভয়ে ভয়ে পার করে হয়ে উঠেছেন যুবতী। আনোয়ারা সৈয়দ হকের শৈশবের আকর্ষণীয় দিকটি হচ্ছে,
-
আমার মনের প্রান্তে তুমি হবে পল্লবপ্রচ্ছন্নশাখাশস্যের মঞ্জরী, আমার প্রাণের বৃত্তে করবীলাঞ্ছনআনত পুষ্পের ভার নিয়ে এসো তুমি। সোনাবালু ঢাকাএ প্রাণ ব্যর্থ হবে তা না হলে, তা না হলে অগণনপাপড়ি খুলে খুলে আকাশ ছড়িয়ে দিলেআশ্বিনের নীলকান্তচ্ছটা, তোমার আমার মাঝে সেতুবন্ধগানের রচনা হবে না; বিশ্বাস দেবে না কেউ জীবনে নিখিলে।তুমি দাও সৃষ্টির প্রেরণা, দাও মৃত্যু, অকরুণ অসহ্য দ্বন্দ্ব!
তুমি হবে শস্যের মঞ্জরী, আনত পুষ্পের ভারকরবীলাঞ্ছন। আমি তাই প্রতিদিন কৃষকের মতোএ প্রাণ করেছি ছিন্ন হালের আঘাতে। করেছি তো অঙ্গীকারচৈত্রের চণ্ডাল সূর্য, বন্যার হাহাকার। তুমি আছো রতআমার রক্তের স্রোতে শিকড়ের জিহবা মেলে দিয়ে রাত্রিদিনঅশ্রান্ত শোষণে, আমার মৃত্যুতে উদ্ভিন্ন মঞ্জরী তোমার হবে মৃত্যুহীন।
মৃগাঙ্ক রায়
পরিচয়
-
সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের দিন থেকে এই বিশ বছরে মহাকাশ-বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণে মহাকাশকে বাস্তব কাজে ব্যবহারের দিকে এগিয়েছে। মহাকাশযুগের যে তৃতীয় দশক সবে শুরু হয়েছে তাতে এই ঝোঁক বাড়বে। বর্তমানে মহাকাশকে, শুধুমাত্র গবেষণার বস্তু হিসেবেই দেখা হয় না। মহাকাশকে দেখা হয় এক অনন্য প্রয়োগ বিদ্যাবিষয়ক পরিমণ্ডল হিসেবে, আমাদের গ্রহ ও তার সম্পদের অনুসন্ধান এবং অধিক থেকে অধিকতর কর্মক্ষম প্রয়োগবিষয়ক পদ্ধতির রূপকরণের সেতুফলক হিসেবে দেখা হয় মহাকাশকে।
সমস্ত দেশ এবং জাতির পক্ষেই বহির্বিশ্ব প্রয়োজনীয়, কিন্তু সবাই-ই অর্থনৈতিক দিক থেকে মহাকাশ অভিযানে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী নয়—তাদের শক্তি এ থেকে অনেক কম। সি. এম. ই. এ-র ছোট ছোট দেশগুলোর কোনোটাই নিজস্ব চেষ্টায়
-
এক যে ছিল রাজা।
তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ-সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল— আসল যে-কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় একমুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে— এক যে ছিল রাজা।
এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, “লেখকমহাশয়, তুমি যে বলিতেছ
-
১
মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।
দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।
যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের
-
আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী দুই শরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ-কখানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।
শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃদ্ধির আর-একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র
Catagory
Tags
- অতিপ্রাকৃত
- অনুপ্রেরণামূলক
- অনুবাদ
- অপরাধ
- অভিধান
- অভ্যুত্থান
- অর্থনীতি
- অলিম্পিক
- অস্ট্রেলিয়া
- অস্ত্র
- আইন
- আইনশাস্ত্র
- আইনস্টাইন
- আত্মউন্নয়ন
- আত্মজীবনী
- আদিবাসী
- আধ্যাত্মিকতা
- আন্দোলন
- আফ্রিকা
- আর্টিস্ট
- আলোচনা
- ইউরোপ
- ইসলাম
- উত্তর আমেরিকা
- উদ্ভাবন
- উদ্ভিদ
- উদ্ভিদবিদ্যা
- উদ্যানচর্চা
- উপকথা
- উপন্যাস
- উপন্যাসিকা
- উৎসব
- এশিয়া
- ওয়ার্ল্ড কাপ
- ওষুধ
- কড়চা
- কথোপকথন
- কবিতা
- কমিক
- কলকাতা
- কল্পকাহিনী
- কল্পবিজ্ঞান
- কারুশিল্প
- কিশোর
- কৃষি
- ক্রিকেট
- খাদ্য
- খুলনা
- খেলা
- খ্রিষ্টান
- গণতন্ত্র
- গণযোগাযোগ
- গণহত্যা
- গণিতশাস্ত্র
- গদ্য
- গদ্যকাব্য
- গবেষণা
- গৃহসজ্জা
- গোয়েন্দা
- গ্যাজেট
- গ্রন্থপঞ্জি
- চট্টগ্রাম
- চলচ্চিত্র
- চিঠি
- চিত্রকলা
- চিরায়ত
- চীন
- ছড়া
- ছাত্র আন্দোলন
- ছোটগল্প
- জলবায়ু
- জাতীয়
- জাতীয়তাবাদ
- জাপান
- জার্মানি
- জীবনী
- জীববিজ্ঞান
- জ্যোতির্বিদ্যা
- ঢাকা
- তথ্যসূত্র
- দর্শন
- দাঙ্গা
- দুর্ভিক্ষ
- দুঃসাহসিক
- ধর্ম
- নজরুল
- নদী
- নাটক
- নাট্যশালা
- নারী
- নারীবাদী
- নির্বাচন
- নৃত্য
- পদার্থবিদ্যা
- পরিবেশ
- পশ্চিমবঙ্গ
- পাকিস্তান
- পাখি
- পুঁজিবাদ
- পৌরাণিক
- প্রতিবেশ
- প্রযুক্তি
- প্রহসন
- প্রাণিবিদ্যা
- ফিচার
- ফিনান্স
- ফুটবল
- ফ্যাসিবাদ
- ফ্রান্স
- বই
- বইমেলা
- বরিশাল
- বাজেট
- বাংলা
- বিজ্ঞান
- বিজ্ঞানী
- বিনোদন
- বিপ্লব
- বিবর্তন
- বিয়োগান্তক
- বিশ্ববিদ্যালয়
- বিশ্লেষণ
- বৌদ্ধ
- ব্যাঙ্গাত্মক
- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন
- ভারত
- ভাষণ
- ভাষা
- ভূগোল
- ভৌতিক
- মধ্যপ্রাচ্য
- মনোবিজ্ঞান
- ময়মনসিংহ
- মহাকাশ
- মহাবিশ্বতত্ত্ব
- মানসিক স্বাস্থ্য
- মার্কসবাদ
- মুক্তিযুদ্ধ
- মুদ্রণ ও প্রকাশনা
- যুক্তরাজ্য
- যুক্তরাষ্ট্র
- যুদ্ধ
- রংপুর
- রবীন্দ্রনাথ
- রমন্যাস
- রম্যরচনা
- রসায়ন
- রহস্য
- রাজশাহী
- রান্নাবান্না
- রাশিয়া
- রূপকথা
- রূপচর্চা
- রেসিপি
- রোজনামচা
- রোমাঞ্চ
- লেখক
- লোককাহিনী
- ল্যাটিন আমেরিকা
- শিল্পকলা
- শিশুতোষ
- শৈলী
- সংঘর্ষ
- সঙ্গীত
- সংবাদ
- সমসাময়িক
- সমাজ
- সমাজতন্ত্র
- সমান্তরাল বিশ্ব
- সম্পাদকীয়
- সরকার
- সাংবাদিকতা
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
- সাম্যবাদ
- সাম্রাজ্যবাদ
- সিলেট
- সুপারহিরো
- সোভিয়েত ইউনিয়ন
- স্থাপত্য
- স্মৃতিকথা
- হিন্দু
Archives
- 2025(72)
- 2024(242)
- 2019(4)
- 2018(1)
- 2017(1)
- 2016(8)
- 2015(7)
- 2014(2)
- 2012(1)
- 2011(1)
- 2010(1)
- 2009(1)
- 2006(1)
- 2005(2)
- 2004(2)
- 2003(6)
- 1999(2)
- 1997(2)
- 1995(1)
- 1990(2)
- 1986(2)
- 1984(3)
- 1981(3)
- 1980(2)
- 1979(1)
- 1978(6)
- 1976(1)
- 1975(25)
- 1971(28)
- 1968(4)
- 1965(17)
- 1963(1)
- 1960(3)
- 1952(3)
- 1951(1)
- 1949(16)
- 1946(15)
- 1945(1)
- 1936(1)
- 1931(3)
- 1904(1)
- 1903(1)
- 1901(1)
- 1892(1)
- 1891(1)
- 1890(1)
Stay Connected
Get Newsletter
Subscribe to our newsletter to get latest news, popular news and exclusive updates.