ঢাকার বুকে
আমরা উঠলুম ৩৬ নম্বর কামিনীভূষণ রুদ্র রোডে, যার পোশাকি নাম চাঁদনী ঘাট। ১৯৪৮-এর ঢাকা। ব্রিটিশ আমলের পুরো গন্ধ তো ছিলই, মোগল আমলের ছিটেফোঁটা লালবাগ, আমলিটোলা, চকবাজার, মোগলটুলি, ইসলামপুর-এসব এলাকার অলিগলিতে যেন বা সেকালও উঁকি মারত। আমাদের এই হিসেবে প্রাউডলকের উদ্যান নগরী শ্যামলী রমনা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এক বিস্ময়। এ কথা বলা যাবে না নবাবি আমলের ঢাকা সম্পর্কে। বিদ্যুতের ব্যবহার তখনো সর্বগামী ছিল না। ফলে সন্ধে নামলেই সেকালের জেলা শহরগুলোর মতোই অন্ধকার নেমে আসত ঢাকার শিরা-উপশিরায়, বাড়ি বাড়ি জ্বলে উঠতো হারিকেন লণ্ঠনের আলো। মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে কোনো কোনো ভাগ্যবানের বাড়ির জানালা গলিয়ে বিদ্যুতের ঝলমলে নরম আলো এসে পড়ত খোয়াভাঙা রাস্তার ওপর। হয়তো গুটিসুটি শুয়েছিল কোনো নষ্টচেতন কুকুর। ভয় পেয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পিটপিট করে তাকাত ওই আলোকচ্ছটার দিকে এবং আশু কোনো আশঙ্কা দেখতে না পেয়ে পৈথানে মুখটি আলতোভাবে রেখে চোখ বুজত আবার। রাত যত গভীর হতো, নাইট শোয়ের যাত্রীদের নামিয়ে ঘরে ফিরত ছ্যাকড়া গাড়িগুলো ছরছর-টগবগ শব্দ তুলে। কোচোয়ানের মুখে হয়তো ফিরছে 'অচ্ছুৎকন্যা'র দেবীকা রানীর গান 'স'বনকে চিড়িয়া বনবন বন্ধুরে' কিংবা কাননের অমর গান 'আমি বন ফুল গো' অথবা 'বসন্ত' কি 'বন্ধন' ছবির চটুল কোনো চরণ। আবার কুমোরটুলি কি সাঁচীবন্দরের হট্টবিলাসিনীদের সঙ্গসুখ ফেরত টুপভুজঙ্গ কেউ টোয়াতে টোয়াতে একবার পড়ছে নর্দমায় তো আরেকবার 'আয় মেরি জান' বলে জড়িয়ে ধরছে ইয়ার-সাঙ্গাতকে কিংবা কোনো নিরীহ পথচারীকে। বওয়াটে পিলইয়ার ছোকরার তাড়ির পেটগোলানো গন্ধে বেচারির বিবমিষার যো-পালাতে পথ পায় না। রিকশাওয়ালা অকারণ ঘণ্টা বাজিয়ে গৃহস্থের শয়নভঞ্জন ঘটিয়ে এবং ওই অতো রাতে 'চিনাবাদাম' বলে শেষ হাঁকটি হেঁকে ঘরে ফিরছে পিচ্চি এক বাদামওয়ালা। পাড়ার যে ভাগ্যিমানের বাড়িতে বেতারযন্ত্র রয়েছে, ভেসে আসছে তারই সুবাদে সেকালের জনপ্রিয় রেডিও সিলোনের কৃপায় শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন মায়াবী রাতে কোকিলকণ্ঠী খুরশিদের তানসেন ছায়াছবির বর্ষার আগমনী গান- 'বরষো বরষো/জোর জোর ঘন ঘোর শোর কর বরষো...।' অদূরে ফাঁড়িতে পেটা ঘণ্টায় যামিনীর দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হতেই পুরবাসীরা নতুন করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিত। জেগে উঠত আজকের মতো মাইকের অসুর ধ্বনিতে নয়, সাদামাটা মিঠে গলায় আজানের বোলে।
আগেই বলেছি, আমাদের তখন চকবাজারের কাছে উর্দু রোডসংলগ্ন চাঁদনীঘাট রোড তথা কামিনীভূষণ রুদ্র রোডে বাড়ি। চাঁদনীঘাট কেন কামিনীর রুদ্র রোষে পড়ে ঘাট মানল, এখন সেই কথা।
মোগল আমল সেটা। নবাব ইসলাম খাঁ চিশতি তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর নিয়োজিত বাংলার প্রথম সুবেদার হিসেবে ঢাকাতে। বুড়িগঙ্গার তীরের এই চাঁদনীঘাটের তখন খুব নামডাক। বর্তমান ওয়াটার ওয়ার্কস রোড এবং বিলুপ্তপ্রায় বশিরুদ্দিন সরদার পার্কটিকে ঘিরে যে মস্ত এলাকা, তার পুরোটা জুড়ে ছিল চাঁদনীঘাট অঞ্চল। এই ঘাটের নামের সঙ্গে চাঁদনী যুক্ত হওয়ার পেছনে রয়েছে নবাব ইসলাম খাঁর এক বজরা।
এ ঘাটে থাকত নবাবের বজরার বহর। বহরে ছিল চাঁদনী নামের এক বিরাট শাহিবজরা। প্রমোদতরী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যদিও ফতেহ দরিয়া নামেও তার আরেকটি প্রমোদতরী ছিল, তথাপি জাঁকজমকের দিক দিয়ে বেশি আড়ম্বরপূর্ণ চাঁদনীর নামেই ঘাটের নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই বজরা ও ঘাটের প্রতি নবাবের এতই দুর্বলতা ছিল যে তিনি এই ঘাটের কয়েক মাইলের মধ্যে কোনো নৌকো বা জলযানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মতান্তরে এই চাঁদনী বজরাটি ছিল সুবেদার ইসলাম খাঁর পরিবারের আবাসস্থল। এটি যেখানে বাঁধা থাকত বা যেখানে তার প্রথম আগমন ঘটেছিল, সেই স্থানটিই চাঁদনীঘাট নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। আজ সেই খাঁ সাহেবও নেই, তাঁর বোলবোলা ও চাঁদনীও নেই। কালের ছোবলে সবকিছুই নিশ্চিহ্ন।
তবে বজরার বহর না থাকলেও যেন বা ঘাটের মর্যাদা রক্ষার জন্য বর্ষাকালে যখন ক্ষীণতোয়া বুড়িগঙ্গা তীরের পাশ দিয়ে কুলকুল রবে বয়ে যেত, তখন এই ঘাটজুড়ে এই সেদিনও চোখে পড়ত বেদেদের নৌকোর বহর। আর দেখা মিলত দূরদূরান্তে যাত্রী ও মাল বহনকারী গহনা নৌকোগুলোকে নোঙর ফেলতে এই ঘাটে। "আহেন, আহেন, শ্রীনগর, ষোলোঘর, হাঁসাড়া, বহর, টঙ্গিবাড়ী, বহর...'-গহনার মাঝিদের এ রকমের হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকিতে ঘাটটা মুখর হয়ে উঠত। শুধু কি গহনা, এই ঢাকার বুকে গ্রাম থেকে আসা পালকিও দেখেছি আমি। তোলবোলে গা খোট্টা বেহারারা যখন নির্দিষ্ট ছন্দে পা মিলিয়ে হুম্ হুম্ শব্দে শহরের বুকে পা দিত, সে ভারি দেখার জিনিস ছিল। পঞ্চাশের পব আর পালকি চোখে পড়েনি। তবে পালকি নিয়ে আরও দু-চার কথা বলা যায়।
আমাদের দেশে যেসব পালকি বাহকদের দেখা যেত, তাদের বেশির ভাগই বিহারের চাপরা ও মোজাফফরপুর থেকে আসত। বেহারা বলতে হাড়ি, দুলে, বাগদি-এসব হিন্দু ছোট জাতের লোকদের বোঝাত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পেশায় ধর্মজীবী। দূরদূরান্তে ধর্ম প্রচারের জন্য যাতায়াত ছিল তাঁদের। বাহন ছিল প্রধানত ঘোড়া। তারপরই পালকি। আমাদের গ্রামের বাড়িতে তাই বেহারাদের একটা আস্তানা ছিল। ওদের নিজেদের ঢঙে ঘরও তুলে নিয়েছিল। আসত ওরা বর্ষা শেষে শীতের শুকনো মৌসুমে। বর্ষার পানি যখন পথে-প্রান্তরে ডানা ছড়াত, বার-বাড়ির নির্দিষ্ট একটি এলাকায় পালকি তুলে রেখে দেশমুখো হতো ওরা। আমার বেশ মনে পড়ে, কলকাতা থেকে এসে সেকালের প্রথা অনুযায়ী আমার খতনা উপলক্ষে রামধনিদের পালকি চড়া হয়েছিল। সে ভারি মজার অভিজ্ঞতা। রামধনি, মুনশি-এসব নাম আজও মনে পড়ে। মনে পড়ে নিশুতি রাতটাকে ওদের কণ্ঠের গল্প কেমন উদাস করে তুলত।
আমাদের সেই কালে, যখন ঢাকা ছিল ছোট, যার গা থেকে জেলা শহরের গন্ধ পর্যন্ত যায়নি, আসত বেদেনিরা তাদের শাড়ির গাঁঠরি আর বেলোয়ারি চুড়ি, সস্তা পমেটম ও অন্যান্য বিনোদী পশরার ধামা নিয়ে। বিপুলজঙ্ঘা এসব গজেন্দ্রগমনা বেদেনিদের দিকে তাকিয়ে বখাটে পথচারী কেন যে গান গেয়ে উঠত, বুঝতাম না। যাতায়াতব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হওয়ায় এবং দৈনন্দিন দ্রব্য হাতের নাগালে এসে যাওয়ায় ঘাটে ঘাটে বেদেদের কেনাবেচা যেমন বন্ধ হওয়ার পথে, নৌকোর যাযাবর ভাসমান জীবনও লুপ্ত হওয়ার পথে। চাঁদনীঘাটে বেদে নৌকোর বহর তেমন আর দেখা না মিললে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজ থেকে আশি বছরাধিক আগে এই চাঁদনী অঞ্চলে থাকতেন প্রতিপত্তিশালী এক বিশিষ্ট নাগরিক-কামিনীভূষণ রুদ্র। তাঁর মৃত্যুর পর তৎকালীন পৌরসভা তাঁর সম্মানে কলমের এক খোঁচায় চাঁদনীঘাট রোডের ঐতিহাসিক নামটি মুছে ফেলে। তবে কাগজপত্রে নাম পরিবর্তিত হলেও লোকমুখে ওই এলাকার নাম কিন্তু চাঁদনীঘাটই ঘোরে। স্থানীয় বোলে যা চান্নিঘাট।
লগইন করুন? লগইন করুন



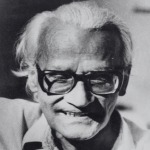


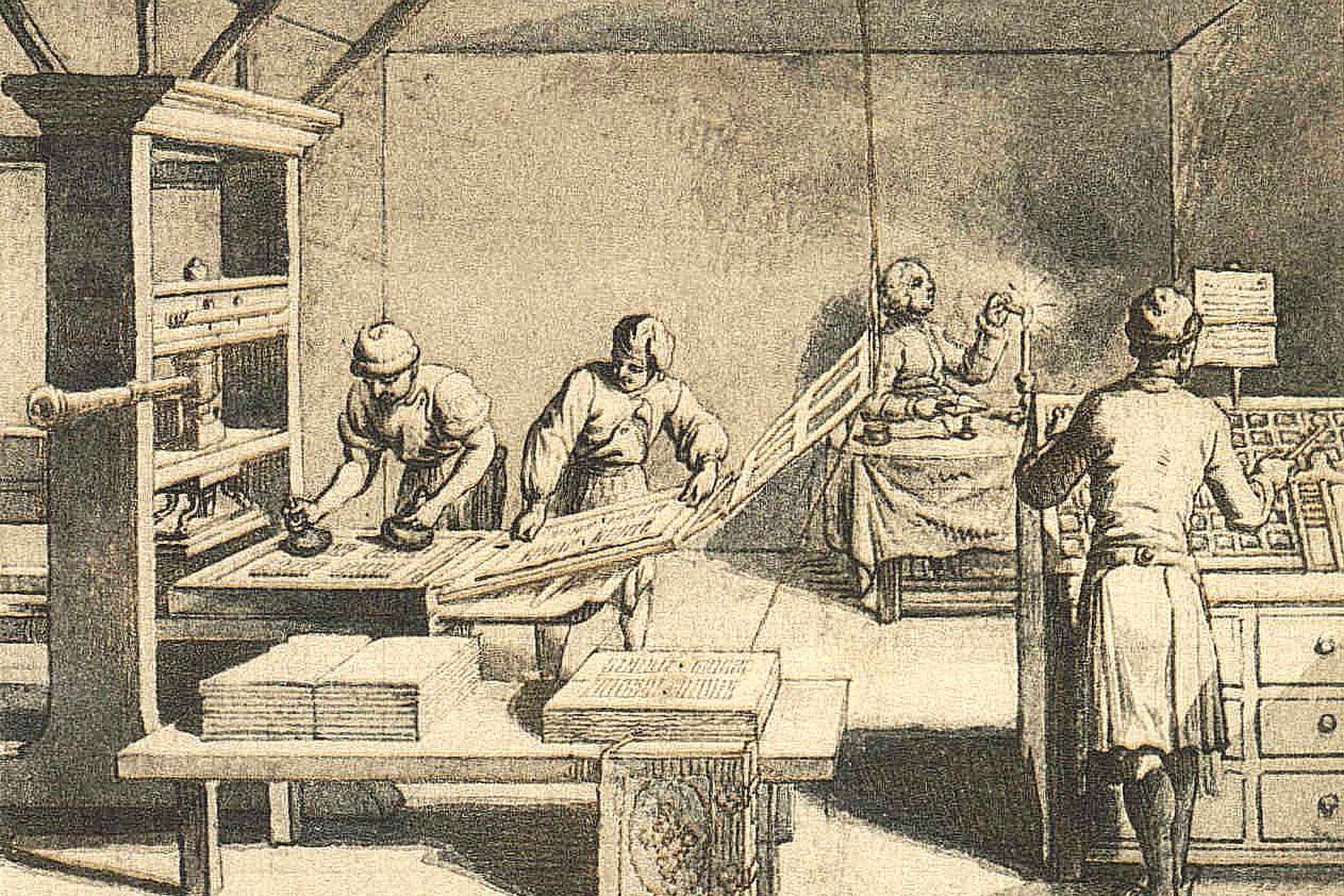












03 Comments
Karla Gleichauf
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment
M Shyamalan
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment
Liz Montano
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment