সিলেটের মরমি-মানস সৃজন ও গণশিক্ষায় সিলেটি নাগরীলিপির ভূমিকা
বঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ এবং তার সংলগ্ন এলাকায় সিলেটি নাগরীলিপি প্রবর্তন এবং প্রায় পাঁচশ’ বছর টিকে থাকা বিস্ময়কর এক ঘটনা। একটি ভাষার একাধিক লিপি উদ্ভাবনা, তার প্রয়োগ এবং চর্চায় মানুষের যে বিপুল অংশগ্রহণ তার নজীরও দুনিয়ায় বেশি একটা নেই। সিলেটি নাগরীলিপি একটি বর্ণমালা, বাংলাভাষারই বর্ণমালা। বাংলা বর্ণমালার সহযোগী বর্ণমালা। সৈয়দ মুতার্জা আলী, মুহম্মদ আসাদ্দর আলী, গবেষক ড. গোলাম কাদির, ড. মোহাম্মদ সাদিকসহ আরও অনেকেই একে বাংলা ভাষার ‘বিকল্প বর্ণমালা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সিলেটি নাগরীলিপি বাংলা বর্ণমালার বিকল্প বর্ণমালা হলেও স্বকীয়তামণ্ডিত। কেবল বর্ণাকৃতিই আলাদা নয়, তার রয়েছে নিজস্ব রীতি। বাংলা বর্ণমালাকে ব্যাপক পরিমার্জনা করে ‘সিলেটি নাগরীলিপি’ উদ্ভাবন করেছেন প্রবর্তকেরা। বর্ণ সংখ্যা, যুক্তবর্ণ ইত্যাদি কমিয়ে ভাষা চর্চাকে গতিময় করা হয়েছে। সাধারণ এবং নিরক্ষর মানুষের কাছে ভাষা চর্চা সহজতর করাই ছিল এই লিপি আবিস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সিলেটি নাগরীলিপির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, এটি বাংলা বর্ণমালাকে অনুসরণ করলেও তার সাহিত্য ধারণ করেছে সিলেটের লোকভাষাকে, কেতাবি ভাষায় যা ‘সিলেটি উপভাষা’ হিসেবে স্বীকৃত।
সিলেটি নাগরীলিপির বর্ণনাম, উচ্চারণ এবং ব্যবহারবিধি বাংলা বর্ণমালাকে অনুসরণ করলেও তার রয়েছে নানা ব্যতিক্রম। নাগরীলিপির সৌজন্যে সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত লোকভাষাটির বিগত চারশ’ বছরের ভাষা-কাঠামো সংরক্ষিত রইল। এ অঞ্চলের ভাষার বিবর্তন-ধারাটিও বুঝতে সিলেটি নাগরীলিপিসাহিত্য অধ্যয়নের বিকল্প নেই।
২
মানবমনীষার শ্রেষ্ট কীর্তি লিপি বা লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন। বস্তুত, এই উদ্ভাবনার মধ্য দিয়ে পৃথিবী সভ্যতার পথে দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে। লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে মানবসভ্যতায় যুগান্তকারী এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। লিপি চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ তথ্য, তত্ত্ব, জ্ঞান, চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং সৃষ্ঠিশীলতাকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ, প্রচার এবং বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগে পেয়ে অভিনব জাগরণ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে।
লিপি আবিস্কারের ইতিহাস ১০ হাজার বছরের প্রাচীন হলেও বাংলা বর্ণমালা চালু হয় সহস্রাধিক বছর আগে। বাংলা বর্ণমালার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদে, প্রায় হাজার বছর আগে। তারপর এগিয়েছে বাংলালিপির সাহিত্য। বাংলা ভাষাচর্চার মূলধারা বাংলা বর্ণমালার অরুদ্ধ যাত্রাপথে চতুর্দশ শতকে যুক্ত হয় আরেক বর্ণমালা, নাম তার ‘সিলেটি নাগরীলিপি’। ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই বর্ণমালা ৫০০ বছর বাংলা বর্ণমালার সমান্তরালে অবস্থান করে বঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের বড় আপন হয়ে ওঠেছিল। তাদের অপত্যস্নেহে এই লিপির দাপটে বাংলালিপি চর্চা অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়ে ওই অঞ্চলে। সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় আদৃত হয়ে নবউদ্ভাবিত সিলেটি নাগরীলিপি জীবন এবং সাহিত্যচর্চায় অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করে।
৩
লিপির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে চতুর্দশ শতকে। ঘটনাটি পৃথিবীতে এখনও ব্যতিক্রমী এক ঘটনা। গোটা দুনিয়ার মানুষ প্রায় সাত হাজার ভাষায় কথা বলেন। সাতহাজার ভাষার অধিকাংশের নিজের লিপি নেই। যাদের ভাষা আছে, অথচ লিপি নেই সেসব ভাষার মানুষেরা তাদের ভাষার জন্য লিপি উদ্ভাবনের পরিবর্তে আশ্রয় নেন অন্য ভাষার লিপিতে। অর্থাৎ অন্য ভাষার লিপিকে ব্যবহার করে তাদের ভাষাকে তারা লিপিবদ্ধ করেন। অন্য কোনও লিপিকে তারা আত্তীকরণ করেন নিজের ভাষার জন্য। এক্ষেত্রে রোমান লিপিকেই বেশি গ্রহণ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশেও এর নজীর রয়েছে। কয়েকটি আদিবাসী নৃগোষ্টী তাদের ভাষা লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন অন্যের লিপি—অধিকাংশে ক্ষেত্রে রোমানলিপি, অথবা বাংলালিপি। অনেক জনগোষ্টী আছেন, যাদের ভাষার চর্চা চলে শুধু মুখে মুখে, তাদের লিখিত সাহিত্য নেই। ওই ভাষাগুলো ক্রমেই বিলোপের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এর কোনও কোনওটি হারিয়েও যাচ্ছে চিরতরে। ভাষা গবেষকদের তথ্যমতে, প্রতি পনের দিনে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে একটি ভাষা। বাংলাদেশে কয়েকটি ভাষা এরকম বিপন্ন অবস্থায় আছে। এদের একটি ‘রেমচিংটা’। ওই ভাষায় কথা বলার জন্য এখন বেঁচে আছেন মাত্র ১০-১২ জন মানুষ। এদের জীবনাবসান হলেই এই ভাষাটিও হারিয়ে যাবে চিরতরে।
গোটা পৃথিবীর ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনেক বড় ভাষারও নিজের অর্থাৎ মৌলিক লিপি নেই। সেই বাস্তবতায় ভাষাভূমি বাংলাদেশে ঘটে পৃথিবীর ব্যতিক্রমী এক ঘটনা। ইতিহাসে যার নজীর খুব একটা নেই। বঙ্গের মানুষের ভাষা এবং সংস্কৃতি প্রেমের এ এক অনন্য উদাহরণ।
বাংলাভাষার দুটো লিপি শুধু কেবল উদ্ভাবনের মধ্যে গুটিয়ে ছিল না, বরং তার চর্চা ছিল বিস্তৃত পরিসরে, বছরের পর বছর। বাংলালিপির বিকল্প লিপি সিলেটি নাগরীলিপি ব্যবহারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনপদের মানুষ নিজেদের চিন্তা, দর্শন এবং সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন স্বতস্ফূর্ত। সিলেটের যে বিশাল বিপুলায়তন মরমি গানের ভুবন এই সৃষ্টির পেছনে নাগরীলিপির অবদান ছিল বড় সহায়ক। নাগরীলিপির মতো একটি গণলিপি জারী না থাকলে গণমানুষের মুখে মুখে রচিত গানগুলো হয়ত লিপিবদ্ধ হওয়ার সুযোগই পেত না। হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ত। নাগরীলিপি ছিল সহজ এবং সরল লিপি যার মাধ্যমে মাত্র আড়াই দিনে বর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন নিরক্ষর ব্রাত্যশ্রেণির মানুষ। পরাক্রমশালী বাংলালিপি যখন দাপুটে অবস্থানে, প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্টপোষকতায় ব্যাপক শক্তিশালী, তখন এর প্রতিপক্ষ হয়ে সিলেটি নাগরীলিপি নিতান্তই অপ্রাতিষ্ঠানিক লোকজনের হাতে প্রবর্তিত হয়ে টিকে থাকা এবং ক্রমেই বিপুল শক্তি অর্জনে সাধারণ মানুষের যে সমর্থন দরকার ছিল, নাগরীলিপির ভাগ্যে তা ঝুটেছিল।
নাগরীলিপি কখনো রাজানুকুল্য লাভ করেনি। কখনও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলেনি তার অনুকুলে। বরং তাকে অনাদর সইতে হয়েছে সরকারি মহলে। তারপরও সাধারণ মানুষ ভালোবাসায় গ্রহণ করেছিলেন নাগরীলিপিকে। একটি ভাষা বা লিপি কখনোই সাধারণ মানুষের সমর্থন না পেলে পল্লবিত হতে পারে না। চতুর্দশ শতাব্দীতে চালু হয়ে ধীরে ধীরে তার বিস্তার হয় সাধারণ্যে। উনিশ শতকে তার জোয়ার আসে। মহাপ্লাবণের ঢেউ আছড়ে পড়ে সিলেটের গণ্ডি পেরিয়ে চারপাশে, ঢাকার অদূরে গাজীপুর অবধি।
নাগরীলিপি কেবল গণমানুষের সাধারণ কাজের বা দৈনন্দিন জীবনাচারের প্রয়োজনীয় লিপি হিসেবে গুটিয়ে ছিল না। সাহিত্যচর্চাও চলে তুমুলভাবে। উনিশ শতকে তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গস্পর্শ করে। একের পর এক জনপদে ঠাই পেয়েছিল এই লিপি। শতশত পুথি রচিত হয় নাগরীলিপিতে। বিপুল বৈভবে, বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তার বিষয়। মধ্যযুগের সাহিত্যের অনুকুলেই ছিল তার শৈলী। মঙ্গলকাব্যের মতো সিলেটি নাগরীতে রচিত হয় বিশাল বিশাল আখ্যান। ‘তালিব হুসন’, ‘নূর পরিচয়, ‘নূর নসিহত’ যেমন রচনা হয় তেমনি রচিত হয় ‘কেতাব হালতুন্নবী’। হালতুন্নবী নবী জীবনের এক মহাকাব্যিক আখ্যান। সামজিক আখ্যান ‘সাতকন্যার বাখান’ থেকে ধর্মীয় বিষয় ‘সয়ফুল বেদাত’। যুদ্ধকাহিনী ‘সোনাভানের পুথি’ থেকে ‘জঙ্গনামা’। প্রেমরোমাঞ্চের কাহিনীকাব্য ‘মহব্বতনামা’ থেকে ‘বাহরাম থেকে জহুরা’। বিপুল বিচিত্র ছিল তার সাহিত্যসম্ভার। সিলেটের মানুষের জনজীবন ছিল তখন এসব পুথির প্রাণষ্পর্শে ভরপুর। গান, আখ্যানকাব্যে যেমন তারা কালের জয়গান গেয়েছেন তেমনি পরমসত্তাকে পাওয়ার সাধনায়ও ছিলেন ব্যাকুল। বিপুলায়তন সাহিত্যের প্রায় ২০০ পুথির সন্ধান রয়েছে আমাদের হাতে। একটি জনপদের মানুষ ভিন্ন একটি লিপিতে সেইকালে রচনা করেছেন এই বিপুল গ্রন্থরাজি, রচনা করেছেন বিস্ময় জাগানিয়া সাহিত্যভাণ্ডার। বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের মানুষের ভাষামনীষার এ এক নতুন পরিচয়।
সিলেটি নাগরীলিপির এই বিরাট বৈভবে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের চিন্তাজগৎ। গানের দেশ, ভাবের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সিলেটি নাগরীলিপির এই অতিগুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রসঙ্গটি কোথাও ইতোপূর্বে আলোচিত হয়নি। এই প্রথম বিষয়টির অবতারণা হল। ২০০৯ সাল সিলেটি নাগরীলিপি ও তার সাহিত্য নবজাগরণের লক্ষ্য নিয়ে কাজের ফলে এখন তার পুথির বড় একটা অংশ প্রকাশিত হয়েছে, নানা রকম বইপত্র প্রকাশের ফলে বিষয়টির প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি নতুনভাবে আকৃষ্ঠ হচ্ছে।
৪
বাংলালিপির আদলে নাগরীলিপিকে সাজানো হয়েছে। বর্ণ সংখ্যা ৩৩, স্বরবর্ণ ৫, ব্যঞ্জন বর্ণ ২৮। এই লিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলালিপির জটিলতার স্থানগুলোকে সহজবোধ্য এবং সরলীকরন। বাংলালিপির সবচেয়ে জটিল বিষয়টি হচ্ছে তার যুক্তবর্ণ। প্রায় শতাধিক যুক্তবর্ণ রয়েছে এই বাংলায়। এগুলো এতই
লগইন করুন? লগইন করুন



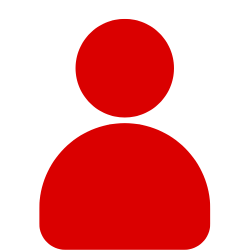




















03 Comments
Karla Gleichauf
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment
M Shyamalan
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment
Liz Montano
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment