ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি
লেখক: কাজল বন্দোপাধ্যায়ায়
১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় 'ভাষা শহীদ গ্রন্থমালা'। এই গ্রন্থমালার বই স্বপ্ন লেখার দায়িত্ব পেয়ে আমি যেমন সম্মানিত বোধ করি, তেমনি উদ্বিগ্ন। বিষয়টির নানা দিক ও মাত্রা রয়েছে। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থিত করাও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'স্বপ্ন' বিষয়টি মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মনোস্তত্ত্বের বস্তুবাদী ধারার সঙ্গে তখনও আমার পর্যাপ্ত পরিচয় ঘটেনি। আমাদের দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের এলাকায় মনোবিজ্ঞানী হিসেবে ফ্রয়েড, ইয়ুং, এ্যাডলারদেরই জয়-জয়কার; শিল্পসাহিত্যেও ফ্রয়েডীয় ভাবধারার বিশাল, প্রায় একচ্ছত্র প্রভাব। এমনকি মার্ক্সবাদীরাও দেখেছি ফ্রয়েডীয় মনোস্তত্ত্বের ভাববাদী চরিত্র সম্পর্কে অবগত নন। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধেয় যতীন সরকার আমাকে অত্যন্ত বড় সাহায্য করেন। তিনিই আমাকে বলেন শ্রী ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের দুইখণ্ডে প্রকাশিত বই পাভলভ পরিচিতি-র সাহায্য নিতে। বাংলাভাষায় বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের (Theory of Alienation) প্রবক্তা হিসেবে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ও বইয়ের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। ওঁর লেখা বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যত বইটি কিনে আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে দিয়েছিলাম, তিনিও বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি সম্পর্কে ঐ বইয়ের সাহায্য নিয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন মনে পড়ে। এবারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ধীরেনবাবুর পথিকৃতের ভূমিকার সঙ্গে সবিস্তারে পরিচিত হলাম। শুধু পাভলভপরিচিতি-র লেখক নন, শ্রী ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতার পাভলভইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমৃত্যু তার প্রাণপুরুষ। ঐ ইনস্টিটিউট থেকে তাঁরা দীর্ঘকাল প্রকাশ করেছেন মনোস্তত্ত্ব, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে চমৎকার মননশীল পত্রিকা মানবমন।
জাস্বপ্ন বইটি প্রকাশিত হলে আমি তার একটি কপি ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পৌঁছুবার জন্যে উদগ্রীব বোধ করি। তখন একবার কলকাতা যাওয়ার সুযোগও এসে গিয়েছিল। পিএইচডি-পর্যায়ের গবেষণা করার জন্যে স্বপ্নভিত্তিক সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ভাবছিলাম। কলকাতা কিংবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অবকাশ কিছু রয়েছে কি-না, খুঁজেছি। কলকাতায় ধীরেনবাবুর বাড়িতেই ছিল পাভলভ ইনস্টিটিউটের কার্যালয়। সেখানে গিয়ে দেখা পেয়েছিলাম এক অক্লান্ত মনীষী-বুদ্ধিজীবীর। মানবমন পত্রিকার অন্যান্য কর্মীদেরকে দেখলাম, তাঁদের কাউকে-কাউকে নিয়ে ধীরেনবাবুর ছিল একটি নাটকের গ্রুপও। ধীরেনবাবুর নিজের লেখা নাটকও তারা মঞ্চস্থ করেছে। কিন্তু, নাটক তো 'বাহা'। মনোবিদ হিসেবে চিকিৎসা-কর্মকাণ্ড, মানবমন পত্রিকাসহ পাভলভইনস্টিটিউটের বিভিন্নমুখী কাজ-এসবই ছিল মূল। একদিন এমন একটি সভায় উপস্থিত দেখলাম অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, উ. বেলা দত্তগুপ্ত, প্রমুখকে। তাঁরা গবেষণা-কাজের ব্যাপারে আমাকে অনেক উৎসাহ দিলেন, স্বপ্ন বইটির ব্যাপারেও। মানবমন পত্রিকার পুরনো কিছু সংখ্যা আমাকে বিনামূল্যে দিলেন। ধীরেনবাবুর কন্যা উশ্রীও পিতার পাভলভ ইনস্টিটিউটের কর্মী। গোটা পরিবারই একটি আদর্শ-উজ্জীবিত দল। পাভলভ মনোস্তত্ত্ব সম্পর্কে উশ্রীর ইংরেজিতে লেখা একটি পুস্তিকা আমি পরবর্তীকালে অনুবাদ করি। কাজকান চায়। উজ্যাৎ উকিল চট্টজোর উৎ ম্যাসাচ্যাক
ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেবারে সংঘঠিত যোগাযোগ দীর্ঘকাল বজায় ছিল। মানবমন পত্রিকায় স্বপ্ন বইটির একটি সমালোচনা ছাপা হয়েছিল। এ-ব্যাপারে একবার তিনি আমাকে নিম্নরূপ একটি চিঠি লিখেছিলেন—
১৩২/১এ বিধান সরণি
কলকাতা ৭০০০৪৪
১১/৪/৮৭
প্রীতিভাজনেষু,
শরীর ভাল যাচ্ছিল না। উত্তর দিতে দেরি হল। মনে কিছু করবেন না। বইটি ভাল লেগেছে। 'মানবমন' এর ১৯৮৮ জানুয়ারী সংখ্যায় বইটির সমালোচনা প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে। অক্টোবর সংখ্যায় স্থানাভাব ঘটেছে। এ বিষয়ে আপনার formal সম্মতি দিয়ে একটা চিঠি দেবেন।
প্রতিটি চিঠির সঙ্গে ঠিকানাটা লিখবেন। আমি একটু অগোছালো ব্যক্তি। রোগীদের চিঠি ও অন্যান্য চিঠি এলে সপ্তাহে প্রায় ৫০/৬০ খানা চিঠি লিখতে হয়। ঠিকানা হাতের কাছে পেলে সুবিধে হয়।
আপনার এখানে আসার সম্ভাবনা আছে জেনে সুখী হলাম।
প্রীতিনমস্কার। ইতি শুভার্থী
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
পরবর্তী সময়ে ১৯৯০-৯৪ সালে আমি যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করেছি, তখনও বেশ ক'বার ধীরেনবাবুর কাছে গিয়েছি। অনন্য একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে ওঁর একটি সীমিত মাপের প্রতিষ্ঠাও আমি কলকাতায় দেখতে পেয়েছি। কিছু সভাসমিতিতে অন্তত ওঁর ডাক পড়তো। তবে, সে প্রতিষ্ঠা ওঁর মনীষা কিংবা কৃতীর তুলনায় নিঃসন্দেহে খুবই কম বলেও আমার মনে হয়েছে। রণেশ দাশগুপ্তকে সবসময় দেখতাম ওঁর খোঁজ রেখেছেন, এমনকি আমার কাছ থেকেও কখনও-কখনও। আমার কাছে মনে হয়েছে, কলকাতায় ক্ষুদ্র একটি মহলে অন্তত ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের মর্যাদা ছিল হীরেন মুখোপাধ্যায়ের কাছাকাছি। বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব এবং বস্তুবাদী (পাভলভীয়) মনোস্তত্ত্বের মতো দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার পথিকৃৎসুলভ এবং বিশদ লেখালেখি তাঁকে এই সম্মান এনে দিয়েছিল অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষের মনে। এ দু'টো বিষয়ে কলকাতা শহরেও তার মতো গভীরতা ও বিস্তার নিয়ে তেমন কেউই আর লিখতে আসেননি। ভবিষ্যৎ সময় এ বিষয়দুটোর গুরুত্বকে আরো ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে বলেই আমার বিশ্বাস। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্যে সংগ্রামে পুনরায় গতিসঞ্চারেও এ বিষয় দু'টোর অনেক গুরুত্ব থাকবে। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের যে ব্যাপক মূল্য হলো না, কিংবা মর্যাদা, তা-ই ছিল সমাজতন্ত্রের জন্যে আন্দোলনে সৃষ্ট সঙ্কটের একটি সঙ্কেত। এসব বিষয়কে আমলে নিয়েই মানুষের জন্যে আগ্রহোদ্দীপক কিছু ধারণা হাজির করা সম্ভব। সেজন্যে যেতে হবে ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা পাঠে, তাঁর বিশ্ববীক্ষার বিচার-বিশ্লেষণে।
আমি আজ ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত একটি পুস্তিকা সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করবো। পুস্তিকাটি ১৯৮৩-৮৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ওঁর রায়-বাহাদুর জি সি ঘোষ স্মারক বক্তৃতার সঙ্কলন। পাভলভ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত পুস্তিকাটির শিরোনাম A Psychiatrist Reviews Indian Religion. বর্তমানে পৃথিবীতে যখন ধর্ম এবং ধর্মীয় মৌলবাদ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে, তার বঙ্গ পূর্বেই কিন্তু এই বিপদ সম্পর্কে আঁচ-অনুমান করতে পারার প্রমাণ পাওয়া যায় ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তৃতা দু'টোতে। ১৯৯০ সালে লেখা পুস্তিকার মুখবন্ধে ধীরেনবাবু লিখেছিলেন:
"আমি যখন বক্তৃতাগুলো দিই, ধর্মীয় দিগন্ত তখন এখনকার মতো এতো কালো ছিল না। অবশ্য তখনকার চেয়ে এখন পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্ব কম বিপন্ন। দুটো পরাশক্তির মধ্যে তারকাযুদ্ধের শঙ্কা সাময়িকভাবে হলেও হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু, বিকশিত ধর্মগুলোর মৌলবাদীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে ধ্বংস নেমে আসার ভয় দ্রুতগতিতে বাড়ছে। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় নয়, পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু এলাকায় মৌলবাদীরা তাদের ভূমিকা পালন করছে। পৃথিবীব্যাপীই শাসক ব্যারন এবং মৌলবাদীদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সংযোগের ভয়াবহ খবর সংবাদমাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরও পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন, মৌলবাদের উত্থান রুদ্ধ করার জন্যে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের শুরু করা উচিৎ সংগঠিত প্রচেষ্টা। যে কোনো মূল্যে আমাদের নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে।"
এ বক্তব্যের মধ্যে কী প্রভৃত সত্য ও দূরদৃষ্টি ছিল, পরবর্তী সময়ের উপমহাদেশের ও বিশ্ব-পরিস্থিতি সামান্য পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যায়। উপমহাদেশে দুটো দেশেরই সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি পারমাণবিক শক্তি অর্জনের মহড়া দিয়েছে, পূর্ব ইউরোপে কসোভো-সার্বিয়া-ক্রোয়েশিয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গে চেচনিয়ার দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকেও মৌলবাদসমূহের মধ্যকার বিরোধের ভয়াবহ পরিণতিই উপলব্ধি করা যায়।
মুখবন্ধে ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় E. W. Hopkins-এর Origin and Evaluation of Religion বইটি থেকে একটি অত্যন্ত ভাবনাউদ্দীপক উদ্ধৃতি উপস্থিত করেছেন, যেখানে হপকিন্স্ ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যকার একটি সাধারণ (Common) অনুসন্ধান-প্রয়াস সম্পর্কে বলেছেন:
কোনো শক্তি যদি মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে তা সুশৃঙ্খলভাবে অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদন্ডী, মেরুদণ্ডী থেকে সচেতন, আত্মসচেতন যুক্তিবাদী সুশৃঙ্খল প্রাণকে পরিচালনা করে। এই সহজাত সুশৃঙ্খলার একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী উপস্থিত করেছেন সেই বিজ্ঞানীগণ যাঁরা দুই বা ততোধিক প্রজন্মব্যাপী সপরিশ্রমে মহাবিশ্বের দৃশ্যমান সব বাস্তব সত্যকে সংগ্রহ করেছেন এবং পদ্ধতিসম্মতভাবে সেগুলোকে সাজিয়েছেন কিন্তু, বস্তু এবং তার নিয়মকে কেন তারা এতোটা সময় দিয়েছেন? স্পষ্টতই তারা আকাঙ্ক্ষা করেন শৃঙ্খলা... বিশৃঙ্খলায় তারা অস্বস্তি বোধ করেন; এ থেকে তারা পরিত্রাণ চান এবং এটা বোধ করার আরামটুকু চান যে তারা একটি সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে বাস করেন। যাদুর সাহায্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দিয়ে তার শুরু। এখন সে শৃঙ্খলা চায় বিশ্বকে বোঝার মধ্য দিয়ে...হিন্দু
লগইন করুন? লগইন করুন


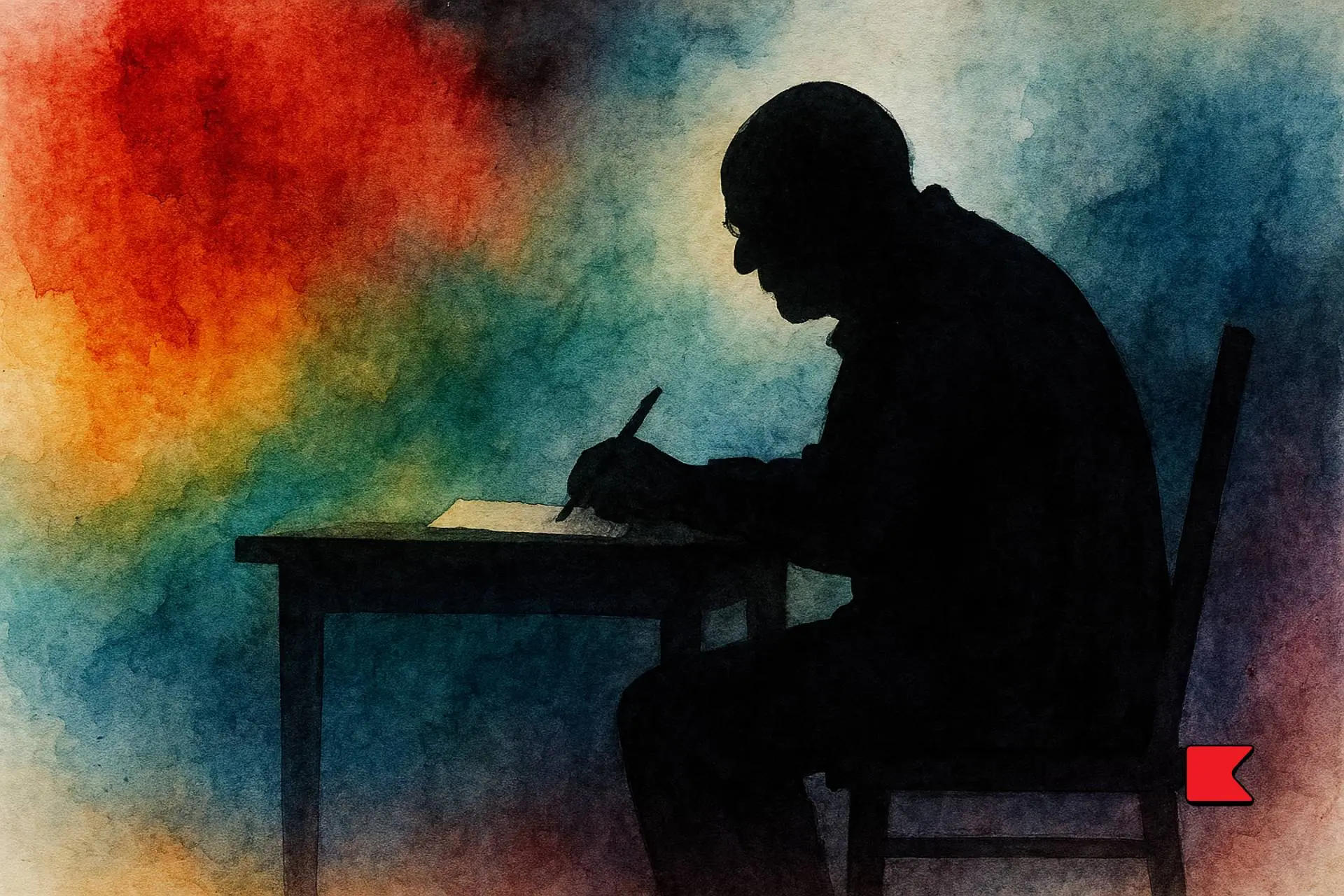




















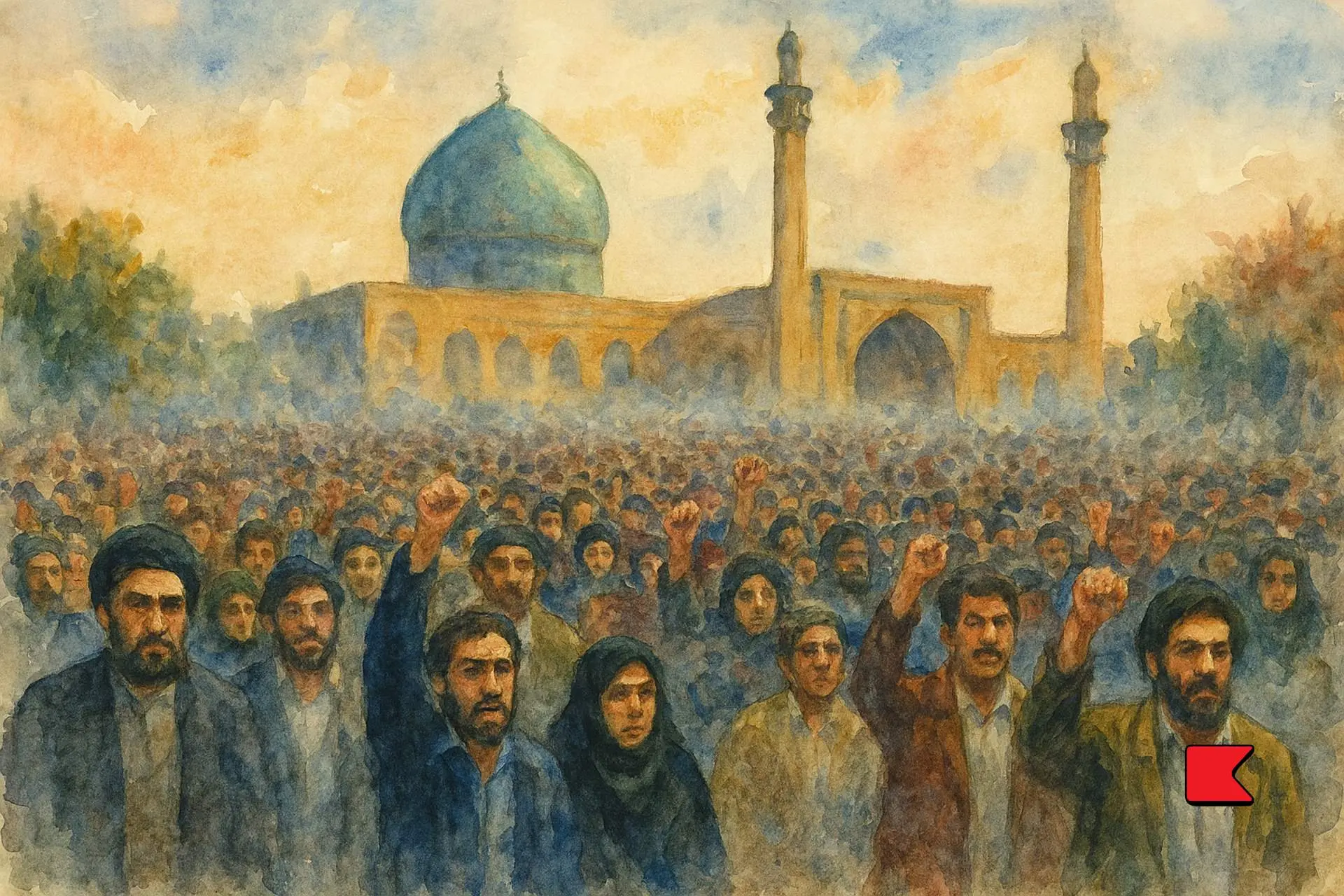

03 Comments
Karla Gleichauf
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment
M Shyamalan
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment
Liz Montano
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment