সদরঘাটের বাকল্যান্ড বাঁধ
সেদিন বুড়ীগঙ্গার তীরবর্তী আমাদের এই বাকল্যাণ্ড বাঁধের কথা বলছিলাম আহমদউল্লাহ সাহেবের সাথে। বলছিলাম—কি ছিল আর কি হয়ে গেল! কি দেখেছিলাম সে সময় আর কি দেখছি আজ! দশ বছর আগে যে লোক ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সে যদি আজ ফিরে আসে, তাহলে বাকল্যান্ড বাঁধের শ্রী দেখে সে তাজ্জব বনে যাবে। আর যদি আমার মতো নেশাখোর ভ্রমণার্থীদের কেউ হয়, তাহলে মর্মান্তিক আঘাত পাবে। কতোদিনের কতো স্মৃতি এই নদী আর এই নদীতীরের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে! এখন তাই একান্ত বাধ্য হয়ে না পড়লে ও পথে পা বাড়াই না। কেনো এমন হলো? এই বাকল্যান্ড বাঁধের পিছনে একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসটা অনেকেরই হয়তো জানা নাই। পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় এক মাইল লম্বা এবং গড়ে ৩০ ফুট প্রশস্ত বাকল্যান্ড বাঁধ বছর কয়েক আগেও মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি ছিল। এখন এই সম্পত্তির মালিক I.W.T.A (Inland water transport Authority) বা আভ্যন্তরীণ পানি পরিবহণ কর্তৃপক্ষ। তার মানে মাত্র ক’বছর আগে এই বাকল্যান্ড বাঁধ আপনার আমার সকলের অর্থাৎ ঢাকা শহরের নাগরিকদের নিজেদের সম্পত্তি ছিল। সেই সম্পত্তি কোন সময়, কেনো এবং কেমন করে I.W.T.A-র নিকট হস্তান্তরিত হয়ে গেল, আপনারা এ খবর রাখেন? বোধ হয় না।
তৎকালীন পৌরসভার সদস্য জনাব আহমদ উল্লার বয়ানীতে শুনুন। এই হস্তান্তরের কাজটি বড় সহজে সম্পন্ন হয় নি। এজন্য বেশ কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। সরকার আর পৌরসভার মধ্যে এই নিয়ে বছর দুই ধরে রীতিমত টাগ-অব-ওয়ার চলেছে। পৌরসভা তার এতোদিনের এই অধিকার বড় সহজে ছেড়ে দেয় নি।
১৯৬৩ সালের কথা। বিনামেঘে বজ্রাঘাত বলে একটা কথা আছে না? ঠিক তাই। পৌরসভা হঠাৎ একদিন সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন যে, এই বাকল্যান্ড বাঁধটিকে তাঁদের আভ্যন্তরীণ পানি পরিবহণ কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এর কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল I.W.T.A ঢাকার বুড়ীগঙ্গার ঘাটকে একটি পোর্টে পরিণত করব। এই পোর্ট গড়ে তোলা হলে প্রদেশের দূর দূর অঞ্চলের যাত্রীদের আসা-যাওয়া এবং মাল চলাচলের ব্যাপারে প্রচুর সুবিধা হবে। ফলে ঢাকা শহরের আয় যথেষ্ট পরিমাণ বেড়ে যাবে, তার মর্যাদাও বাড়বে।
এই নির্দেশ পাওয়ার ফলে পৌরসভার সদস্যদের মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়ে গেল। সবাই উত্তেজিত। বাকল্যান্ড বাঁধ ঢাকা শহরের সর্বসাধারণের সম্পত্তি। এর পিছনে দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। শহরের নাগরিকেরা এক শতাব্দীকালেরও আগে থেকে এ অধিকার ভোগ করে আসছে। সরকার এখন সেই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছেন—উত্তেজনার কারণ আছে বই কি।
এই বাকল্যান্ড বাঁধের জন্ম হয় ১৮৬০ সালে—সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হবার তিন বছর পরে। তার আগে নদীর পাড় সমতল না থাকায় এবং নানা লোকের মালিকানার জমি থাকায় সর্বসাধারণের বেড়াবার সুযোগ ছিল না। শহরের গা ঘেঁষে নদী থাকবে, কিন্তু সেই নদীর ধারে বেড়ানো যাবে না এটা কি কম দুঃখের কথা! হিন্দু-মুসলমান ভ্রমণার্থীরা এই নিয়ে প্রায়ই জল্পনা-কল্পনা করত। অবশেষে শুধু জল্পনা-কল্পনা নয়, তারা একটা সংকল্প নিয়ে কাজে নামল। হিন্দু আর মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ে উদ্যোগী ও উৎসাহী যারা, তাঁরা দল বেঁধে নদীর ধারের জমিগুলি যাদের, তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে ধন্না দিতে শুরু করলেন। চাঁদার খাতা নিয়ে নয়। তাঁদের আবেদন—বিচিত্র এক আবেদন—এই জমির মালিকদের সবাইকে কিছু কিছু নদী সংলগ্ন জমি ছেড়ে দিতে হবে।
কেনো, কি হবে জমি দিয়ে? তাঁরা বললেন, তাঁরা নদীর ধার দিয়ে লম্বা একটা পাকা রাস্তা তৈরী করবেন। সেই রাস্তা দিয়ে সকাল-বিকাল দুবেলা বেড়ানো যাবো।
প্রথমে কাউকে কাউকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পরে ক্রমে ক্রমে সকলেই তাঁদের এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। বলল, বেশ তো, নদীর ধারে উঁচু বাঁধা রাস্তা যদি তৈরী হয়, তবে তো সবারই ভালো—সবাই বেড়াতে পারবে। তখন তারা সবাই নিজের নিজের জমি থেকে বাঁধের জন্য যেটুকু জমি দরকার তা পৌরসভার নামে দিল লিখে। ১৮৬০ সালে তাদের দেওয়া সেই জমির উপর পাকা বাঁধটা তৈরী করা হলো। এই হচ্ছে বাকল্যান্ড বাঁধের জন্মকথা।
সেই থেকে ঢাকা পৌরসভা বাকল্যান্ড বাঁধের একচ্ছত্র মালিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে। সরকার বিভিন্ন উপলক্ষে একাধিকবার এই স্বীকৃতি দিয়ে আসছেন। উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতক চল্ল। এর মধ্যে এই মালিকানার প্রশ্ন নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি। এই নিয়ে প্রথম বিরোধের সৃষ্টি হলো ১৯২৭ সালে। এই সময় ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর সর্বপ্রথম বাকল্যান্ড বাঁধকে সরকারী সম্পত্তি বলে দাবী করলেন।
এবার বাকল্যান্ড বাঁধের মালিকানার স্বত্ব নিয়ে পৌরসভা আর কালেক্টর-এর মধ্যে বিরোধ শুরু হলো। এই বিরোধ একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলে পর সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করলেন যে, বাকল্যান্ড বাঁধ পৌরসভার সম্পত্তি। তবে পৌরসভার সমস্ত সদস্য যদি একমত হয়ে এর মালিকানার অধিকার ছেড়ে দেন, তা হলেই বাকল্যান্ড বাঁধ সরকারী সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। তখন পৌরসভার এই প্রশ্নের উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটাভুটির ফলে দেখা গেল, শুধু নির্বাচিত সদস্যেরা নয়, নির্বাচিত, মনোনীত এমনকি ইংরেজ সদস্যেরা পর্যন্ত সবাই একমত। এই সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল যে, কালেক্টর বাকল্যান্ড বাঁধকে সরকারী সম্পত্তি বলে যে দাবী করেছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। কালেক্টরের বিরুদ্ধে পৌরসভায় এই প্রস্তাব জাতি-বর্ণ-দল নির্বিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার ফলে সরকারকে একটু অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। তখন সরকার কালেক্টরকে সতর্ক করে দেন যে, তিনি যেন এই বিষয়টা নিয়ে আর বেশীদূর অগ্রসর না হন।
কিন্তু তা সত্ত্বেও কালেক্টরের তখনও যথেষ্ট শিক্ষা হয় নি। নেটিভদের কাছে তার প্রেষ্টিজটা এভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ায় তার গোঁ তখন আরও বেড়ে গিয়েছে। সরকারের এই সতর্কবাণী তাঁর হুঁশ ফিরিয়ে আনতে পারেনি। পরাজয়ের জখমটার কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। পৌরসভাকে ঘায়েল করবার মতলব নিয়ে তিনি তাঁর তূণ থেকে এক নতুন অস্ত্র বার করলেন। তিনি এক নতুন নির্দেশ জারী করলেন। বুড়ীগঙ্গা নদীতে মালপত্র ওঠানো-নামানোর জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে সমস্ত অস্থায়ী বা স্থায়ী কাঠের কিংবা বাঁশের জেটি অথবা বাঁশের সাঁকো তৈরী হবে তাহার জন্য কালেক্টরকে খাজনা দিতে হবে।
ইতিপূর্বে এই প্রথা চালু ছিল না। পৌরসভার বিরুদ্ধে মনের ঝাল মিটানোর জন্য কালেক্টর অনেক ভেবে-চিন্তে এই নতুন অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই অস্ত্রও বিশেষ কাজে এলো না। পৌরসভা কালেক্টরের এই নির্দেশ সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে লেখালেখি চালালেন। এবার সরকারের তরফ থেকে কালেক্টরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, এই ব্যাপারে পৌরসভার কাছ থেকে তিনি কোনো খাজনা দাবী করতে পারেন না। অবশ্য তিনি রয়ালটি হিসাবে কিছু পেতে পারেন। কিন্তু এই রয়ালটির পরিমাণ বছরে দু’শো টাকার বেশী হতে পারবে না। কালেক্টর এর পরে আর এসব বিষয় নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করতে যান নি। বছরে দু’শো টাকা রয়ালটি হিসাবটা কাগজ-পত্রেই লেখা রইল, পৌরসভাকে কোনো দিন সরকারের কাছে এই খাতে কোনো টাকা জমা দিতে হয় নি।
১৮৬০ থেকে ১৯৬০, এই এক শতাব্দী এইভাবে কাটল। তার মধ্যে ১৯২০ সালের পৌরসভা বনাম কালেক্টর—কৌতুক নাট্যটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।
ছবি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাপ্রসূত
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



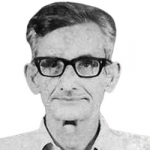















Comments