জননেতা মণি সিং
মণি সিং—রহস্য আর রোমাঞ্চ দিয়ে ঘেরা একটি নাম। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মুখে মুখে প্রচারিত এই নামটি। তার সঠিক পরিচয় আর কার্যকলাপের ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই। তাঁকে কেন্দ্র করে বাস্তবে আর কল্পনায় মিশানো বহু কাহিনি রচিত হয়ে উঠেছে। ময়মনসিংহ জেলার গ্রামাঞ্চলের বুড়ো চাষীরা তাঁদের নাতি-নাতনীদের কাছে রূপকথার মতো সেই সমস্ত কাহিনি শোনায়। ছোটরা অবাক কৌতুহলে বড় বড় চোখ করে সেই সব কথা শোনে। আধুনিক যুগের রূপকথার নায়ক মণি সিং।
কমরেড মণি সিং ময়মনসিংহ জেলার সুসং-দুর্গাপুরের রাজ পরিবারের ছেলে—এই কথাটা, কে জানে কেমন করে, ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে গেছে। এমনকি তাঁর পরিচিত মহলেও অনেকের মনে এই ধারণাটা বদ্ধমুল হয়ে আছে। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। তবে সেখানকার জমিদার বাড়ির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। তাঁর মাতামহী জমিদার বাড়ির মেয়ে। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। মণি সিং তাঁরই ছেলে। তাঁর পিতা উনিশ শতকের শেষ ভাগে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক কোলকাতায় চলে যান। সঙ্গে তাঁদের দুটি ছেলে। তিনি কোলকাতায় পৌঁছে একটা চাকরী জুটিয়ে নিয়ে সেখাইে বসবাস করতে লাগলেন। ১৯০১ সালে কোলকাতায় মণি সিংএর জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন মাত্র আড়াই বছর সে সময় তাঁর পিতা অকালে মারা গেলেন। তিনি কোনোই সঞ্চয় রেখে যেতে পারেননি। ফলে তাদের সম্পূর্ণভাবে মামাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হলো। বড় দুই ভাই কোলকাতায় দুই মামার বাসায় থেকে লেখাপড়া করতে লাগল। মণি সিং-এর মা তাঁর মেয়ে নির্মলা আর মণি সিংকে নিয়ে ঢাকায় তাঁর এক ভাইয়ের বাসায় এসে রইলেন।
এই সময় সুসং জমিদারী এষ্টেট থেকে তাঁদের সংসার নির্বাহের জন্য তাঁর মাতামহের ভিটার উপর একটি বাড়িসহ নয় একর জমি লিখে দেওয়া হয়। তার মাতামহীর নামে যেই টংক জমিগুলি ছিল, সেগুলিই তাঁর মার নামে লিখে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া মা-র বছরের খোরাকীর ধান ও মাসোহারার ব্যবস্থা জমিদারী এষ্টেট থেকে করা হয়েছিল। সুসং এর এই বাড়ি তৈরী হলে পর তাঁর মা তাঁর দিদি ও তাঁকে নিয়ে সুসং এ চলে এলেন। সুসংএর নীচু ক্লাসের পড়া শেষ হলে তাঁকে লেখাপড়া করানোর জন্য কোলকাতায় পাঠানো হয়। কোলকাতায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সুসং-এর জমিদার মহারাজ কুমুদচন্দ্রের বাড়িতে। এক সুরম্য অট্টালিক। ঠাকুর, চাকর, ঝি, দারোয়ান, কোচোয়ান, কর্মচারী—এক এলাহী ব্যাপার! এই পরিবার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল এবং এঁদের বিনয়ী ও ভদ্র বলেও নাম ছিল। এখানে বেশ ভালোভাবেই তাঁর শিক্ষাজীবনের দিনগুলো কাটছিল।
কিন্তু এই বাড়িতে কিছুকাল থাকার পর এক নতুন চিন্তা তাঁর মাথায় এসে চাপল। এখানে এসে প্রথমে নতুন নতুন কতগুলি কথা শুনলেন। দেশের পরাধীনতার কথা, ইতিপূর্বে তাঁর মনে কোনোদিনই জাগেনি। এখানে এসে নানাজনের বলাবলির মধ্য দিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, বৃটিশরা ভারতকে গোলাম করে রেখেছে; দিনে ডাকাতি করে কোটি কোটি টাকা বিলেতে নিয়ে যাচ্ছে; সারা গারো পাহাড়টা সুসংএর জমিদারদের হাত থেকে জবরদস্তি করে কেড়ে নিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথা শুনতে শুনতে তাঁর মনে ব্রিটিশ বিরোধীতার ভাব ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল। এরপর ১৯১৪ সলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখা গেলো, এদেশের মানুষ সবাই জার্মানীর পক্ষে, ইংরেজদের পক্ষে কেউ নেই। সেই সময় ঘরে বাইরে সর্বত্র এই নিয়ে আলোচনা চলেছে। এদের এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সুচনা হয়েছিল।
অনুশীলন দলে যোগদান
এই সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল খুবই গরম। ‘অনুশীলন’ আর ‘যুগান্তর’ এই দুটি সন্ত্রাসবাদী দল তখন বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি অনুশীলনদলের সংস্পর্শে এলেন এবং তার সশস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যে ইংরেজ বিতাড়নের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দলে যোগ দিলেন। এই উদ্দেশ্যে, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তিনি একাধিক্রমে প্রায় দশ বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে শরীরচর্চা করে চললেন। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই শরীরচর্চা তাঁর পক্ষে আশীর্বাদস্বরপ হয়েছিল। এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সামান্য রকম শরীর খারাপ হওয়া ছাড়া তিনি কোনোদিন কোনো গুরুতর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েননি।
অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন
১৯২১ সালে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে অভূতপূর্ব গণ জাগরণ দেখা দিল। তিনি এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েছিলেন। কিন্তু অনুশীলন দল এই আন্দোলনে যোগদানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তাঁদের মতে এইভাবে আন্দোলন করে জেল ভর্তি করে ফেললেও ইংরেজকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা যাবে না। এই আন্দোলন বিপ্লব-বিরোধী কাজ; প্রকারান্তে দেশের লোকদের ভেড়া বানিয়ে রাখার কাজ। কোনো বিপ্লবী এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারে না। অথচ এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের এরূপ ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন আর কোনোদিন হয়নি। এইটাই ছিল হিন্দু-মুসলমানের প্রথম বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এই অভুতপূর্ব গণজাগরণ তাঁর মনে গভীর রেখাপতা করেছিল। কিন্তু অনুশীলন দল এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে তিনি ক্ষুণ্নমনে আন্দোলনের বাইরে থেকে গেলেন। অনুশীলন দল সে সময় যে মারাত্মক ভুল করেছিল তিনি পরে তা পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।
কৃষকদের মধ্যে প্রথম কাজ
১৯২৪ সালে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বপ্রথম কৃষকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তখনও তিনি অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই আদর্শে বিশ্বাসী। তখনও তাঁর সামনে একমাত্র লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে টেনে নিয়ে আসা, যাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। গত শতাব্দীর হাজং বিদ্রোহের কাহিনি এবং অসহযোগ আন্দোলনে চৌরীচৌরার কৃষকদের হিংসাত্মক সংগ্রাম—এই দৃষ্টান্তগুলি তাঁর চিন্তাকে এ পথে চালিত করেছিল। সুসং থেকে বেশ কিছু দূরে কালিকাপুর গ্রাম। তিনি আর তাঁর একজন সহকর্মী সেখানকার হাজং কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তাদের এক বড় সমস্যা ছিল, ছেলেপিলেদের শিক্ষার সমস্যা। এই ব্যাপারে তারা তাঁদের সাহায্য চাইল। তাঁরা এই ব্যাপারে হাত দিলেন এবং জিলা কেন্দ্র থেকে কয়েকজন কর্মী আনিয়ে পর পর পাঁচটা গ্রামে পাঠশালা বসালেন। এইভাবে সেখানকার হাজং কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের কিছুটা ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হলো।
মার্ক্সবাদে দীক্ষা
এইভাবে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। ইতিমধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটা বিরাট রূপান্তর ঘটে গেলো। অনুশীলন দলের জেলা কেন্দ্রের নেতা একদিন এক বিশিষ্ট কর্মীকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের কাছে। এই কর্মীকে গোপনে রাখতে হবে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে। এর নাম গোপেন চক্রবর্তী। বয়সে মণি সিংএর চেয়ে সামান্য কিছু বড়। সন্ত্রাসবাদীর কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি পালিয়ে রাশিয়া গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরে এসেছেন মার্ক্সবাদ লেনিনবাদে দীক্ষিত হয়ে। গোপেন চক্রবর্তী মণি সিং এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি প্রথমেই মন্তব্য করে বসলেন, এখানে যে কাজ চলছে তা বিপ্লব বিরোধী সংস্কারবাদী কাজ; এগুলো ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কথা শুনে মণি সিং আর তাঁর সহকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। দু’পক্ষে বেঁধে গেলো ঘোর তর্ক। পর পর সাতদিন ধরে এ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলল। গোপেন চক্রবর্তী মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম, ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এ পক্ষের এ সব বিষয় সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণাই ছিল না। হাতিয়ার ছাড়াই তাঁরা লড়াই করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্ক চলল। গোপেন চক্রবর্তী মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম, ধনতন্ত্র, সামন্ত্রতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এ পক্ষের এ সব বিষয় সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণাই
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



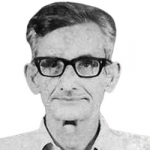















Comments