‘সুশীল সমাজ’ সমাচার
॥ ১॥
‘সুশীল সমাজ’ (‘Civil Society')-এর প্রসঙ্গটি আজকাল এদেশের শিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তিন-চার দশক আগে কিন্তু ঠিক এ রকমটা ছিল না। তবে একথাও অবশ্য বলা যাবে না যে, ‘সুশীল সমাজ' অভিধাটির ব্যবহার তখনকার দিনে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু স্তরে লেখাপড়ার সময়ে এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব চর্চার প্রয়াসকালে ‘সুশীল সমাজ' প্রসঙ্গটির সাথে কারো কারো কিছুটা পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটতো। তবে সে সময় তাদের সাথে সেই পরিচয়টি ঘটতো প্রধানত একটি একাডেমিক ও তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে। পরিচয় সীমাবদ্ধ থাকতো মূলতঃ বইয়ের পাতার গণ্ডির মধ্যে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌর বিজ্ঞানসহ কোনো বিষয়ের নির্ধারিত টেক্সট বইয়ের পাতায় ‘সুশীল সমাজ' প্রসঙ্গের কোনো খোঁজ ছিল বলে অন্তত আমার তো মনে পড়ে না। আরো অনেক ওপরের ক্লাসে লেখাপড়া করার সময়ে, কিংবা রাজনৈতিক সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক বা গবেষক হিসেবে, দুই একটি পাঠ্য বইয়ে এবং বিশেষত নির্ধারিত পাঠ্য বইয়ের বাইরের দুষ্প্রাপ্য কিছু বই থেকে, ‘সুশীল সমাজ' প্রসঙ্গের সাথে উৎসাহী কোনো মানুষের পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটতো।
বাংলাদেশে ‘সুশীল সমাজ' অভিধাটির বহুল ব্যবহার ও প্রয়োগ শুরু হয়েছে তিন দশক আগে, আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকে। এখন পত্রিকার কলামে, টিভি'র টক শোতে, সংবাদ প্রতিবেদনে, সেমিনারে, গোলটেবিল আলোচনায়, মানববন্ধনের ঘোষণায়, পাঁচ তারা হোটেলের আলোচনা সভায়, বিশিষ্টজনদের বক্তৃতায়-ভাষণে, পোস্টার-ব্যানার-হোর্ডিংয়ে-প্রায় সর্বত্রই বহুল উচ্চারিত ও ব্যবহৃত একটি প্রসঙ্গ হলো ‘সুশীল সমাজ'। বলা যায় যে, তখন থেকেই বাংলাদেশে ‘সুশীল সমাজ' অভিধাটি ব্যবহারের সাম্প্রতিক ঢলের শুরু। বিশ্বপরিমণ্ডলেও সেই আশির দশক থেকেই ‘সুশীল সমাজ’ প্রসঙ্গটিকে ‘জাতে উঠ'তে দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিলে ও প্রতিবেদনে, দাতা সংস্থাগুলোর নির্দেশাবলী ও সুপারিশে, গ্লোবাল সংস্থাগুলোর বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদনে, নামী-দামী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বিশ্বের পণ্ডিত মহলের গবেষণাপত্র ও থিসিসে 'সুশীল সমাজে'র প্রসঙ্গটিকে পরিণত করা হয়েছে আলোচনার একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ে। এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতাতেই, এ বিষয়ে উৎসাহের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের চেয়ে লক্ষণীয় রূপে অগ্রবর্তী হিসেবে, বাংলাদেশে 'সুশীল সমাজ' অভিধাটির ব্যবহারই শুধু বাড়েনি, ‘সুশীল সমাজ' বলে কথিতরা বাংলাদেশের সমাজ জীবনে একটি শক্তিশালী প্রায়োগিক বাস্তব উপাদান ও শক্তি হয়ে উঠেছে দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক মহল থেকে অনেক আগেই 'সিভিল সোসাইটি' বা 'সুশীল সমাজ' প্রসঙ্গ নিয়ে একটি গভীর আলোচনার সূত্রপাত করা উচিত ছিল। যতোটা প্রয়োজন, সেই তুলনায় এই প্রয়োজনীয় কাজের সামান্যই করা হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিত, ভিন্ন ভিন্ন বিবেচনা থেকে হলেও, ‘'সুশীল সমাজে'র বিষয়টিকে গভীর বিশ্লেষণ না করেই, হয় তাকে চোখ বন্ধ রেখে অন্ধভাবে 'প্রাসঙ্গিকতা' দিতে তৎপর হয়েছেন, নয়তো বা তা নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া থেকে সচেতনভাবে বিরত থেকেছেন। আরো যেটা লক্ষণীয় তা হলো, বিজ্ঞজনদের মধ্যে একেক জন ‘সুশীল সমাজ' সম্পর্কে একেক রকম মনগড়া ধারণা নিয়ে অনেকটা অন্ধজনের মতো অগ্রসর হয়েছেন। হাল ফ্যাশনের বৈশ্বিক ভোকাবুলারিতে 'সিভিল সোসাইটি' অভিধাটি আন্তর্জাতিক সব উচ্চ মহলে বিশেষ জোরের সাথে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হওয়ায়, তাদের অনেকেই পরিবর্তিত যুগের নতুন এই ফ্যাশনের কাছে বিনা প্রশ্নে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। একবারও তারা বেশির ভাগই নিজের মনের কাছেও এই প্রশ্নটি তোলেননি যে, ‘সিভিল সোসাইটি' বা 'সুশীল সমাজ' বিষয়টি আসলে কী?
‘সুশীল সমাজ’ অর্থাৎ ইংরেজিতে ‘Civil Society' বলতে কী বোঝায় এবং কাদের নিয়ে তা গঠিত সে ধরনের প্রশ্নের কোনো স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জবাব দিতে 'সুশীল সমাজ' হিসেবে আত্মপরিচয়দানকারীরা মোটেও রাজি হতে চান না। এই রহস্যের(!) পেছনে কারণ কি? এর পেছনে একটি প্রধান কারণ হলো, এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলে যুক্তিতর্কের ফাঁদে পড়ে তারা নিজেরাও সংজ্ঞায়নের বিষয়ে একমত হতে পারবেন না এবং অন্যদেরকেও একমতে আনতে ব্যর্থ হবেন।
দেশের যেসব বিজ্ঞজন ‘সুশীল সমাজ' অভিধাটি উঠতে বসতে হরহামেশা ব্যবহার করে থাকেন তাদেরকে যদি আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করা হয় যে ‘সুশীল সমাজ’ কাকে বলে, তাহলে সকলে এক রকম জবাব দেবেন না। একেক জনের জবাব হবে একেক রকম। আবার একই বিজ্ঞজন একেক বার একেক রকম জবাব দেবেন। তারা একদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এবং অন্যদিকে অস্পষ্ট ধোঁয়াশাপূর্ণ ধারণা নিয়ে, ‘সুশীল সমাজ' অভিধাটি ব্যবহার করে থাকেন। এসব বিজ্ঞজনেরা ‘সুশীল সমাজ'-এর কথা উচ্চারণে নির্বিচার আগ্রহ দেখালেও, এই অভিধাটির সংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাদের প্রবল আলসেমি ও অনাগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অভিধাটিকে তারা অহরহ ব্যবহার করে চলেছেন, অথচ তার সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা কী, তা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই কেন? বিষয়টি খুব রহস্যজনক নয় কি? কিন্তু এই রহস্যের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি কারণের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর একটি প্রধান কারণ হলো, ‘সুশীল সমাজ'-এর সংজ্ঞায়ন করতে গেলে তাদেরকে হয় সর্বসাধারণের কণ্ঠস্বর ও মুখপাত্র হওয়ার স্বঘোষিত দাবি পরিত্যাগ করতে হয়, নয়তো দেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন মুষ্টিমেয় বিজ্ঞবান সামাজিক অভিজাত স্তরের ব্যক্তির দ্বারা স্থির হয় বলে একটি গণতন্ত্র-পরিপন্থী তত্ত্ব হাজির করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ‘সুশীল সমাজে’র দাবিদারদের সমস্যা হলো এখানেই। ‘সুশীল সমাজে’র সংজ্ঞায়নে তাদের এ ধরনের সচেতন অনীহার পেছনে রহস্যের একটি প্রধান কারণ সম্ভবত এটি।
সংজ্ঞায়নের জন্য বেশি চাপচাপির মুখে পড়লে তাদের মধ্যে অনেকে ‘সুশীল সমাজে'র মূল ইংরেজি উৎস ‘সিভিল সোসাইটি’[র ‘সিভিল' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ ‘বেসামরিক’ শব্দটিকে ভিত্তি করে তার সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেন। অতি সরল ও সাদামাটাভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বলে থাকেন যে, ‘সুশীল সমাজ’ হলো দেশের সামরিক পরিমণ্ডলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একটি সামাজিক সত্তা। ‘মিলিটারি’র বাইরে যেমন ‘সিভিল’, তেমনই ‘সামরিকে'র বাইরের সত্তা হলো ‘বেসামরিক’, তথা তারই উন্নত শব্দগত রূপান্তর ‘সুশীল’;-এটাতো অতি সহজ একটি কথা! তাই সংজ্ঞায়ন নিয়ে এতো কথা জিজ্ঞাসার কী আছে? কিন্তু কথা এতো সহজ নয়! ‘সুশীল সমাজ' কাকে বলে সে সম্পর্কে এ ধরনের ব্যাখ্যা মেনে নিলে বলতে হয় যে মন্ত্রী, এমপি, বেসরকারী প্রশাসনের লোকজন, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী-সদস্যবৃন্দ, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীসহ দেশের সব বেসামরিক নাগরিকদের সমন্বয়েই একটি দেশের ‘সুশীল সমাজ' গঠিত। অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর দু'এক লক্ষ সদস্য ব্যতীত দেশের সব নাগরিকই ‘সুশীল সমাজে’র সমান মর্যাদা সম্পন্ন সদস্য। যদি সেভাবেই তাকে সংজ্ঞায়ন করা হয়, তাহলে ‘সুশীল সমাজে'র আলাদা কৌলিন্য ও বিশেষ গুরুত্ব থাকে কোথায়? এমতাবস্থায় ‘সুশীল সমাজে'র গণ্ডি ছোট পরিধির মধ্যে সীমিত রাখার জন্য আরেকটি সহজ ব্যাখ্যা কখনো কখনো উপস্থিত করা হয়। তা হলো, ‘সুশীল সমাজে'র সংজ্ঞা নির্ধারণে ‘অশীল' শব্দের বিপরীতে ‘সুশীল' শব্দের অর্থকে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়ে থাকে। এর দ্বারা শুধুমাত্র শিক্ষিত, মার্জিত, কৌলিন্য সম্পন্ন, ভদ্রশ্রেণীর মানুষ নিয়ে ‘সুশীল সমাজ' গঠিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এক সময়ের কলকাতার ‘বাবু সমাজ' বলে যেভাবে সমাজের একাংশকে চিহ্নিত করা হতো অনেকটা তেমনি! কিন্তু এতেও সমস্যা থেকে যায়। কারণ সেভাবে সংজ্ঞায়িত হলে 'সুশীল সমাজ'ওয়ালাদেরকে সমস্ত সমাজের স্বঘোষিত মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলার ‘গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল’ স্বরূপ দাবি করতে হয়। সে দাবি কে মানবে?
এসব নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ‘সুশীল সমাজে'র চূড়োমনিরা নিজেদের নাম পাল্টে ‘নাগরিক সমাজ’ অথবা ‘জনসমাজ’ ইত্যাদি করার চেষ্টা নানা সময় করেছেন। এখনো তা তারা করে থাকেন। এর দ্বারা ‘সুশীল' বনাম ‘অশীল’ সম্পর্কিত আপত্তিকে কোনক্রমে উৎড়ানোর প্রয়াসে কিছুটা সফল হলেও, উত্থাপিত অন্যান্য প্রশ্ন ও আপত্তির সদুত্তর দিতে তারা অপারগ হন। কারণ, গোড়ার সমস্যাটি হলো, “সিভিল সোসাইটি' সম্পর্কিত ধারণাতেই তাদের
লগইন করুন? লগইন করুন











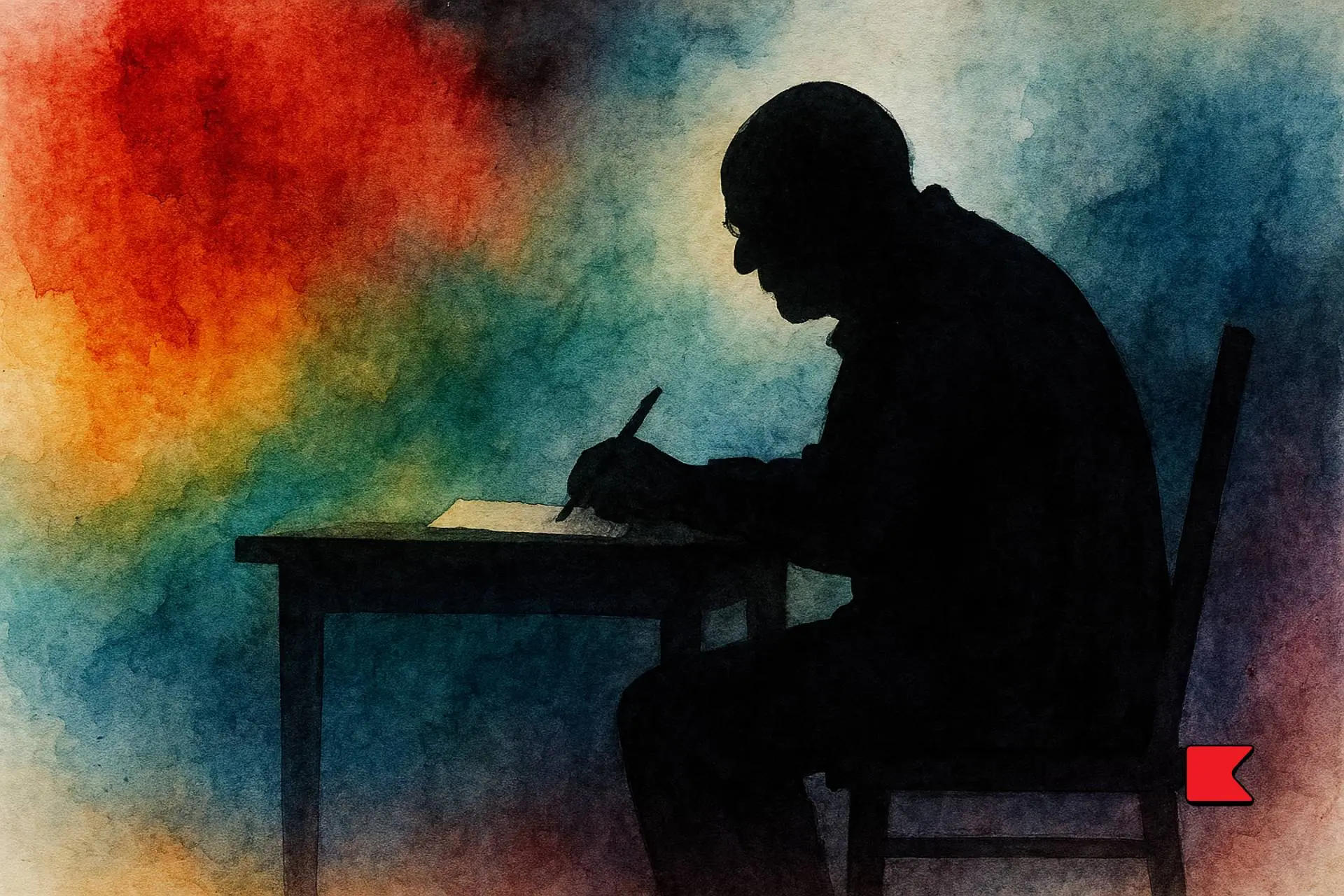

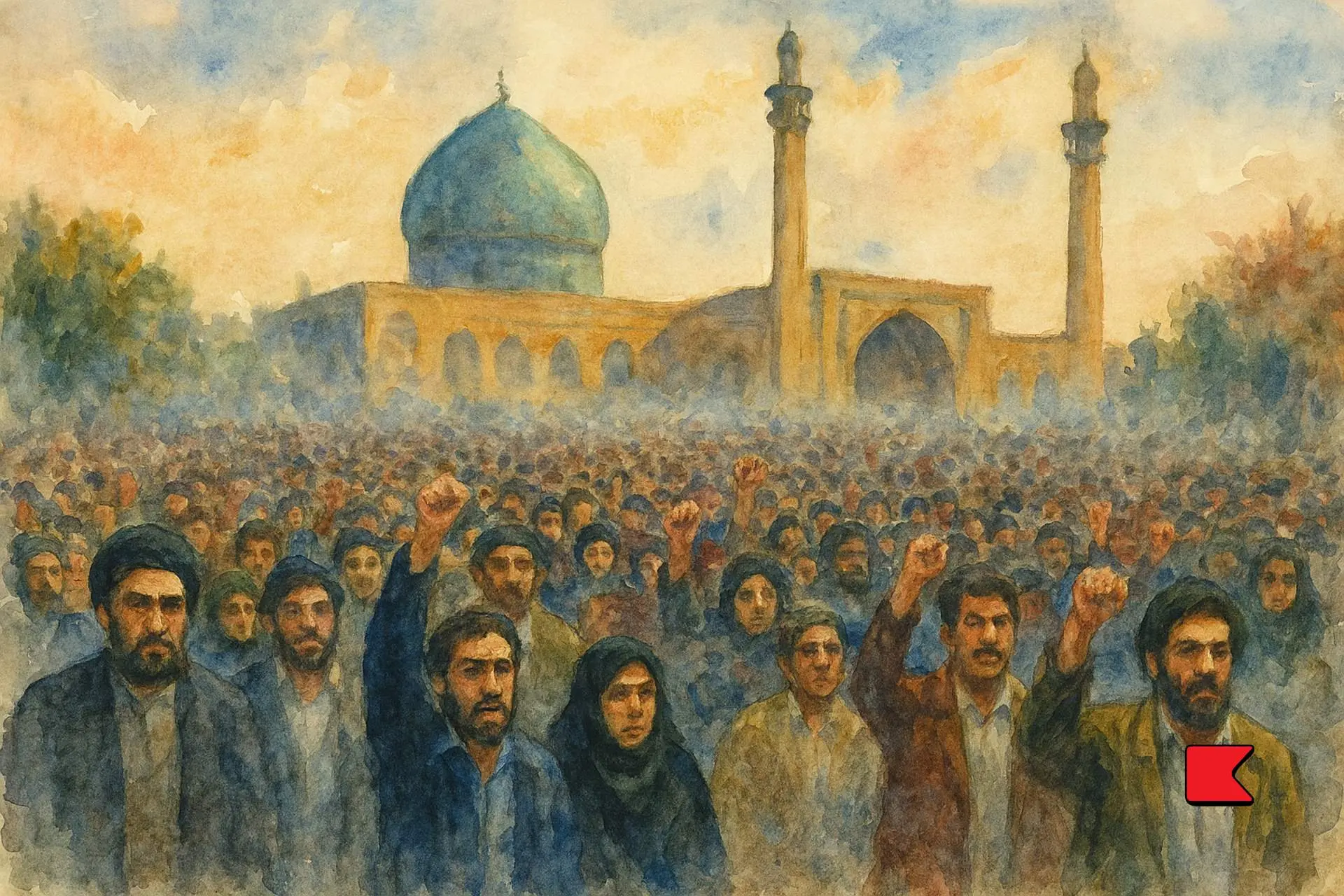









03 Comments
Karla Gleichauf
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment
M Shyamalan
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment
Liz Montano
12 May 2017 at 05:28 pm
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment