প্রাচীন মিসরের মেহনতী মানুষ
প্রাচীন মিসরের জনৈক ভদ্রলোক তার ছেলেকে নিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিতে যাচ্ছেন আর পথে পথে উপদেশ দিয়ে চলেছেন, বাপুরে, খেটেখুটে মন দিয়ে লেখাপড়া করো, যাতে লেখাপড়া শিখে একজন লিপিকার (ঝপৎরনব) হয়ে উঠতে পার। আমাদের এই সমাজে পেটের ধান্দা মিটাবার জন্য নানা জনে নানারকম পেশা নিয়ে মেহনত করে চলেছে। কিন্তু এদের মধ্যে একমাত্র লিপিকারেরাই সুখে আছে, আর সকলের দুর্দশার চূড়ান্ত। কর্মকারদের মধ্যে থেকে কেউ রাষ্ট্রদূতের পদ পেয়েছে, এ আমি কোনো দিন দেখিনি। দেখছি তো কামারদের—এরা দিনের পর দিন এদের চুল্লির আগুনের সামনে বসে কাজ করে চলে, এদের হাতের আঙ্গুলগুলো কুমীরের নখের মতো বেঁকে যায় আর এদের গা থেকে মাছের ডিমের চেয়েও বেশী দুর্গন্ধ ছড়ায়... রাজমিস্ত্রীরা কি সব শক্ত শক্ত পাথর ভেঙ্গে কাজ করে। সারাদিন এইভাবে কাজ করার পর তাদের হাত অবশ হয়ে আসে, অবসন্ন হয়ে আসে দেহ-রাত্রিবেলা তারা কুঁকড়ে-মুকড়ে পড়ে থাকে, পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত ওইভাবেই ঘুমিয়ে কাটায়। তার হাঁটু আর পিঠের শিরদাঁড়া যেন ভেঙ্গে গেছে, উঠে দাঁড়াবার মতো জোর নেই। নাপিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকের চুল-দাড়ি কেটে চলে। একমাত্র খাওয়ার সময় ছাড়া তার একটু বসবার ফুরসুত নেই। কাজের সন্ধানে সে বাড়ি বাড়ি ছুটাছুটি করে বেড়ায়। পেট ভরবার জন্য সে হাত দুটোকে ক্ষয় করে চলে। চাষী দিনের পর দিন এক কাপড়েই কাটিয়ে দেয়, বদল করবার মতো দ্বিতীয় কাপড় তার নেই। তার হাতের আঙ্গুলগুলি সব সময়ে কাজে ব্যস্ত, গরম বাতাসে হাত দুটো শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। যখন সে একটু অবসর পায়, ক্ষেতের কাদামাটির উপর বসেই বিশ্রাম নেয়। যখন সে সুস্থ থাকে তখন গৃহপালিত পশুদের সঙ্গেই তার দিন কাটে। আবার যখন অসুস্থ হয়, তখনও সেই পশুদের মধ্যেই খালি মাটির উপরে শুয়ে থাকে। রাত্রিতে সে খুব কমই বাড়িতে যায়। আর যদিওবা যায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসতে হয়। কাজেই লেখাপড়ার দিকে ভালো করে মন দাও, এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এমন পেশা আর একটিও নেই।
একাদশ রাজবংশের আমলে লিখিত ‘দুয়াউফ-এর ছেলে খেতীর শিক্ষামালা’ নামক বইটিতে তখনকার দিনের মিসরের সাধারণ মেহনতী মানুষের নিদারুণ জীবন কথার চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছিল।
মিসরের সমৃদ্ধ রাজধানীর এক প্রান্তে চাঁদের মধ্যে কলংকের মতো বস্তির মধ্যে বাস করত হস্তশিল্পী আর কারিগরেরা। নিজ নিজ পেশার পরিবর্তন করা এবং নাগরিক ব্যাপারে মাথা ঘামানো এদের পক্ষে আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল। ফ্যারাওয়ের রাজকীয় ভূসম্পত্তি বা জায়গীরদারদের জায়গীরে যারা জমি চাষের কাজ করত তারা ছিল ভূ-দাস। এদের ক্রীতদাস বলা যায় না এই জন্য যে তাদের বিকি-কিনি করা চলতো না। এবং যত সামান্যই হোক না কেনো, তাদের নিজস্ব বাড়ি ছিল। কিন্তু তারা জমির সঙ্গে এমনভাবে গাঁটছড়ায় বাঁধা ছিল যে, জমির মালিকানা বদলে গেলে তারা আপনা থেকে অপর মালিকের হাতে গিয়ে পড়তো। মালিকদের লাভের জন্য তাদের দিয়ে অপরের কাছে ভাড়া খাটানোও চলত। নাগরিক হিসাবে তাদের কতকগুলি বিধিসম্মত অধিকার ছিল বটে, কিন্তু তা শুধু কথার কথা, উচ্চতর শ্রেণীগুলি সব সময়ই নানাভাবে তাদের নির্যাতন করত। এরা ক্রীতদাস নয়, কিন্তু ক্রীতদাসের চেয়ে কম কিসে?
মিসরের মেহনতী জনসাধারণ এইভাবে অকথ্য দুঃখ-দুর্দশা, অভাব ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতো। এরা ছাড়া ক্রীতদাসরাও ছিল। বিদেশী ও যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করে নিয়ে আসা হতো। কিন্তু মিসরের অর্থনীতির উপর তাদের প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। সমসাময়িক জগতে সভ্যতার ক্রমবিকাশে ক্রীতদাস ব্যবস্থার যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, মিসরের ক্ষেত্রে তা ছিল গৌণ। ব্যক্তিগত ভাবে ক্রীতদাস রাখার সুযোগ ছিল না বললেই চলে! ফ্যারাওরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী নিয়ে এসে তাদের প্রাসাদের তাঁতী, পাচক ইত্যাদির কাছে এবং মন্দিরের ভূসম্পত্তিকে ব্যক্তি বিশেষের হাতে কি করে সমর্পণ করা যেতে পারে, সেই জন্যই পরিবারগতভাবে ক্রীতদাস রাখার ব্যবস্থা সেখানে চালু হতে পারেনি। সমকালীন জগতে এই ব্যাপারে মিসরীয় সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।
কালক্রমে এই যুদ্ধবন্দী ক্রীতদাসের অবস্থার রূপান্তর ঘটেছিল। তৃতীয় রামেসিসের প্রায় একলক্ষ যুদ্ধবন্দী ক্রীতদাস ছিল। এরা মন্দিরের ভূসম্পত্তি চাষের কাজ করতো। ফ্যারাও পরে এদের করদাতা ভূ-দাসে পরিণত করে সমাজের একটা নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করলেন। এদের বিরাট বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ গঠনের কাজে লাগানো হতো। তাছাড়া এদের ব্যাপক হারে সেনা দলভুক্ত করা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে মিসরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির দেখা দিয়েছিল। রাজ শক্তি ও পুরোহিত শক্তির অর্ন্তদ্বন্দ্ব বাড়তে বাড়তে অবশেষে পুরোহিত শক্তি রাজশক্তির প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়াল- ফ্যারাও নিজে এই সংকটাপন্ন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে আত্মরক্ষার জন্য এই যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটি নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন। এই দেহরক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আপনাকে সুরক্ষিত করে তুললেন। এই ক্রীতদাসদের সন্তানদের রাজসভায় ও সরকারে উচ্চ পদে নিয়োগ করে নিজের বাহুকে দৃঢ়তর করে তুলছিলেন। আর এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যুদ্ধবন্দী ক্রীতদাস শ্রেণী ফ্যারাওয়ের অনুগ্রহ লাভের নতুন মর্যাদায় উন্নীত হয়ে গেলো।
সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য ক্রীতদাস প্রথা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মিসরের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য তার ইতিহাস এক স্বতন্ত্র পথ ধরে এগিয়ে চলছিল। মিসরের অর্থনীতি ও সমাজ সংগঠনের বিশেষ প্রকৃতির জন্য সেখানে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। নীল নদের উপত্যকা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, এখানে কৃষি মজুরের অভাব ছিল না। তার উপর শাসক শ্রেণী নিজেদের শ্রেণী স্বার্থকে হাসিল করবার জন্য ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণকে শোষণ করবার এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। তার ফলে মেহনতী জনসাধারণ নামে যাই হোক না কেনো, কার্যত প্রায় ক্রীতদাসের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। সে এক নির্মম আর করুণ কাহিনি। আর তার প্রতিক্রিয়া যখন প্রচণ্ড আর হিংস্র মূর্তি নিয়ে দেখা দিল তখন সমগ্র সমাজ ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেলো। কিন্তু সে আর এক ইতিহাস।
মানব সভ্যতার উষালগ্নে, সত্যেন সেন ও আসাহাবুর রহমান, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭০
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



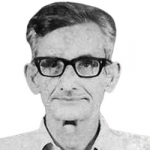















Comments