ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা
১৮০৩ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। ভারতের রাজধানী দিল্লী শহর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এসে গেল, আসলে এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। বহুদিন আগে থেকেই ভারতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাকে এই অনির্বায পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। যাদের দেখবার মত চোখ ছিল তারা দেখতেও পাচ্ছিলেন যে তার সর্বদেহে ক্ষয়রোগের লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে। এ এক বিরাট মহীরুহ, যার ভিতরকার সমস্ত সার পদার্থ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাহলেও সাধারণের দৃষ্টির সামনে এতদিন সে তার প্রভুত্বব্যঞ্জক মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, অবশেষে সেই মহীরুহের পতন ঘটল; চমকিত হয়ে উঠল সবাই। দিল্লীশ্বরেরা জগদীশ্বরেরা শেষকালে এই হলো তার পরিণতি।
মুঘল সাম্রাজ্য সত্য কথা বলতে গেলে একেবারে বিনা বাধায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খাস তালুকে পরিণত হয়ে গেল। বহুকাল আগে থেকেই ভারতের অপরিমিত ধনসম্পদের সত্য কল্পিত কাহিনী সারা বিশ্বময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। তার মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় জলদস্যু ও বণিকের দল একের পর এক উন্মত্তের মত ছুটে আসছিল এবং তাদের পরস্পরের হানাহানির ফলে সমুদ্রের জল ও স্থলভূমি রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠেছিল অবশেষে তার চূড়ান্ত অবসান ঘটল। ভাগ্যের নির্দেশে যারা আগে এসেছিল তারা পিছনে পড়ে গেল। আর ভাগ্যলক্ষ্মী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠে তাঁর জয়মালা পরিয়ে দিলেন।
চমকিত হয়ে উঠল সবাই। যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা জেগে উঠল, যারা বসে ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এই পর্যন্তই, এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত শক্তি তাদের ছিল কি? হয়তো তা ছিল, কিন্তু এই উন্নততর মারণাস্ত্রে সু-সজ্জিত শক্তির বিরুদ্ধে কে তাদের সংগঠিত করবে, কে তাদের নেতৃত্ব দেবে? তাদের নেতৃস্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর প্রভুরা তখন মধুপানে মত্ত হয়ে বিলাস ব্যসনে ডুবে আছেন। কে জানে হয়তো তখনও তারা নিশ্চিত মনে সুখ-স্বপ্ন দেখছিলেন দিল্লী অনেক দূর।
প্রতিরোধ কি একেবারেই আসেনি? বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কি ক্রমে ক্রমেই জমে উঠছিলো না? কিন্তু বিক্ষোভ যতদিন পর্যন্ত চাপা দেওয়া আগুনের মত ধুমায়িত হয়ে উঠতে থাকে, ততদিন ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ এল মুসলমান উলেমা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে।
মূলত ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকেই বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসন অসহনীয় বলে তাদের কাছে মনে হয়েছিলো। কিন্তু যে কোনো ধর্মই হোক, ধর্মীয় জীবন বৈষয়িক জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেনা। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য।
প্রথম প্রতিবাদ তুললেন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ। মুসলমানদের হাত থেকে বাদশাহী শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কাজেই আঘাতটা মুসলমানদের বেশী করে বাজবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই তাদের এই বিরোধিতা হয়তো এই ধর্মীয় নেতার অভিমতের মধ্য দিয়েই রূপ নিয়েছিলো।
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ স্পষ্টই রায় দিলেন যে, ইসলাম তাঁর ধর্মীয় বিধান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, এই দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই এই পরাধীন পরিবেশে ইসলাম কখনই সজীবতা ও স্ফুর্তি লাভ করতে পারে না। তার এই সূত্রটির যুক্তিযুক্ত রূপায়ণ ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে তার শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে এসেছিলেন। সেই দীর্ঘায়িত সংগ্রামের অতি সামান্য অংশই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আর তা খণ্ডে খণ্ডে ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে পরিচালিত হয়ে এসেছিলো। তাঁদের চরিত্র ও ভূমিকা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এই জেহাদকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া চলে কি না এ বিষয়ে রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্-এর পুত্র ও তার পরবর্তী ধর্মগুরু আবদুল আজিজ তাঁর পিতার এই সূত্রটিকে কার্যকরী রূপে সম্প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় মুসলমানরা এই পরাধীন অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এই পরিবেশের মধ্যে কোনো প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে যথাযথভাবে ধর্মাচরণ করে চলা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে ভারত হচ্ছে ‘দার-উল-হরব’ অর্থাৎ ‘যুদ্ধরত দেশ’। তিনি এদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক ফতোয়া জারী করলেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদে শরীক হওয়া তাদের সকলের কর্তব্য। আর ব্রিটিশ শক্তিকে যদি তারা তাদের তুলনায় অনেক বেশি প্রবল বলে মনে করে অথবা এই সংগ্রামে যদি জয়লাভের আশা না থাকে, তবে তারা যেন অন্যান্য স্বাধীন মুসলমান দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বাইরের সেই সমস্ত শক্তির সাহায্য নিয়ে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতারিত করতে হবে। বাইরের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি যে এ বিষয়ে তাদের অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করবে এ সর্ম্পকে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না।
শাহ্ আবদুল আজিজের এই ফতোয়া ভারতের মুসলমানদের এক অংশের মনে সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর এই আহ্বানে তারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও মুসলামান রাষ্ট্রগুলির বাস্তব অবস্থা সর্ম্পকে ধর্মগুরু আবদুল আজিজের কোনো স্পষ্ট ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিলো না। আর যারা তাঁর এই ফতোয়াকে মান্য করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছিলেন এবং এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে যে সাহস, সংগঠনশক্তি ও আত্ম-ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই উত্তরাধিকার আমরা গর্বের সাথে বহন করি। এই ইতিহাসকে অবহেলা করে বিস্মৃতির তলায় চাপা দেওয়া এক জাতীয় অপরাধ।
দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী এই ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল ক’জনেই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়। ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নামকরণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আবদুল ওয়াইয়ের প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কোনো সংযোগ ছিলোনা। তবুও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা ‘ওহাবী আন্দোলন’ বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।
সৈয়দ আহমদ উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর অনুবর্তী ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীনতার আদর্শ থেকে তিনি তাঁর আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৮০৮ সালে তিনি তার শিক্ষা সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে আসেন এবং বিবাহ করেন। তিনি যে আদর্শ নিয়ে পথে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্য তিনি “টঙ্ক’ রাজ্যের আমীরের কাছে এসে তাঁর সৈন্য বিভাগে যোগদান করেন। ‘টঙ্ক’ তখনও স্বাধীন রাজ্য ছিলো। তার ভবিষ্যৎ সংগ্রামী জীবনের পক্ষে এটা খুবই কাজে লেগেছিলো। এখানেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। রণনীতি ও রণকৌশল সর্ম্পকেও তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেন। কিন্তু ১৮১৭ সালে ‘টঙ্ক’ রাজ্যের আমীর যখন ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন, তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন।
‘টঙ্ক’ রাজ্য থেকে ফিরে এসে তিনি উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলা-গুলিতে ভ্রমণ করলেন এবং মীরাট, মজঃফরনগর ও সাহারানপুর জেলার উল্লেখযোগ্য শহর ও গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করলেন। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণে তিনি এলাহাবাদ, বারানসী, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ জেলাগুলি এবং তৃতীয়বারের ভ্রমণে রোহিলাখণ্ড অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন।
তিনি যেখানেই গেছেন সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। তাঁর উপদেশ শোনার জন্যে বহুলোক এসে জমায়েত হতো। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর মূল উপদেশ ছিলো দুটি প্রথমতঃ খোদার কোনো শরিক নেই, তিনি একেশ্বর, একচ্ছত্র এবং ফেরেস্তা, ধর্মগুরু, পয়গম্বর বা পীর যেই হোক না কেন, খোদা আর মানুষের মধ্যে কেউ মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। মানুষকে সরাসরি খোদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সত্যকারের মুসলমান বৃহৎ ব্যাপারেই হোক বা সামান্য ব্যাপারেই হোক কোরান
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



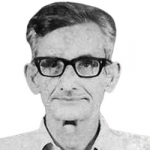

















Comments