ঢাকা শহরে বাঙ্গালি ধাঙ্গর জন্মের ইতিহাস
কবি সত্যেন দত্ত বহুদিন আগে মেথরদের উদ্দেশ করে ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন ‘কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি?’ কিন্তু তা হলেও মেথর সম্প্রদায় আমাদের সমাজে এখনও অশুচি বলেই গণ্য। আর এই বৃত্তি অবলম্বন করার ফলে যেই পরিবেশের মধ্যে তাদের বাস করতে হয়, তা মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের পক্ষে একেবারেই প্রতিকূল। অথচ তারা তাদের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিলে সারা শহর-জীবন অচল হয়ে পড়বে। জননীর মতো, চিকিৎসকের মতো শহর-জীবনকে যারা সর্বভাবে পরিচ্ছন্ন ও ক্লেদমুক্ত করে চলেছে তাদের কাজ কেমন করে নীচ ও মর্যাদাহানিকর হতে পারে? যাদের নিরলস সেবা সমাজের শুচিতাকে রক্ষা করে চলেছে, তারাই হলো অশুচি! মোটামুটি সবাই এই দৃষ্টি নিয়েই তাদের দেখে থাকে। আর তারা নিজেরাই নিজেদের সম্বন্ধে মনে মনে এই রকম ধারণাই পোষণ করে।
এই জন্যই বাংলাদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান, কেউ এ কাজ করতে চাইত না। চাইত না বললেও যথার্থ বলা হবে না। তাদের মধ্যে কেউ এ কাজ করত না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জেলখানা। জেলখানার সমাজ বাইরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অনেকদিন আগে থেকেই জেলখানায় কয়েদীদের দিয়ে মেথর বা সাফাইয়ের কাজ করানোর রেওয়াজ চলে আসছিল। কিন্তু এই রেওয়াজটাকে চালু করতে জেলকর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। বিড়ি, বাড়তি মাছ মৎস্য, তেল, গুড় এবং সর্বশেষে মাসিক দু’টাকা বেতন। এই সব কিছুর প্রলোভন দেখিয়ে তবে তাদের দিয়ে এই কাজ করানো সম্ভব হয়েছে। জেলখানার মধ্যেও একটা সমাজ আছে। সেই সমাজেও এই সাফাইয়ারা অন্যান্য কয়েদীর দৃষ্টিতে অশুচি বলেই গণ্য। তবে এই সাফাইয়ারা মনে করে যে, মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের গায়ে এই কলঙ্কের চিহ্ন লেগে থাকবে না। তবে জেলে থাকার সময় তারা যে জেলখানায় মেথরের কাজ করে, সে খবরটা যাতে বাইরের লোকে জানতে না পারে, সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না।
কিন্তু আজ আপনি আমাদের এই শহরের দিকে লক্ষ করে দেখুন। দেখবেন বহু বাঙ্গালি শ্রমিক এই কাজে নেমে গিয়েছে। তাদের মধ্যে পুরুষও আছে, মেয়েও আছে। এদের এক পুরুষ আগেকার লোকেরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের যে এই পথে নেমে আসতে হবে, এ কথা কল্পনাও করতে পারত না। গত কুড়ি বাইশ বছরে এই অঘটনটি ঘটে গেছে আমাদের এই গোঁড়া, রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এ যে কি এক বিরাট পরিবর্তন, তার তাৎপর্য বাইরের লোকে বুঝবে না, আমরা বুঝি।
এ ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে মেথর না বলে ধাঙ্গর শব্দটির ব্যবহার করাই সঙ্গত। ধাঙ্গরদের মধ্যে তিনটা ভাগ: ১. ঝাড়ুদার বা সুইপার, যারা রাস্তাঘাট ঝাঁট দেয়, ২. যারা ড্রেন পরিষ্কার করে। ৩. মেথর অর্থাৎ যারা ময়লা পরিষ্কার করে নিয়ে যায়।
এরা সবাই মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে চাকরি করে। আমাদের ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম হয়েছে ১৮৬৪ সালে। অবশ্য আজকালকার দিনে মিউনিসিপ্যালিটি বলতে যেই স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বুঝায়, তখনও তার সৃষ্টি হয় নি; শহরটাকে দেখাশোনা করার জন্য সরকার কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করতেন। তাঁরাই ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ। প্রথমদিকে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তিনটি কাজের দায়িত্ব ছিল: কন্সারভেন্সি অর্থাৎ শহরকে সাফ-সাফাই রাখা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা। ২. পানি সরবরাহ ও ৩. বিদ্যুৎ সরবরাহ। পরবর্তী দুটি নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বলতে প্রধানতঃ কন্সারভেন্সিকেই বোঝাত।
শহরকে সাফসাফাই রাখতে হলে ধাঙ্গরদের একান্ত প্রয়োজন অথচ মেথরের কাজ দূরে থাক; ঝাড়ুদারের কাজেও কোনো বাঙালি হিন্দু বা মুসলমানকে পাওয়া যেত না। এটা অনুমান করলে ভুল করা হবে না যে, মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হবার দীর্ঘকাল আগে থেকে যুক্ত প্রদেশ (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) ও বিহারে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণিত হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক শ্রেণীর লোক আমাদের এখানকার শহরাঞ্চলে এসে এ কাজ করত। শুধু বাংলাদেশে নয়, উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র এরা ছড়িয়েছিল।
মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। আবার কেউ কেউ চুক্তি হিসাবে বা রোজ হিসাবে অস্থায়ীভাবে কাজ করত।
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা শহর পূর্ববঙ্গের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করল। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মিউনিসিপ্যালিটির শক্তি ও মর্যাদা অনেক বেশী বেড়ে গেল। সত্য কথা বলতে গেলে এই সময় থেকে মিউনিসিপ্যালিটি নতুন জীবন লাভ করল। এই বছর ঢাকা শহরকে ৭টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছিল। শহরের সাফ-সাফাই ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার জন্য একটি স্বাস্থ্য বিভাগ গঠন করা হয়েছিল। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন হেল্থ অফিসার। তারপরেই সাত ওয়ার্ডের জন্য সাতজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও সাতজন কন্সারভেন্সি ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন ডিপো ইন্সপেক্টর। এ ছাড়া সে সময় ৭০/৮০ জন ধাঙ্গর নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। এদের সবাইকে নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ গঠিত ছিল। ধাঙ্গরদের মধ্যে ঝাড়ুদারদের বেতন ছিল ২৫ টাকা, যারা ড্রেন পরিষ্কার করত তাদের ৭ টাকা আর মেথরদের ১৫ টাকা।
মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার কাজের মাত্রা বেড়ে চলার সাথে সাথেই ধাঙ্গরদের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলল। বাইরে থেকে ধাঙ্গর আমদানী না করে এই চাহিদা মিটানো সম্ভব ছিল না। কোন্ সময় থেকে প্ল্যান মাফিক এই ধাঙ্গর আমদানী শুরু হয়েছিল, সে সম্পর্কে আপাতত কোন আলোকপাত করতে পারছি না। চা-বাগানের আড়কাঠিরা নানা জায়গা থেকে দুঃস্থ সরলমনা লোকদের যেভাবে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এসে চা-বাগানে ভর্তি করত। ঠিক সেইভাবে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙ্গর যোগাড় করে নিয়ে আসার জন্য বাইরে মিউনিসিপ্যালিটির আড়কাঠিদের পাঠানো হতো। ধাঙ্গর সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র ছিল দুটি-যুক্ত প্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) কানপুর আর প্রাক্তন মাদ্রাজ; ওরা, বিশেষ করে সুদূর মাদ্রাজী ধাঙ্গরেরা দুটো ভাতের আশায় জন্মভূমির মায়া ছেড়ে এদেশে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। তাদের এই নতুন মাতৃভূমিকে তারা প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে। কিন্তু তার বিনিময়ে না পেয়েছে সুস্থ জীবন আর শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো, না পেয়েছে মানুষের মর্যাদা। সত্য কথা বলতে গেলে, আমাদের দৃষ্টিতে এরা মানুষ নয়; সচল যন্ত্র মাত্র।
সম্ভবতঃ ১৯২০ সালের পর থেকেই বাইরে থেকে ধাঙ্গর আমদানী শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার কোনো উল্লেখ বা বিবরণ আমরা পাই না। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই আড়কাঠিদের কার্যকলাপের প্রথম পরিচয় পাই। ১৯২৫ সালে চন্দ্রবাবু, হারানবাবু ও আবদুল জব্বার মিঞা নামে তিনজন জাদরেল কনসারভেন্সি ইন্সপেক্টার ছিলেন। এরা আড়কাঠি হিসাবে ধাঙ্গর সংগ্রহের জন্য কানপুর আর মাদ্রাজ যেতেন। তারপর সেখানকার বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সরলমনা লোকদের বিনামূল্যে ঘরবাড়ি, সস্তায় ভালোখাবার আর ভালো মদ এবং আনন্দময় জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। একবার কোনোমতে নিয়ে এসে ফাঁদে ফেলে দিতে পারলে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন ছিল।
জংলা হাতীকে ধরে এনে পোষ মানাবার জন্য যেমন মাদী হাতীর দরকার হয়, এরাও তেমনি এদের বশ করার জন্য অনুগত ও দালাল শ্রেণীর হিন্দুস্থানী ও মাদ্রাজী ধাঙ্গরদের সঙ্গে করে নিয়ে যেত।
ভূগর্ভস্থ নর্দমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে ঢাকা শহরে মল নিস্কাশনের কি ব্যবস্থা ছিল এখানকার দিনের অনেকেরই তা জানা নেই। কেউ কেউ শুনলে হয়তো বা চমকে উঠবেন। বাড়িতে বাড়িতে খাটা পায়খানা ছিল। মলাধারা হিসাবে বড় বড় গামলা ব্যবহার করা হতো। মেথররা কয়েকদিন বাদে বাদে গামলায় সঞ্চিত মল তাদের গরুর গাড়ীতে করে নিয়ে যেত। এখন যেটা আমাদের পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ময়দান, আগে সেই জায়গাটার নাম ছিল মীরনজল্লা। এখান থেকে হধৎৎড়ি মধুঁব একটি রেল লাইন রেলওয়ে হাসপাতাল হয়ে শাহবাগ হোটেলের পাশ দিয়ে
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



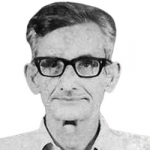
















Comments