ঢাকা শহরের বাইশ পঞ্চায়েত
ঢাকা শহরের সুরসিক লোকেরা এককালে তাদের শহরের আর একটা নামকরণ করেছিল-‘বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি।’ সেই নাম আজ বিস্মৃতির পথে হারিয়ে গেছে। এই বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলির উপরে বাইশ পঞ্চায়েত তার সার্বভৌম কর্তৃত্ব নিয়ে সমাজ রক্ষার কাজ চালাত। তাদের কথার উপর কারুর কথা বলা চলত না। বাইশ পঞ্চায়েত আজও বেঁচে আছে। কিন্তু একে বেঁচে থাকা বলা চলে না। তার মূলগুলো একটা একটা করে মরে যাচ্ছে, ডালগুলো অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়েছে। পাতাগুলো খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। তার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে এলো বলে। কালের অমোঘ বিধান কে লংঘন করতে পারে। এমন প্রবল প্রতাপশালী সরদার আর তাদের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা! কালের বিধানে তাদেরও আজ সসম্মানে সরে গিয়ে নবাগত ইউনিয়ন কমিটিকে জায়গা করে দিতে হচ্ছে। অবশ্য ইউনিয়ন কমিটি প্রবর্তনের আগেই, এখানকার বাইশ-পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা নিজ থেকেই ‘উইদার এওয়ে’ অর্থাৎ শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছিল। চেষ্টা করলেও এই স্বাভাবিক মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যেত না। যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এক সময়ে সজীব ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করে চলেছিল বহুদিন আগে তাতে ভাঙ্গন ধরেছিল। সেই জন্যই তা আজ দাঁড়াবার মতো মাটি পাচ্ছে না। নতুন মুদ্রার পাশাপাশি পুরানো মুদ্রার মতো পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা আজও কোনোমতে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু পুরানো মুদ্রার মতো তার দিনও শেষ হয়ে এসেছে। ‘বাইশ পঞ্চায়েত’ আজও লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কিন্তু সেদিন হয়তো দূরে নয়, যেদিন ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে এই কথাটি অপরিচিত হয়ে যাবে।
‘পঞ্চায়েতী’ কথাটি পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। ‘পাঁচ’ সংখ্যাটি আমাদের এই অঞ্চলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নানা ব্যাপারেই পাঁচ সংখ্যাটির প্রয়োগ দেখা যায়। এর পিছনে রয়েছে ‘হাতের পাঁচ আঙ্গুল’ এটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। কিন্তু সমাজ পরিচালনার জন্য এই যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা, এটা আমাদের এদিককার কোনো অভিনব আবিষ্কার নয়। এই ব্যবস্থা সার্বজনীন। পৃথিবীর সব দেশেই এর প্রচলন ছিল বা আছে। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ এই ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে বাধ্য হয়েছে। সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু আগে থেকেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে এসেছে।
ফরাশগঞ্জ ইউনিয়ন কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব আহমদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে বাইশ পঞ্চায়েত সম্পর্কে আলাপ হচ্ছিল। এখানে এ সম্পর্কে যেটুকু তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা তাঁর কাছ থেকেই সংগৃহীত। অবশ্য তথ্যের পরিমাণ অপ্রচুর। প্রাচীন দিনের নথিপত্র সুরক্ষিত না থাকার ফলে এই বাইশ পঞ্চায়েতের উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতির ইতিহাসটা আমাদের কাছে একেবারেই ঝাপসা। এই ইতিহাসটা পেলে তা থেকে এখানকার অতীত দিনের সামাজিক জীবনের অনেক ছবি হয়তো আমরা পেতে পারতাম।
আহমদুল্লাহ সাহেব বলছিলেন, ঢাকা শহরের সরদারী প্রথা ঢাকার নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মধ্যে চলে আসছিল। কথাটা শুনলে মনে হতে পারে, এখানকার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা নবাব পরিবারেরই সৃষ্টি। কিন্তু এ কথাটা তো আর সত্য হতে পারে না। গত শতাব্দীর কোনো এক ভাগে হয় তো প্রথমাংশে এই নবাব পরিবার বাইরে থেকে এখানে এসেছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা তার বহু আগে থেকে প্রচলিত হয়ে এসেছে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কেননা, কি গ্রামাঞ্চলে কি পুরানো শহরে সর্বত্রই প্রাচীনকাল থেকে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে আসছিল এবং প্রধান বা মহৎ বা মাতবর বা সরদাররা সেই ব্যবস্থার মূল ভূমিকা গ্রহণ করে আসছিলেন। কিন্তু তা হলেও ঢাকা শহরের বাইশ পঞ্চায়েতের সঙ্গে নবাব পরিবারের কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিল, এই ধারণাটাকে একেবারে অসত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই বাইশ পঞ্চায়েত কবে সৃষ্টি হয়েছিল, সে ইতিহাস আজও আমাদের জানা নেই। তবে যে কোনোভাবইে হোক, এই বাইশ মহল্লার মুসলমানদের উপর এই নবাব পরিবার বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছিলেন। এই প্রভাবের জোরে তাঁরা এদের নিজেদের বিচার-বিবেচনা ও ইচ্ছানুযায়ী সুপথে বা কুপথে পরিচালিত করতে পারতেন। এরা ছিলেন বাইশ পঞ্চায়েতেরর একচ্ছত্র ও অবিসংবাদিত নেতা। এদের আশীর্বাদ নিয়ে সরদাররা সরদারের পদে অভিষিক্ত হয়ে এসেছেন এবং মহল্লা থেকে কোনো সরদারের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠলে একমাত্র এরাই তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। এ থেকে এ কথাটা অনুমান করা হয়তো ভুল হবে না যে, ‘বাইশ পঞ্চায়েত’ ব্যবস্থার সৃষ্টির গোড়া থেকেই নবাব পরিবারের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ইতিহাস চলে আসছে। এমনও হতে পারে, এই নবাব পরিবারের উদ্যোগেই এক সময় ঢাকা শহরের মুসলমান এলাকাকে বাইশটি মহল্লায় ভাগ করা হয়েছিল অথবা পুনঃসংস্কার সাধিত হয়েছিল।
বর্তমানে ঢাকা শহরে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা থেকে তার অতীত দিনের শক্তি ও মহিমার কোনোই পরিচয় পাওয়া যাবে না। আমরা আধুনিক যুগের লোকেরা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ও তার বিধিবিধান সম্পর্কে সচেতন। সচেতন না থাকলে পুলিশ ও বিচার বিভাগ সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সচেতন করে দেয়। কিন্তু পঞ্চায়েতী বিধিবিধানের পিছনে সরকারী দণ্ডনীতির ব্যবস্থা না থাকলেও যে কোনো ব্যক্তি, সে যতই প্রতাপশালী হোক না কেনো, তাকে পঞ্চায়েতের রায় অবনত শিরে মেনে চলতে হতো।
প্রতিটি মহল্লায় স্থানীয় পাঁচজন বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ লোককে নিয়ে মহল্লা পঞ্চায়েত গঠিত হতো। এই পাঁচজনকে বলা হতো ‘লায়েক বেরাদর’। এই মহল্লা পঞ্চায়েত মহল্লার সরদারের উপদেষ্টা কমিটির মতো কাজ করত। এরা সরদারের কাজে সাহায্য করতেন।
সরদারের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত-সর্ব ব্যাপারেই সরদারের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল। প্রথমতঃ, আগেকার দিনে মামলা-মোকদ্দমা খুব কমই হতো। কোনো কিছু নিয়ে বিবাদ বাধলে সরদার সালিসি করে তার নিষ্পত্তি করে দিতেন। এই সালিসির রায় মেনে নিতে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই বাধ্য থাকত। পঞ্চায়েতী বিধিবিধানের পিছনে সরকারের শাসনের ভয় না থাকলেও সামাজিক শাসনের ভয় ছিল। সালিসির বা অন্য কোনোরূপ রায় অমান্য করলে মহল্লার সমাজে তার নল-পানি (হুঁকোপানি) বন্ধ হয়ে যেত। তার বাড়িতে বিয়ে ও অনুষ্ঠানে কেউ যোগ দিত না বা সহযোগিতা করত না। এখনকার দিনে এই শাসনের মর্ম আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি না। কিন্তু আগেকার দিনে অবাধ্য লোককে শায়েস্তা করার পক্ষে এ ছিল এক মারাত্মক অস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, কোনো বাড়িঘরের সীমানা নিয়ে কোনো গোলযোগ দেখা দিলে বা সম্পত্তির বাঁটোয়ারার ব্যাপারে সরদারকে মাপ জোক করে মীমাংসা করে দিতে হতো। তৃতীয়তঃ, বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করার সময় ও বিয়ের সময় সরদারকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হতো। সরদার ছাড়া বিয়ে চলতে পারে না। চতুর্থতঃ, মৃতের দাফন-জানাজা ইত্যাদি পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সময় সরদারকে উপস্থিত থাকতে হতো। সরদারের বহুমুখী দায়িত্বের মধ্যে প্রধান প্রধান এই কয়টির উল্লেখ করা গেল।
সাধারণতঃ ঈমানদার, ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মহল্লা পঞ্চায়েতের সরদার নির্বাচিত করা হতো। উত্তরাধিকার বিধি, সামাজিক রাজনীতি আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে সরদারকে ওয়াকিবহাল থাকতে হতো। পঞ্চায়েত তথা মহল্লার লোকদের উপর সরদারের প্রভাব থাকার ফলে সরদারের পদটা ক্রমে ক্রমে বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল। ফলে মাঝে মাঝে অসৎ, দুর্বলচেতা ও অকর্মণ্য লোক সরদার হয়ে দাঁড়াত। এ রকম অবস্থায় মহল্লার লোকদের পক্ষ থেকে সরদারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ও আপত্তি জোরদার হয়ে উঠলে বাইশ পঞ্চায়েতের সর্বাধিনায়ক নবাব বাহাদুর তাকে পদচ্যুত করে সরদারের পুনর্নির্বাচনের জন্য নির্দেশ দিতেন। সরদার নির্বাচিত হয়ে যাবার পর ‘নায়েব সরদার’-এর নির্বাচন হতো। নায়েব সরদার সরদারের অনুপস্থিতিতে সরদারের করণীয় কাজ সম্পন্ন করতেন।
প্রত্যেক মহল্লার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটা পঞ্চায়েতের ঘর বা বাংলা ঘর থাকত। পঞ্চায়েতের কাছারি ছাড়াও এই ঘর মহল্লাবাসীদের ক্লাব বা আড্ডার জায়গা হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। কোনো কোনো মহল্লায় এই কাছারি ঘরে মহল্লার ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



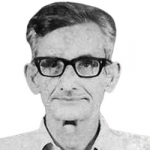
















Comments