ঢাকা শহরের নাচগান
পূজার নাটমণ্ডপগুলি নাচঘরে রূপান্তরিত হবার আগে পূজা উপলক্ষে যাত্রা, কবিগান, কীর্তন, কথকতা-এই সমস্তই চলত। নাচঘর নিয়ে এলো নতুন জিনিস-ঢপ, কীর্তন, খেমটা আর বাইজীদের নাচ-গান।
জীবন বাবুর বাড়ির নাচঘরের মালিক গোকুল রায়ের পিতা গৌরচন্দ্র রায় ঢপ, কীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন। ঢপ পূর্ববঙ্গের কোথাও প্রচলিত ছিল না। ঢপ কীর্তনের দল কলকাতা থেকে আমদানী করা হতো। সাধারণ কীর্তনের মতোই এই বিশেষ ধরনের কীর্তন বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদি ভূমি নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও কাটোয়ার মাটিতে জন্মলাভ করেছিল। ঢপ কীর্তনের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, মেয়েরা এই কীর্তন গান গাইত।
পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ করে কলকাতার নাগরিক আবহাওয়ায় খেমটা নাচ-গানের উৎপত্তি। কেউ কেউ মনে করেন সেখানকার হাফ আখড়াই গান ও ঝুমুর নাচের সংমিশ্রণে খেমটা নাচ-গান বিকাশ লাভ করে। পরে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকা শহরেও খেমটার দলগুলি গড়ে ওঠে। খেমটা নাচের সর্বনিম্ন ইউনিট দু’জনকে নিয়ে এক জোড়ার কমে খেমটা চলতে পারত না। লোকে উৎসবাদি উপলক্ষে ২ জোড়া, তিন জোড়া, ৪ জোড়া যার যেমন সামর্থ্য সেই হিসাবে বায়না দিত। সে সময় সারা ঢাকা শহরে সবশুদ্ধ কুড়ি-বাইশ জোড়া খেমটাওয়ালী ছিল। ওদের মধ্যে মিলন, সরফু, পারুল, প্রমদা, নাটকী, ছুট্কি, বীণা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, চারু, মলিনা, হরিমতি, প্রিয়া (পিয়া নামে পরিচিত) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ওদের নাম-যশ যে শুধু ঢাকা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয় সারা পূর্ব বঙ্গ, উত্তর বংগ, আসাম এবং বিশেষ করে চা-বাগান অঞ্চল থেকে এদের যথেষ্ট বায়না আসত।
এই দলগুলির মধ্যে একশ্রেণীর লোক ছিল, যারা ‘সফরদার’ নামে পরিচিত ছিল। তারা বাজনা বাজাত এবং খেমটাতে দালাল হিসাবেও কাজ করত। আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষার্থিনী খেমটাদের নাচগানও শিক্ষা দিত। খেমটার দলের বাদ্যযন্ত্র-হারমোনিয়াম ২টি। একটি দলে দু’জন করে কীর্তন-ওয়ালী থাকত। একজন প্রধানা, দ্বিতীয়জন তার সহকারী প্রধানা গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে-দ্বিতীয়া তার বদলী হিসাবে গান ধরত। দু’জনেই রাধা বেশে গান করত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কীর্তনীয়ারা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ঠাকুর, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট পদকর্তাদের বাছা বাছা পদ চয়ন করে বিভিন্ন পালাগান তৈরী করতেন। কীর্তনওয়ালীরা এই গুরুদের কাছে শিক্ষা নিয়ে এই পালাগানগুলি গাইতেন।
খেমটা
‘খেমটা’ শব্দটি হাল্কা ধরনের তালের নাম। খেমটা গান ও নাচ দুটিই ছিল আদিরসাত্মক, হাল্কা চটুল।
তানপুরার মত সুরের রক্ষক হিসাবে, অপরটি বাজনার জন্য, সাধারণ সারেঙ্গী ২টি, মন্দিরা, বায়া-তবলা ইত্যাদি। কলকাতা থেকে যারা আসত তারা সারেঙ্গীর বদলে ২টি বেহালা ও ক্লারিওনেট ব্যবহার করত।
স্থানীয় খেমটাদের জন্য জোড়া হিসাবে গুণানুসারে দৈনিক ৩৫ টাকা থেকে ৭০ টাকা দেওয়া হতো। কিন্তু যারা কলকাতা থেকে আসত তারা জোড়া হিসাবে দৈনিক ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পেত।
বাইজী
বাইজীদের নাচ-গানের রেওয়াজটা সম্ভবতঃ মোগলরা নিয়ে এসেছিল। বাইজীরা এককভাবে গান করত এবং এককভাবে নাচত। এদের গান ও নাচ, সংযত রুচিসম্পন্ন এবং খেমটাদের তুলনায় আভিজাত্য বোধের পরিচায়ক ছিল। বাইজী ও খেমটার নাচের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, তাদের নাচের মধ্যে পায়ের কাজটাই ছিল প্রধান এবং তার নৃত্যভঙ্গির মধ্য দিয়ে যৌন আবেদন সৃষ্টি করে তুলতে চাইত। অপরপক্ষে বাইজীর নাচে প্রধান ছিল হাতের দোলা ও মুখ, চোখ, নাক ও ওষ্ঠের সূক্ষ্ম কম্পন।
স্থানীয়ই হোক আর বাইরে থেকে আমদানী হোক, কোনো বাইজী বাংলা গান গাইত না। এখানকার আসরে এক ধরনের হিন্দী বা উর্দু গান গাওয়া হতো।
বাইজীদের নাচ-গানের সঙ্গে দুইটি বেনারসী সারেঙ্গী, বেনারসী তবলা, বেনারসী মন্দিরা ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। এগুলি আকারে সাধারণ সারেঙ্গী, তবলা ও মন্দিরার চেয়ে বড়। বাইজীরা যখন নাচত তখন যন্ত্রীরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজিয়ে চলত। খেমটা নাচের সময় যন্ত্রীরা এক জায়গায় বসে বাজনা বাজাত। বাইজীদের প্রচলিত পোশাক ছিল পেশওয়াজ, চুড়ীদার পাজামা ওড়না, পায়ে চিকন ঘুঙুর (খেমটাওয়ালীরা বড় ঘুঙুর পরত)। খেমটাদলের মতো বাইজীদের দলেও ‘সফরদার’ থাকত। তাদের পোশাক ছিল পাঞ্জাবী, ভেলভেটের ওয়েষ্ট কোট, মাথায় ভেলভেটের কিশতী টুপী।
এই নাচঘরগুলির আসরে যে সমস্ত বাইজী নাচ-গান করে গেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম:
স্থানীয় নওবান বাইজী, রাজলক্ষ্মী, জামুর্কির কুসুম, সরোজিনী, ইরি।
যারা খেমটা থেকে পরে বাইজী পর্যায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের মধ্যে এই তিন জনের নাম করা যেতে পারে: গোবিন্দ রাণী, দেবী, সীতা। কলকাতা ও ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে যে সমস্ত বাইজী বায়না নিয়ে এখানে মুজরা করতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে এই নামগুলি উল্লেখযোগ্য: গহরজান, নুরজাহান, মাল্কাজান, সিদ্ধেশ্বরী, জানকী বাই (ছাপ্পান ছুরী), জরদান বাই (সিনেমার নার্গিসের মা), কোহিনুর, ইন্দুবালা।
এই সমস্ত বাইরে থেকে আমদানী করা বাইজীর মুজরা গুণানুসারে দৈনিক ৫০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হতো। কিন্তু এদের বাবদ খরচের পালাটা এইখানেই শেষ নয়। এদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রী ও চাকরবাকর মিলিয়ে একটা দল আসত। তাদের খাদ্য পানীয় এবং আসা-যাওয়া-থাকার যাবতীয় ব্যয় নাচঘরের কর্তাদেরই বহন করতে হতো।
এখানকার মুসলিম ওস্তাদরা ও বসাক ওস্তাদরা শিক্ষার্থিনী স্থানীয় বাইজীদের নাচগানে ট্রেনিং দিত। খেমটারা ছিল ওদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ‘সফরদার’রা তাদের ট্রেনিং দিত।
ঢাকা শহরের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও প্রমোদজীবনে বাইজী ও খেমটাওয়ালীদের অবদানকে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া চলতে পারে না। কিন্তু এ যুগে আধুনিক দৃষ্টি নিয়ে তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। এদের অনেকের জীবনের পিছনেই করুণ ও মর্মান্তিক ইতিহাস জড়িত ছিল এবং এদের ব্যক্তিগত জীবনে হাসির চেয়ে অশ্রু ছিল বেশী। কিন্তু সত্যিকারের ছবিটা থাকত লোকনয়নের আড়ালে। এরা সবাইকে আনন্দ দিত, তাই নিয়েই সবাই খুশী, এদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা কেইবা জানে, কেইবা জানতে চায়! এদের দু-একজন সম্পর্কে দু একটু যা জানা গেছে, তা বলছি।
সীতা ছিলেন খেমটা দলের মেয়ে। পরে নিজের উদ্যোগ ও সাধনার ফলে তিনি বাঈজীর পর্যায়ে উন্নীত হন। নারায়ণগঞ্জ শহরের এক নিঃস্ব পরিবারে তার জন্ম। অভাবের দরুন তাঁকে কুমারী অবস্থায় এক নারীদেহ ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের এই সমাজে এভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে মেয়ে বিকিকিনি তখন চলত। যে লোক তাঁকে কিনেছিল সে আবার তাঁকে ওস্তাদ গৌর বসাকের কাছে বিক্রি করে দেয়। গৌর বসাক নামজাদা তবলচি ছিলেন। তাঁর পিতা পান্না বসাক পাখোয়াজ বাজনায় ওস্তাদ ছিলেন। গৌর বসাক সীতাকে নাচ-গান ও বাজনায় সুশিক্ষিত করে তোলেন। পরে সীতাকে বিয়ে করেছিলেন।
সীতা পরে অভিনেত্রীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে এই ঢাকা শহরেই তার হাতেখড়ি হয়। কোনো এক শখের থিয়েটারের দলের উদ্যোগে মানসী হলে (বর্তমানে নিশাত হল) ‘মেশিন ও মানুষ’ নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। সীতা এই উপলক্ষেই প্রথম অভিনয় করতে নেমেছিলেন। সীতা পরে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি নানা উপলক্ষে কলকাতার বিভিন্ন পাবলিক থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। বর্তমানে তিনি হিন্দী থিয়েটারে অভিনয় করছেন।
পল্লীবধূ সরোজিনী স্বামীর ও সমাজের নির্যাতনের ফলে বাঈজী বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার স্বামী গাঁজার নেশায় টং হয়ে হয়ে থাকত। আর ঘরে এসে বউর উপর অমানুষিক অত্যাচার করত। একদিন অনেক রাত্রিতে টলতে টলতে এসে তার উপর হুকুম জারী করল, গাঁজা সেজে দে। সরোজিনী সেদিন বিষম জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীর এই আদেশের উত্তরে তিনি বললেন, আমি জ্বরের জন্য মাথা তুলতে পারছি না, কেমন করে গাঁজা সাজাব! দুবার, তিনবার হুকুম করার পরেও কোনো ফল না হওয়ায় স্বামী অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে বলল, কি
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



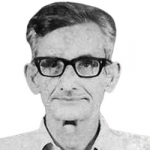
















Comments