দেওবন্দ শিক্ষা-কেন্দ্র
দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র ও আলীগড় শিক্ষা কেন্দ্র এই উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে বিশেষ পরিচিত। অবশ্য আজকালকার দিনের শিক্ষিত তরুণ মুসলমানেরা আলীগড়ের নাম যে ভাবে জানে দেওবন্দ এর নাম তেমন করে জানে না। হিন্দুদের পক্ষে এ কথা সত্য, আলীগড়ের কথা তারা অনেকেই জানে কিন্তু দেওবন্দের কথা খুব কম লোকেই জানে। অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র যে দেশপ্রেমিক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, সেজন্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছেই তা স্মরণীয় থাকা উচিত ছিল।
এই উপমহাদেশের সুদুর পল্লী অঞ্চলে মুসলমানদের কাছে একসময় আলীগড়ের চেয়েও দেওবন্দের নামই কিন্তু অনেক বেশী পরিচিত ছিল। এর প্রধান কারণ দেওবন্দ কেন্দ্র উলেমাদের দ্বারা পরিচালিত এবং এখানে প্রাচীন ধারায় ধর্মীয় শিক্ষার উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। অপর পক্ষে আলীগড়কে মুসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচারের পীঠস্থান বলা চলে। সেদিক দিয়ে এর একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।
কিন্তু আরও একটি কারণ আছে এবং সেই কারণটা একেবারেই তুচ্ছ নয়। আলীগড়ে অভিজাত ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান ছেলেরাই শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে কিন্তু দেওবন্দের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না। সারা দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ ঘরের শিক্ষার্থীদের জন্যও তার দ্বার অবারিত। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ছিল সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে এবং তাদের সাংসারিক জীবনের সুখ-দুখের সঙ্গে অব্যাহতভাবে তার সম্পর্ক রক্ষা করে এসেছে।
ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত এই শিক্ষা কেন্দ্রটির স্বরূপ বুঝাতে হলে তার অতীত দিনের ইতিহাসের সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরে আলীগড়ে তাঁর শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। দেওবন্দের শিক্ষা কেন্দ্র প্রায় একই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী ঐতিহ্য। এই সংগ্রামী প্রেরণার মূলে ছিলেন দিল্লীর শাহ-ওয়ালীউল্লাহ।
শাহ ওয়ালীউল্লাহের দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমটি ধর্মীয়: তিনি ইসলাম ধর্মকে পরবর্তীকালের নানারূপ কুসংস্কার ও আচার বিচারের জাল থেকে মুক্ত করে হযরত মহম্মদ (দঃ) প্রবর্তিত ধর্মের প্রাথমিক বিশুদ্ধতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি বৈষয়িক: ব্রিটিশের ভারত অধিকারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের যে সমস্ত সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে তিনি তার সমাধান করতে চেয়েছিলেন।
১৮০৩ সালে ইংরেজদের আক্রমণ দিল্লীর পতনের পর তাঁর পুত্র ও শিষ্য শাহ আবদুল আজীজের উপর এক গুরু দায়িত্ব এসে পড়ল। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতকে ‘দার উল হরব’ অর্থাৎ যুদ্ধরত দেশ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এই ফতোয়ায় সমস্ত মুসলমানদের উপর এই নির্দেশ দেওয়া হলো যে তারা হয় জেহাদ ঘোষণা করে এই দেশকে বিজেতা খ্রিষ্টানদের হাত থেকে মুক্ত করুক নয়ত এদেশ ত্যাগ করে যে-কোন স্বাধীন মুসলমানের দেশে চলে যাক। কিন্তু শুধু দেশত্যাগ করে গেলেই চলবে না, বাইরে থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে আবার তাদের ইংরেজদের হাত থেকে এই দেশকে মুক্ত করতে হবে। একমাত্র তখনই এই দেশে ‘দার-উল্-ইসলাম’ অর্থাৎ ‘শান্তির রাজ্য’ প্রতিষ্ঠিত হবে।
সেই নির্দেশকে মান্য করে উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য ও আত্মীয় স্বজনরাও এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বর্ণিত এই ‘ওয়াহবী’ দল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্গম বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলকে ঘাঁটি করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। তারা সেই সময় থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাঁচিয়ে রেখেছিল।
১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দলের কিছু কিছু লোক বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান করেছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেওয়ার পর জেহাদের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার সম্ভাবনা বহুদূরে পিছিয়ে গেল। উলেমাদের মধ্যে একটি দল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের যোগ দিয়েছিলেন। তারা উত্তর মজঃক্করনগর জেলার শামলীতে তাদের কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন। বিদ্রোহ ভেঙ্গে যাওয়ার পর তাঁরা কোনোমতে ইংরেজদের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে শাহারানপুর জেলার দেওবন্দে চলে এলেন এবং মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তৈরী করে দেওয়ার জন্য সেখানে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই উলেমাদের মধ্যে যে দুইজন তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের নাম মহম্মদ কাশিম নানাউতবী ও রশিদ আহমদ জানগোহী। এরা দুজনেই হাজী ইমাদউল্লাহর শিষ্য। হাজী ইমাদউল্লাহ ১৮৫৭ সালে দেশত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন।
১৮৬৭ সালে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে দেওবন্দের এ শিক্ষায়নটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল:
১. কোনো প্রভোলন, পৃষ্ঠপোষকতা, চাপ অথবা অনুগ্রহের বশবর্তী না হয়ে খোদার বাণীর মহিমা ঘোষণা করা,
২. ইসলামের মূল নীতিগুলির অনুসরণ করে জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তার করা,
৩. সরকার ও অভিজাতবর্গের সাথে কোনোরকম সহযোগিতা করে চলা এই শিক্ষায়তনের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিজনক, এই সত্য উপলব্ধি করা,
৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র উপদেশগুলিকে দৃঢ়ভাবে ও যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা,
৫. অভিজাতসূলভ ও স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিহার করা এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে গণতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করার উদ্দেশ্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কাজ করে চলা।
ইসলামের প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী এখানকার পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছিল। পাঠ্যসূচী, আর্থিক ব্যবস্থা ও প্রশাসনের দিক দিয়ে এই শিক্ষা কেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। ফলে যে সমস্ত শিক্ষার্থী এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে বেরিয়ে যেত, তাদের কোনরকম সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকতনা। এটা ছিল গরীবদের বিদ্যালয়, কাজেই এখানকার শিক্ষক ও ছাত্র সবাইকে অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে হতো। শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে উজ্জ্বলতর রাখাটাই ছিল এই শিক্ষা-কেন্দ্রের লক্ষ্য। পার্থিব সাফল্যের দিকে তাঁদের একেবারেই দৃষ্টি ছিলনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও আধিপত্য তাঁরা খুবই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের নৈতিক ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে তাঁরা এশিয়ার দেশগুলিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন।
যদিও এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাবিস্তার ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাহলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যগুলি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাজেই ভারতে ও ইসলামী জগতে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটত, সেগুলি স্বভাবতঃই তাদের মনকে নাড়া দিয়ে তুলত। ১৮৫৯-৬০ সালে নীলকর বিদ্রোহ ১৮৭৬ সালে দাক্ষিণাত্যের হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ এবং গ্রামের কৃষক ও কুটির শিল্পীদের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থার ফলাফল তাদের প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করতে হয়েছে। বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং বিশেষ করে ১৮৮৩ সালে এলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছিল। এই অসন্তোষ দিন দিনই বেড়ে চলছিল।
অপরদিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছিল তাতে সমগ্র ইসলামী জগতে নিদারুণ হতাশা ও বিক্ষোভের ভাব দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যেভাবে মিশর, তুরস্ক, পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ইত্যাদি মুসলমান দেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছিল, ভারতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সৈয়দ জামাল আলদীন আফগানি সে সময়ে এই সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করে ফিরছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি ভারতেও একটি বছর কাটিয়ে গেছেন। তার বক্তৃতার ফলে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মুসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রের কতৃপক্ষ এই সমস্ত প্রশ্নে জামাল আলদীন আফগানির সঙ্গে একমত ছিলেন। তাই ১৮৮৫ সালে নবগঠিত কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাল
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



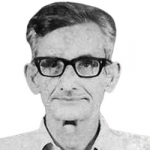

















Comments