ড. সাইফুদ্দিন কিচলু
পাঞ্জাবের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ড. সাইফুদ্দিন কিচলু ১৮৮৮ সালে অমৃতসর শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার কলেজ জীবন কেটেছিল আগ্রা ও আলীগড়ে। আলীগড় কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ইউরোপে যান। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ডিগ্রী এবং জার্মানী থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া তিনি লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।
১৯১৫ সালে ইউরোপ থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর তিনি অমৃতসর শহরে ব্যারিস্টার হিসেবে আইন-ব্যবসা শুরু করলেন। এই সময় তিনি শহরের বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে তিনি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন, তার ফলে তিনি অমৃতসর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
তার অক্লান্ত কর্মশক্তি শুধু মাত্র সমাজহিতকর কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। তারই সাথে সাথে তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপেও অংশগ্রহণ করে চলেছিলেন এবং পরে সেটাই তার প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। পাঞ্জাব প্রদেশে যাঁরা কংগ্রেসকে সংগঠিত করে তুলেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯১৯ সালে তিনি অমৃতসর শহরে কুখ্যাত ‘রাউলাট এ্যাক্ট’ এর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি করাচিতে এক মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দেশীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানী দিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে তিনি ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তিনি কিছুকালের জন্য দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রদেশের সভাপতি হিসেবেও কাজ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে লাহোরে ভারতীয় কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
তখনকার দিনে কিচলু বক্তা হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করে তুলত। এই কারণে তাঁর সম্পর্কে সরকারি কর্তৃপক্ষের মনে একটা আতঙ্কের ভাব ছিল। সেজন্যই যখন তাঁর রাজনৈতিক জীবন সবেমাত্র শুরু হয়েছে, সেই সময় বাংলার সরকার তার বাংলায় প্রবেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। ১৯১৯ সালে তাঁর উপর এই মর্মে এক নির্দেশ জারি হয়েছিল যে, তিনি কোনও জনসভায় বক্তৃতা দিতে পারবেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তাঁকে বহুবার জেল খাটতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের চৌদ্দটি বছর তিনি জেলখানাতেই কাটিয়েছিলেন।
গান্ধীজী কতৃর্ক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর দেশবাসীর মন হতাশা ও অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সময় ভারতে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে নানারূপ দুুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে এই চিন্তাটা পেয়ে বসে যে, দেশের সত্যিকারের কল্যাণ করতে হলে প্রথমে নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়াটা একান্ত প্রয়োজন। এই ধরনের চিন্তার ফলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ‘হিন্দু সংগঠন’-এর কার্যে তার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ রাজনীতির পথ থেকে দূরে সরে এসে শুদ্ধির কাজ নিয়ে মেতে গেলেন। ড. কিচলুর রাজনৈতিক জীবনেও এর অশুভ প্রভাব এসে ছায়াপাত করেছিল। তিনিও সাময়িকভাবে জাতীয় আন্দোলনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মুসলমানদের মধ্যে ‘তাঞ্জিম ও তাবলীগ’-এর ধর্মীয় আন্দোলনে মগ্ন হয়ে রইলেন। প্রায় দুই বছরকাল এই ধর্মীয় আন্দোলনের রাহুগ্রাস তাঁকে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।
সাময়িকভাবে বিচ্যুতি ঘটলেও ড. কিচলু শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কক্ষপথে ফিরে এসেছিলেন। যে সময় তিনি ‘তাঞ্জিম ও ‘তবলীগ’ এর ধর্মীয় আন্দোলনে মগ্ন হয়েছিলেন, তখনও তাঁর বিরুদ্ধে কেউ সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনতে পারেনি। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে কখনও তার বিচ্যুতি ঘটেনি। রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন চরমপন্থী। তার প্রায় প্রতিটি বক্তৃতাতেই তিনি স্পষ্টভাবেই এই অভিমত প্রকাশ করতেন যে, ভবিষ্যতে কৃষক ও শ্রমিকরাই হবে এদেশের প্রকৃত মালিক।
ড. কিচলু সব সময় এই অভিমত প্রকাশ করে এসেছেন যে, অর্থনৈতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলে এ দেশের উন্নতি কখনই হতে পারবেনা। লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে ভাষণ-দান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, “ব্রিটিশ সরকারের শাসনাধীনে কী পেয়েছি আমরা? পেয়েছি চরম দারিদ্র্য, বেকার জীবন, দুর্বহ ঋণের বোঝা, মহামারী, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, অনাহার আর মৃত্যুর অভিশাপ। বন্ধুগণ, আমাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি গৌণ, আমাদের মূল সমস্যা অর্থনৈতিক। কিন্তু এই অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন করতে হলে আমাদের ভাগ্যকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।”
ভারতের কোনও কোনও জাতীয়তাবাদী নেতা-স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন। কিন্তু ড. কিচলু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল এই যে, ভারতকে একান্তভাবে তার নিজের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তিনি বলতেন ‘‘পৃথিবীর অন্যান্য যে সমস্ত জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে, তা তাদের নিজেদের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে এবং আমরা এ পর্যন্ত রাজনৈতিক যে সমস্ত বিষয়ে লাভ করেছি, তাও আমাদের নিজেদের চেষ্টার ফল। আÍ-নির্ভরশীলতা, আÍবিসর্জন এবং দুঃখ দুর্দশাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়াই স্ব-রাজ লাভের একমাত্র পথ।”
গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই একথা বলতেন, ‘‘আমরা যখন এগিয়ে চলেছি তখন পিছনে হটে যাবার কোনো কথাই উঠতে পারে না। যতদিন আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছাতে না পারি ততদিন আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে, “এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!”
ড. কিচলূু কোনোদিনই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসেবে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ড. কিচলু এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন।
বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন চরম পর্যায়ে উঠেছিল। সে সময় ড. কিচলু দেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে দেশবিভাগের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে প্রচারের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বারবার এই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগের দেশ বিভাগের এই দাবীকে যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের কাছে আÍসমর্পণ করতে হবে। অবশ্য তাঁর এই চেষ্টার ফলে দেশ বিভাগকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। দেশ বিভাগের পর তিনি তার জন্মভূমি ভারতেই থেকে গিয়েছিলেন।
স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে নানাদিক দিয়েই তার মতভেদ ঘটেছিল। তার জীবনের শেষ কুড়িটি বছর তিনি সাম্যবাদের দর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ফলে কংগ্রেসের নেতারা তাঁকে আর তাঁদের আপনজন বলে মনে করতেন না। অবশেষে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার ফলে তিনি শীঘ্রই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে সু-পরিচিত হয়ে উঠলেন।
ড. কিচলু ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সোভিয়েত সরকার তাঁর প্রশংসনীয় কাজের জন্য তাঁকে সম্মানজনক পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছিলেন।
ছবি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাপ্রসূত
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



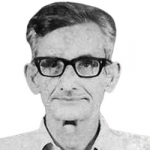
















Comments