কংগ্রেসে মুসলিম নেতৃত্ব
হাকিম আজমল খান
সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে হাকিম আজমল খানের নাম সুপরিচিত। তাঁর পূর্বপুরুষেরা মুগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে এদেশে চলে আসেন এবং তখন থেকেই ডা. আনসারীর মত হাকিম আজমল খানের পূর্বসূরীরাও চিকিৎসা বিদ্যায় সমগ্র উত্তর ভারতে অসামান্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পূর্বপুুরুষদের মধ্যে একজন সম্রাট আকবরের আমলে চিকিৎসাকে তার পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরই এক বংশধর ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজকীয় চিকিৎসক। তারপর থেকে তঁাঁদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ রাজ চিকিৎসক হিসাবে কাজ করে এসেছেন।
এই বিখ্যাত চিকিৎসক বংশের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন হাকিম আজমল খান। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালে। তাঁর পিতার নাম গোলাম মহম্মদ খান।
শিক্ষার দিক দিয়ে তিনি প্রাথমিক বাধ্যতামূলক কোরান অধ্যয়নের পর বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে প্রাচীন দিনের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করেছিলেন। নিজস্ব পেশা হিসেবে হাকিম আজমল খান প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত চিকিৎসা বিদ্যা অর্থাৎ তিব্বি ইউনানী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এজন্য তাঁকে বাইরে যেতে হয়নি, নিজেদের পরিবারের মধ্যে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনকার দিনের উচ্চ বংশের মুসলমানরা ধর্মভ্রষ্ট ও আচার ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কোনো আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাঠাতেন না। সেই কারণে তরুণ হাকিম আজমল খানকে আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি আধুনিক শিক্ষার মর্ম ও সার্থকতা বুঝতে পেরে একমাত্র নিজের চেষ্টাতেই ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।
চিকিৎসক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি রামপুর করদ রাজ্যের রাজকীয় চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। তরুণ হাকিম আজমল খান ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামপুরের নবাব তাঁর সঙ্গে সম্প্রীতি সূচক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে বিরত হননি। রামপুরে থাকতেই স্যার সৈয়দ আহমেদ কর্তৃক প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা তাঁর দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং তিনি আলীগড় কলেজের অন্যতম ট্রাস্টি হিসেবে মনোনীত হন। কিন্তু বিরোধটা দেখা দিল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। আলীগড় কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। কিন্তু হাকিম আজমল খান মনে প্রাণে আন্দোলনের সপক্ষে। ফলে তিনি আলীগড় কলেজের ট্রাস্টি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন।
যখন তাঁর বয়স ত্রিশের উপর, সেই সময় থেকে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। এই কাজ শুরু হলো লেখনী চালনার মধ্যে দিয়ে। তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে ‘আকমল উল-আকবর’ নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। হাকিম আজমল খান এই পত্রিকায় নানারকম রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ ও টীকা-টিপ্পনী লিখতেন।
বিংশ শতাব্দীর পদপাতের সাথে সাথে হাকিম আজমল খানদের পরিবারে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হলো। ইতিপূর্বে এই পরিবারের আর কেউ কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি। হাকিম আজমল খানই সর্বপ্রথম রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করলেন এবং দেখতে দেখতে তার নাম সারা ভারতের রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠল। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমভাগে তিনি একান্তভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়েই তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল বাস্তবিকপক্ষে এটা ছিল তার রাজনৈতিক শিক্ষানবিশীর কাল। কাজের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতির ফলে তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে সারা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করলেন।
তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি যখন মুসলিম রাজনীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন সে সময় ১৯০৬ সালে আগা খান এর নেতৃত্বে কয়েকজন অভিজাত শ্রেণীর বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোক ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজের স্ব-নির্বাচিত প্রতিনিধি স্বরূপ তাদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে দেন-দরবার করার উদ্দেশ্যে সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার আদায় করা এবং সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁরা বড়লাটের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলেন। হাকিম আজমল খান ছিলেন এই তথাকথিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। এই ১৯০৬ সালেই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। এই বছরই সরকারী প্রভুদের ইঙ্গিতে ভারতের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলমান ঢাকার নবাব বাড়িতে সম্মিলিত হয়ে মুসলিম লীগ গঠন করেন। আগা খানকে তাঁরা মুসলীম লীগের স্থায়ী সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। হাকিম আজমল খান এই সম্মেলনেও উদ্যোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন।
হাকিম আজমল খান ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সুপরিচিত হলেও তার কর্মবহুল জীবনের অন্যদিকটি সর্ম্পকেও অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। নানাবিধ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশীয় ‘তিব্বি ইউনানী’ চিকিৎসাবিদ্যার পুনরুদ্ধার ও উন্নতিকল্পে যে সমস্ত কাজ করে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। আধুনিক গবেষণা কার্যের সাহায্যে এই প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকে আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য তিনি যে অসামান্য সাধনা করে গেছেন, তা সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করেছে। এই উদ্দেশ্য তিনি তাদের পরিবার কর্তৃক পরিচালিত তিব্বিয়া স্কুলকে দিল্লীতে তিব্বিয়া কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কলেজে একটি গবেষণা বিভাগ ছিল, তাছাড়া এখানে ধাত্রীবিদ্যা (সরফরিভবৎু) শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। তিনি তার বহু বক্তৃতা ও লেখার মধ্য দিয়ে ধাত্রীবিদ্যাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য দেশের শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি আহব্বান জানিয়ে গেছেন। তিব্বি ইউনানী চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি কল্পে তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার জন্য ভারত সরকার ১৯০৭ সালে তাঁকে ‘হাজিক উল মুল্ক’ উপাধি দান করেন।
বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক দিয়ে হাকিম আজমল খানের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। মুসলিম লীগের সভ্য রাজভক্ত হাকিম আজমল খান সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামীতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এ এক বৈপ্লবিক রূপান্তর।
ভারত সরকার এতদিন পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ী হাকিম ও কবিরাজদের পেশাগতভাবে যে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন ১৯১০ সালে তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রস্তাব করলেন, ভারত সরকার ভারতের দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যাকে উচ্ছেদ করার জন্য মনস্থ করেছেন, একথা বুঝতে পেরে হাকিম আজমল খান সরকারের প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য দেশের হাকিম ও কবিরাজদের সংগঠিত করে চললেন।
ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর দিগন্তে এক নতূন যুদ্ধের কালোমেঘ দেখা দিল। ইতালি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম দেশ ত্রিপলী গ্রাস করে নিল। ব্রিটিশ সরকার উদাসীন দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটানাটিকে তাকিয়ে দেখল, এর বিরুদ্ধে তাদের কোনোই বক্তব্য ছিল না। ত্রিপলীর মুসলিম জনসাধারণের এই অসহায় অবস্থা দেখে ইতালির আক্রমণ এবং বৃটেনের অর্থপূর্ণ নীরবতার জন্য ভারতের মুসলমান বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠল। মুসলিম বিশ্বের শক্র এই ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে প্রতিহত করার জন্য ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন জাগরণ দেখা দিল। সেদিন হাকিম আজমল খানও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।
ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠল। এই যুদ্ধে তুরস্ক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানরা খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। তার কারণ এই যুদ্ধে এখান থেকে যে সমস্ত মুসলমান সৈন্যদের পাঠান হতো, তাদের নিজেদের ‘ধর্মীয় ভাই’ তুরস্কের মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছিল। এদিকে যুদ্ধের জরুরী পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মহম্মদ আলী প্রমুখ নেতাদের আটক করা হচ্ছিল। হাকিম আজমল খান অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের মতো এ পর্যন্ত ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ উদ্যোগের কাজে সাহায্য করে আসছিলেন, কিন্তু মুসলমান নেতাদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে তিনি বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে নিরস্ত হলেন।
১৯১৭ সালে তিনি গান্ধীজী ও অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে রাজভক্ত হাকিম
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



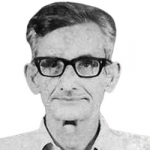
















Comments