সিন্ধু-সভ্যতার পরিচয়
যদি আপনার হাতে সময় থাকে আর মনে বাসনা থাকে তবে চলুন, সিন্ধসভ্যতার যুগে অর্থাৎ মোহেনজোদারো আর হরপ্পার যুগে এক চক্কর বেরিয়ে আসা যাক। যারা কিছু কিছু পড়াশোনা করেন, তাঁরা হয়তো বলবেন, এই বিষয়টা নিয়ে তো ইংরাজী আর বাংলায় যথেষ্ট লেখালেখি হয়ে গিয়েছে, আর কত? সেই একই পুরানো কাসুন্দি আর বেশী ঘেঁটে কি হবে? কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন, কাসুন্দিটা আরও একটু ভালো করে ঘাঁটা দরকার। এই নিয়ে অনেক কিছু জানবার ও চিন্তা করবার রয়েছে। এটা স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের এই উপমহাদেশের সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে যে প্রচলিত ধারণা চলে আসছিল, সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারের ফলে তার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে গেছে। নতূন করে ইতিহাস লিখতে হচ্ছে। কিন্তু সবে সূচনা। সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ সম্পর্কে যেটুকু জানা গেছে, তাতে বিশ্বের ইতিহাস বিজ্ঞানী ও ইতিহাস রসিকদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গেছে। কিন্তু এটাও অতি বড় সত্য যে, আমরা তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারিনি। সেই সমস্ত প্রকাশিত তথ্য আমাদের এই উপমহাদেশের সভ্যতার ইতিহাস রচনা করে তুলবার পক্ষে অপরিহার্য। প্রাচীন মিসর ও মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছি, তার কারণ এই দুই অঞ্চলেই প্রাচীন যুগের বহু লিখিত দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছে, যাদের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ছবিটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ওই ধরনের কোনো দলিলপত্র বা যে কোনো রকমের লেখার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তা হচ্ছে সীলমোহরের উপর ও মাটির পাত্রের উপর অংকিত কতকগুলো সাংকেতিক চিহ্ন। এই সাংকেতিক চিহ্নগুলোর অর্থভেদ করতে পারলে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য অবশ্যই পাওয়া যেতো। কিন্তু দেশ-বিদেশের পণ্ডিতরা বহু চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত তাদের অর্থভেদ করতে পারেননি।
সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য আহরণ করা হয়েছে, তাই নিয়েই কি আমাদের তুষ্ট থাকতে হবে? কোনো রকম দলিলপত্রের সন্ধান যখন পাওয়া গেলো না, তখন আর কি করেই বা ভরসা পাওয়া যায়? সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের মনে এরকম একটা নিশ্চল ধারণা রয়েছে। কিন্তু দলিলপত্র ইতিহাস রচনার একমাত্র উপাদান নয়। ইতিহাসের মাল-মসলা নানা রূপেই ছড়িয়ে পড়ে থাকে। একটা অতি সামান্য জিনিসের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হয়ে যেতে পারে। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারের পর থেকে অনুসন্ধানী পণ্ডিতরা এই নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তাঁরা যতই এগিয়ে চলেছেন, ততই নতুন নতুন পথের সন্ধান পাচ্ছেন।
পরবর্তী গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সভ্যতা শুধু মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ এলাকায় এই সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল। পাকিস্তানে মাকরান উপকুলের সুঞ্জাজেন দোর থেকে ভারতের গুজরাটের ক্যাম্বে উপসাগর পর্যন্ত এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে এদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। মোহেনজোদারো ও হরপ্পা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই সভ্যতার বাহন হয়ে যারা এ বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তো কোনো প্রবল শত্রুর আক্রমণে বা প্রকৃতির দুর্যোগের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানের কাজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার ফলে এই বিস্তারিত অঞ্চলে এই সভ্যতার কোনো নতুন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যাবে না, এমন কথা কেউ জোর করে বলতে পারে? ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এই সভ্যতার বাহকরা ভারতের উর্বর অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু শারীরিকভাবে ছড়িয়ে পড়তে না পারলেও মালপত্রের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য সূত্রে তাদের প্রভাব যে ছড়িয়ে পড়বে এটা বিচিত্র কিছু নয়। কোনো কোনো বিষয়ে তাদের প্রভাব যে সারা উপমহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটা কাল্পনিক কথা নয়, প্রামাণ্য বলে গৃহীত। এই উপমহাদেশে হিন্দুরা তাদের আরাধ্য পশুপতি শিবকে এদের কাছ থেকেই পেয়েছিল। ভারতীয় যোগসাধনার উৎসও এখানেই।
সিন্ধু-সভ্যতার ঐতিহাসিক উপাদান শুধু এই উপমহাদেশের মধ্যে সন্ধান করলেই চলবে না, তার জন্য বাইরের খোঁজ করতে হবে। এখানকার বণিকরা যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত, সেই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা এখানে তন্ন তন্ন করে খুজলেও মিলত না। খবরটা পাওয়া গেলো মেসোপোটেমিয়া থেকে। মেসোপোটেমিয়ার (ইরাক) খনন কার্যের ফলে অনেকগুলো সীলমোহর পাওয়া গেছে। এগুলোর সঙ্গে মোহেনজোদারো-হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহরগুলোর কোনোই প্রভেদ নেই। এই সীলমোহরগুলোর মধ্য দিয়েই এই অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্কের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য ধরা পড়েছে। মেসোপোটেমিয়ার উপকথা ও কাহিনিতে ‘তিলমুন’ দ্বীপের বিবরণ পাওয়া যায়। সেই ‘তিলমুন’ বর্তমানের পারস্য উপসাগরের বাহরিন দ্বীপ। মোহেনজোদারো ও হরপ্পার এতোগুলো সীলমোহর মেসোপোটেমিয়ার অঞ্চল বিশেষে পাওয়া গেলো, তারই বা তাৎপর্য কি? পণ্ডিতরা অনুমান করেন, মোহেনজোদারো হরপ্পার একদল বণিক বা তাদের প্রতিনিধিরা বাণিজ্যের সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে বাস করত। সে যুগে বণিকদের অপর দেশে এই ধরনের উপনিবেশ স্থাপনের রীতি অন্যত্রও লক্ষ করা যায়। আনাতোলিয়ার (বর্তমানে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত) খনি অঞ্চলে মেসোপোটেমিয়ার বণিকদের এই রকম একটি উপনিবেশ ছিল।
এই অঞ্চলের সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার যোগাযোগের আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাও এই সীলমোহরের মধ্যে। সুমের জাতির মধ্যে সুপ্রচলিত ‘গিলগামেশ’-এর কাহিনিতে ‘গিলগামেশ’ সিংহকে শ্বাসরোধ করে মারছেন, এই রকম একটি দৃশ্য আছে। আমাদের এখানকার সীলমোহরেও তারই অনুরূপ একটি ছবি অংকিত আছে। অবশ্য কিছুটা তফাৎ আছে। এখানকার ছবিতে সুমেরীয় গিলগামেশ-এর পরিবর্তে এখানকার স্থানীয় লোকের চেহারা এবং সিংহের পরিবর্তে বাঘ। কিন্তু এই ছবির উপরে যে সুমেরীয় প্রভাব রয়েছে তা দেখেই বোঝা যায়। শুধু এই নয়, আরও আছে। গিলগামেশ-এর সহচর আধা-ষাঁড় আধা-মানুষ ‘এনকিদু’ নামে একটি চরিত্র আছে। আমাদের এখানকার সীলমোহরে তার ছবি রয়েছে। এ থেকে মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কতদূর ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, সে কথাটাই পরিষ্কার হয়ে উঠে। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে শুধু যে মালপত্রের আদান-প্রদান হতো তা নয়, বণিকদের মারফত ওখানকার কাহিনি এখানে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। বাইবেলের সৃষ্টি-পর্বে যেই মহাপ্লাবনের কাহিনি আছে, সুমেরীয় কাহিনি ছিল তার মূলে। ইহুদীরা এই কাহিনি মেসোপোটেমিয়া থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিল। কহুকাল পরের সংস্কৃত গ্রন্থ বিষ্ণু পুরানে আমরা এই মহাপ্লাবনের কাহিনি দেখতে পাই। এর মূলও সুমেরীয় কাহিনির মধ্যে। গিলগামেশ-এর কাহিনির মতো এই মহা প্লাবনের কাহিনিও যে মোহেনজোদারো-হরপ্পার বণিকদের মারফত এদেশে এসে পৌঁছেছিল, এই সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক।
সিন্ধু-সভ্যতার ইতিহাসের মালমসলা খুঁজে খুঁজে বার করতে হলে যে সমস্ত দেশ বা যে সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক অথবা অন্য কোনো রকম যোগাযোগ ছিল সে সব জায়গাতেও অনুসন্ধান চালাতে হবে। কিন্তু কাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল, সে কথাটাই বা কেমন করে জানা যাবে? প্রথম দৃষ্টান্ত মেসোপোটেমিয়া। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা সুমের ও ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ থেকে এই যোগসূত্রের আবিষ্কার করলেন। কিন্তু ইরাকে খননযোগ্য বহু স্থান এখনও বাকী রয়ে গিয়েছে। কে জানে তার মাটির তলায় সিন্ধু সভ্যতার স্মৃতি-বিজড়িত আরও কিছু কিছু ঐতিহাসিক সম্পদ লুকিয়ে আছে কিনা। প্রাচীন তিল মুন অর্থাৎ বাহেরিন দ্বীপ সে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সুমের-ব্যাবিলোন-এর বণিকরা এবং মেলুহ্হার বণিকরা এখানে এসে একত্রিত হতো এবং এইখানেই তাদের জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হতো। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীদের কাছে আমাদের এই সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলটি ‘মেলুহ্হা’ নামে পরিচিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ সালের পর থেকে এই মেলুহ্হা সম্পর্কে আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই সময় মোহেনজোদারো আর হরপ্পা আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। মেলুহ্হা রপ্তানি মাল হিসেবে এখানে ময়ূর, গজদন্ত, গজদন্তজাত দ্রব্যাদি যথা চিরুনী, মুক্তা ও
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



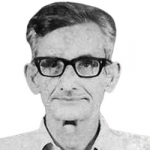

















Comments