প্রাচীন যুগের আদালত
‘প্রাচীন যুগের’ আদালতের ইতিহাসের কথা বলতে চলেছি, কিন্তু আপনাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটাই জাগা উচিত, এই ‘প্রাচীন যুগ’ বলতে কোন যুগটাকে বোঝায়? কথাটা এভাবে বললে ঠিক হয়, সভ্যতার প্রাথমিক যুগের আদালত। শিরোনামটা যেমন আছে তেমনি থাক, আপনারা এই অর্থেই বুঝে নেবেন। তা হলেই হবে।
কতকাল আগেকার কথা বলা হচ্ছে? মোটামুটি ধরে নিন খ্রিষ্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০) থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০) কাল পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে মিসর, সুমেরীয়া, ব্যাবিলন এই কটি দেশ এবং হিট্টীয় ও ইহুদী জাতির মধ্যে কি ধরনের আদালত ব্যবস্থা ছিল? এই সম্পর্কে যে সমস্ত দলিলপত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে যা বলার বলবো। তার বেশী আর কেমন করে বলা যাবে? এই প্রসঙ্গে আমাদের মোহেনজোদারো-হরপ্পার আদালত ব্যবস্থা সম্পর্কেও বলা দরকার ছিল। কিন্তু বলার উপায় নাই, কেননা তাঁরা কোনো দলিলপত্র রেখে যায়নি।
মিসরে বিচারক হিসাবে স্বতন্ত্র কোনো পেশা ছিল না। মিসররাজ ফারাও তাঁর দুজন মন্ত্রী নিয়ে সারা রাজ্যের তোষাখানা ও বিচার বিভাগকে পরিচালনা করতেন। বড় বড় শহরগুলির মেয়র বা শাসনকর্তা এবং ছোট ছোট কেন্দ্রের লেখক (Seribe) ও রেকর্ড রক্ষকরা প্রশাসন ও বিচার এই দুই বিভাগের কাজই করতেন। সারা রাজ্যে বড় আদালত ছিল দুটো, একটা থিবিস-এ আর একটা হেলিওপোলিস-এ। থিবিস-এর আদালতে দক্ষিণ অঞ্চলের মন্ত্রীর এবং হেলিওপোলিস-এর আদালত উত্তর অঞ্চলের মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় আদালত ছিল। শহরের বিশিষ্ট লোকেরা ও জেলার সরকারী কর্মচারীরা এই স্থানীয় আদালতগুলোতে বিচারে কাজ পরিচালনা করতেন। এদের মধ্যে পুরোহিতদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। মামলায় হারলে বড় আদালতে আপিল করা যেত। এই বড় আদালতে যারা হারত তাদের আপিল করতে হতো খোদ ফারাওর কাছে। এইখানেই চূড়ান্ত আপিল। কোনো গুরুতর মামলায়-যেমন যেখানে রাজপরিবারের লোকেরা জড়িত থাকতেন, সেই সব ক্ষেত্রে ফারাও একটি বিশেষ আদালত বসাতে পারতেন। এই বিশেষ আদালত আসামীদের আপিল করার অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন।
অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে লিখিতভাবে দরখাস্ত পেশ করতে হতো। আবেদনকারীর পক্ষ সমর্থন করবার মতো কোনো দলিলপত্র থাকলে তা এই দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করতে হতো। সে যুগে বিচারকের আদর্শটা কি রকম ছিল, উজির রেখমায়ার-এর নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে তা কিছুটা বুঝতে পারা যাবে। এখানে রেখমায়ার তাঁর নিজের উজির পদের দায়িত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করছেন: ‘খুব সাবধানে, তুমি যা কিছু করবে আইন অনুসারে করবে। লোকে উজিরের আচরণে সুবিচারের প্রত্যাশা করে থাকে। উজিরের প্রধান লেখক যে, তাকে বলা হয় ন্যায়ের লেখক। আর যেখানে বসে তুমি তোমার কাজ কর, তাকে বলা হয় ন্যায়ের ভবন। সকলের প্রতি যিনি সুবিচার করেন তিনিই হচ্ছেন উজির।’
এই তো গেলো আদর্শ। কিন্তু কার্যত আদালতের কাজ-কর্ম কি ভাবে চলত? সে সম্পর্কে অল্প কয়েকটি দলিল আমাদের হাতে এসেছে। তার প্রায় সবকটির মধ্যেই বিচার-ব্যবস্থার বীভৎস চিত্র পাওয়া যায়। ফৌজদারী মামলায় কেবলমাত্র দোষীদেরই যে অত্যাচার ও অঙ্গচ্ছেদ করা হতো তা নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্য কথা বলবার জন্য নির্দোষ সাক্ষীদের উপরেও নানারকম অত্যাচার চলত। কবরের ডাকাতির মামলায় একটা বিশেষ কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই মামলায় সাক্ষী হিসেবে যাদের উপস্থিত করা হয়েছিল, তাদের উপরে সন্দেহ থাক আর নাই থাক সত্য কথা বলবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের প্রত্যেককে প্রথমেই পায়ের তলায় বেত্রাঘাত করা হয়েছিল (সে যুগের অত্যাচারের একটা বিশেষ পদ্ধতি)। আর যাদের উপর সন্দেহ হতো, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই মামলাতেই সৈন্যদলের লেখক আঙ্গে ফেনামুনকে সাক্ষ্য দেবার জন্য নিয়ে আশা হলো। ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে ওরা তাকে জেরা করতে লাগল। প্রথমে তারা পায়ের তলায়, তারপর তার হাতের উপর বেত্রাঘাত করা হতে লাগল। তারপর মিথ্যা কথা বললে তার অঙ্গচ্ছেদ করা হবে এই হুমকি দিয়ে তাকে শপথ করানো হলো। তারা তাকে প্রশ্ন করল, ‘তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ওই সমস্ত জায়গায় কিভাবে গিয়েছিলে সে কথা বল।’ তার উত্তরে সে বললো, আমি যে দোষী, সে কথা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীকে ডেকে আনা হোক। এর পর আবার চলল জেরা। সে বলল, আমি কিছুই দেখিনি। এতো করেও ক্ষান্ত হলো না তারা, আবারও তাকে জেরা করবার জন্য গ্রেফতার করে হাজতে আটকে রাখল।
দেওয়ানী মামলায় চূড়ান্ত দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে রাজা আখনাটেন-এর আমলে শাসন কার্যের অব্যবস্থার ফলে আদালতে উৎকোচ দানের রেওয়াজ এমন ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তার ফলে জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আখনাটেন এর পর হোরেমহেব কঠিন হস্তে এই দুর্নীতি দমন করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, ‘যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও পুরোহিতদের দিয়ে বিচার-পরিষদ গঠন করা হয় তাদের মধ্যে কারু সম্পর্কে এমন কথা যদি শোনা যায় যে, তিনি ন্যায্য বিচারের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, তা হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে এতো কঠিন হস্তে শাসন করেও তিনি মিসরের বুক থেকে এই বিষাক্ত আগাছাকে দূর করতে পারেননি। আজকের বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য জগতে আমরাও এই বিষয়ে ভুক্তভোগী। সমাজে দুর্নীতি যখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে রোধ করা যে কি কঠিন ব্যাপার, আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে সে কথা আমরা মর্মে মর্মে অনুুুভব করছি। সেই জন্যই মিসরের জনসাধারণের সেদিনকার এই দুর্দশার কথা আমরা যেভাবে বুঝতে পারি, অন্যে তা পারবে না।
বিশেষ এক শ্রেণীর পুরোহিতকে বিচার কার্যে নিযুক্ত করা হতো। উরনগরীতে তৃতীয় রাজবংশের পতনের আগেই প্রাদেশিক আদালত গঠিত হয়েছিল। এই আদালতের প্রধান ছিলেন নগরের মেয়র। কয়েকজন বিশিষ্ট লোক তাকে এই কাজে সাহায্য করতেন, সেমিটিক জাতির লোকেরা যখন এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসল, তখন থেকে বিচার কার্যে পুরোহিতদের প্রাধান্য ক্রমেই কমে আসতে লাগল। হম্মুরাবির সময় ধর্মনিরপেক্ষ আদালত শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। ধর্মীয় আদালত এবং ধর্মনিরপেক্ষ আদালত দুটোই পাশাপাশি ছিল। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ আদালত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। বিচার কার্যে নিযুক্ত নগরের মেয়র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই কাজের জন্য বেতন পেতেন কিনা জানা যায় না, তবে তারা বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী হিসেবেই গণ্য হতেন। তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিচারের সময় বাদী বিবাদী উভয় যার যার লিখিত দলিল নিয়ে উপস্থিত থাকত। মামলা শুরু হলে প্রথম বাদী পক্ষ এবং তার পরে বিবাদী তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করত। সাক্ষীরা তাদের স্থানীয় দেবতা ও রাজার নামে শপথ নিয়ে সাক্ষ্য দিত। সাক্ষ্য দান শেষ হয়ে গেলে বিচারকরা তাদের রায় দিতেন। উভয় পক্ষেই উচ্চ আদালতে আপিল করার অধিকার ছিল। এই উচ্চ আদালতের নাম ছিল ‘ব্যাবিলনের বিচারপতিগণ’। এদের বিচারেও সন্তুষ্ট না হলে তারা স্বয়ং রাজার কাছে আপিল করতে পারতেন। সর্বক্ষেত্রেই যে ন্যায় বিচার ঘটত এমন নয়, কিন্তু মিসরে বিচারের নাম করে যে নিষ্ঠুর প্রহসন চলত, এখানকার সাহিত্যে বা দলিলপত্রে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।
এবার হিট্টীয়দের কথা বলি। এদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্যক্তিগত দলিলপত্র পাওয়া যায়নি বলে আমরা তাদের আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব কম কথাই জানতে পেরেছি। তবে তাদের বিচার ব্যবস্থা ব্যাবিলনের আদর্শে রচিত হয়েছিল, মোটামুটিভাবে একথা বলা চলে। প্রতিটি প্রাদেশিক কেন্দ্রে নগর মেয়র ও নগর প্রধানদের দিয়ে আদালত গঠন করা হতো। এই আদালতগুলোতে আমাদের আধুনিক পুলিস কোর্টের মতো ছোট ছোট মামলার বিচার হতো। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রাজার পক্ষ থেকে উচ্চপদস্থ সরকারী
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



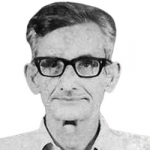

















Comments