১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ লোকের মুখে মুখে সিপাহী বিদ্রোহ নামে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এই নামটা আমরা পেয়েছিলাম ইংরেজদের কাছ থেকে। ব্র্রিটিশ সরকার এর নাম দিয়েছিলো Sepoy Mutiny অর্থাৎ সৈন্য বিদ্রোহ। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তাই মনে হবে বটে তার কারণ গোরা সিপাহীদের তুলনায় দেশীয় সিপাহীদের স্বল্পবেতন উর্ধ্বতন নাগরিক প্রভুদের দুর্ব্যবহার এবং নানা রকম অভাব-অভিযোগ সৈন্যদের মধ্যে দীর্ঘদীন ধরে অসন্তোষ সঞ্চিত করে তুলছিল। এই সমস্ত অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল বলে ১৭৬৪ সালে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সৈন্যদের মধ্যে এই জুলুম অবাধেই চলে আসছিল। ১৮৫৭ সালে দেশীয় সৈন্যরাই বিদ্রোহে প্রথম এবং প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত কারণে এই বিদ্রোহকে সৈন্যবিদ্রোহ বলে মনে করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদরা প্রথম দিকে এই শব্দটিকে ব্যবহার করে আসছিল। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণাটিকে সংশোধন করতে হয়েছিল।
এখানে এ সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদদের মন্তব্য তুলে ধরছি। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ডিজরেলি সর্বপ্রথম এই সত্যটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ২৭ শে জুলাই তারিখে পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি সুষ্পষ্টভাবে তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, একে সামরিক মিউটিনি বললে ভুল বলা হবে, এ হচ্ছে জাতীয় বিদ্রোহ। এরপর আ্যয়লামবুরি সভায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, “আমার বিশ্বাস এখন এ বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন ভারতের এই দুর্ভাগ্যজনক ও অসাধারণ ঘটনাটি সম্পর্কে প্রথমে যে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সমস্ত অবস্থা বিচার করে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। দিনের পর দিন আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ঘটনাটিকে প্রথম আমরা কতগুলি তুচ্ছ কারণের অথবা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট বলে মনে করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন এক জাতীয় ঘটনা যার ফলে ইতিহাসে যুগ পরিবর্তন ঘটে যায়। রাজনীতিবিদগণ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে, এর মূল কোথায় তা উপলব্ধি করতে পারবেন।”
এ প্রসঙ্গে হ্যসটিন ম্যাকারফি লিখেছিলেন, প্রকৃত ঘটানাটি হচেছ এই ভারতের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্যাপক এলাকা জুড়ে দেশীয় জাতিগুলো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এটাকে নিছক সামরিক মিউটিনি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে সৈন্যদের অসন্তোষ, ইংরেজদের প্রতি ঘৃণ্য মনোভাব এবং ধর্মান্ধতা, এই কারণগুলির সংমিশ্রণের ফলেই এই ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশীয় রাজ্য ও দেশীয় সৈন্যরা এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের নিজেদের বিরোধিতা ও বাদ-বিবাদের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে চার্লস বল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, “অবশেষে এই বন্যা প্রবাহ দুকূল ভাসিয়ে সমগ্র ভারতবাসীর জীবন প্লাবিত করে দিয়ে গেল। তখন আশঙ্কা করা গিয়েছিল, এই মহাপ্লাবনের ফলে এ দেশ থেকে ইউরোপিয়দের নাম নিশানা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন এটাও মনে হয়েছিল এই বিদ্রোহের বন্যা অবসানের পর যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে তখন দেশপ্রেমিক ভারত বিদেশী শাসকদের পরির্বতে কোনো এক দেশীয় রাজার আনুগত্য স্বীকার করবে।”
অথচ সেই সময়কার পরিস্থিতিতে এই ধরনের বিদ্রোহ সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না, এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। লর্ড ক্যানিং এদেশে বড়লাট হয়ে আসার প্রাক্কালে বিলাতে তাঁর বিদায়কালীন ভোজসভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলেছিলেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাজনৈতিক গগনে একখণ্ড ঘনক্লিষ্ট মেঘ দেখা দিয়েছে, কে জানে এ কোন দুর্যোগময় পরিণতি বয়ে নিয়ে আসবে!” ভারত থেকে বহুদূরে এসেও লর্ড ক্যানিং সেদিন ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। ডালহাউসি তার কলমের এক খোঁচায় প্রথমে অযোধ্যা রাজ্য, পরে একের পর এক দেশীয় রাজ্য গ্রাস করে চলেছিলেন, তার পক্ষে এটা একটু দুঃসাহসের কাজই হয়েছিল, কেননা এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে মারাত্মক দুর্যোগ দেখা দিতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন। এদেশে আবহমান কাল থেকে প্রজারা রাজাদের সঙ্গে রাজভক্তি ও আনুগত্যের সূত্রে বাধা। রাজমহিমায় আঘাত পড়লে এবং তাদের সম্পদ ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হলে সেই আঘাত তাদের বুকেও এসে বাজে। বিদেশী শাসকদের এই অতর্কিতে আক্রমণ তাদের মনেও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে তুলেছিল।
কিন্তু শুধু রাজভক্তি বা আনুগত্যের প্রশ্নই নয়, দেশের বহু সংখ্যক লোক এই সমস্ত রাজা ও ভূস্বামীদের অধীনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছে। সর্ব ব্যাপারে এদের উপরেই তাদের নির্ভর করে থাকতে হতো। এমন অনেক লোক ছিল যারা এদের অধীনে সৈনিক হিসাবে কাজ করে এসেছে। বংশানুক্রমে যুদ্ধবৃত্তিই ছিল তাদের পেশা, তাদের সামনে জীবিকা অর্জনের অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। এছাড়া ধর্মীয় নেতারা, শিক্ষাদাতা পণ্ডিত ও আলেমরা, পুরোহিত ও মোল্লা মৌলবীরা, লেখক, কবি ইত্যাদি জ্ঞানী-গুণী লোকেরা এবং কুশলী শিল্পীরা এই সমস্ত রাজা এবং ভূম্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।ঐ সমস্ত রাজা ও ভূস্বামীরা তাদের ভূসম্পদ ও ক্ষমতা থেকে বিচ্যূত হওয়ার ফলে তাদের উপর নির্ভরশীল এই সমস্ত লোকেরাও বেকার ও অসহায় হয়ে পড়ল। তাই বিদ্রোহের প্রবল স্রোতে এরাও আকৃষ্ট হয়ে চলে এসেছিল।
কিন্তু এই শেষ নয়, আরও কথা আছে। একটি প্রাচীন ধারাবাহিক সামন্ততান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্যবাদের কব্জার মধ্যে পড়লে যে অবস্থা হয় তার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে চলেছিল। ব্রিটিশের বাণিজ্য লিপ্সার মত্ত হস্তী এদেশের সনাতনপন্থী গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পদদলিত করে সবকিছু ভেঙ্গে তছনছ করে চলেছিল। যন্ত্রশিল্পে উন্নত ইংল্যান্ড থেকে অবাধে আমদানী করা মালের প্রতিযোগিতার সামনে এদেশের শান্তিপ্রিয় কুটিরশিল্পীরা কেমন করে দাঁড়াবে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বনিয়াদী কুটির শিল্পগুলি একের পর এক ধ্বসে পড়েছিল। ফলে দলে দলে লোক বেকার হয়ে পড়তে লাগল। এই জন্য যারা দায়ী সেই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ দিশাহারা এই দুর্ভাগারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে, তাতে আর বিচিত্র কি? বিদ্রোহের সম্ভাবনা ও ব্যাপকতা এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে।
সম্প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এই বিদ্রোহের চরিত্র কি? নামে সিপাহী বিদ্রোহ হলেও আমরা এতকাল একে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই জেনে এসেছি। ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস, এ সম্পর্কে মতানৈক্য ও বিতর্কটা দেখা দিল সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালে, ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে একদল একে ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ আখ্যা দিতে রাজী নন। তাদের মতে এটা দেশীয় রাজা ও ভূস্বামীদের হৃত সম্পদ ও অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা মাত্র। তাঁদের মতে ভারত তখনও একটি ‘নেশন’ বা জাতি হিসেবে গড়ে ওঠেনি, কাজেই তারা জাতীয়তার মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা বৃথা। এই বিদ্রোহে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নয়, তাদের নিজ নিজ প্রভুর অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্যেই সংগ্রাম করেছিল। কাজেই এই অবস্থায় এই বিদ্রোহকে কোনো মতেই জাতীয় সংগ্রাম বলা চলে না।
কালক্রমে সেই বিতর্কের অবসান হয়েছে, প্রশ্নটা কিন্তু অমিমাংসিত রয়ে গেছে। ভারত তখনও ‘নেশন’ অর্থাৎ জাতি হিসেবে গড়ে উঠেনি, সেকথা মেনে নিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের এক বিরাট অঞ্চলের এই ব্যাপক বিদ্রোহকে কি ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাম দেওয়া যেতে পারেনা? খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকাজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন, তখন ভারতের বিভিন্ন রাজারা যদি মিলিতভাবে তাকে প্রতিরোধ দিতেন, তাদের সেই সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দিলে কি ভুল বলা হতো? অনুরূপভাবে হিন্দু ও মুঘল যুগে বহিরাগত মুসলমান ও ব্রিটিশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



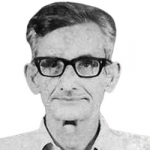
















Comments