মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ
বাড়ি? বাড়ি আমার বরিশার জেলার মূলাদি গ্রামে। মূলাদির নাম শোনেন নি?
হ্যাঁ, শুনেছি বৈ কি, উত্তর দিলাম আমি।
ছোটো বেলাতে সখ ছিল মিলিটারিতে যাব। শেষ পর্যন্ত সাংসারিক প্রয়োজনে সেই মিলিটারিতেই ঢুকতে হলো। সৈনিকের জীবনটা ভালোই লাগছিল আমার। বছর কয়েক পরে আমাকে স্পেশিয়াল ট্রেনিং-এর জন্য কোয়েটায় পাঠানো হয়েছিল। সেখানে আমি প্যারাট্রুপারের ট্রেনিং নিচ্ছিলাম। একটা শত্রু-অধিকৃত অপরিচিত এলাকায় কি করে ধ্বংস কার্য চালাতে হয় এই ট্রেনিং-এর মধ্য দিয়ে তারই শিক্ষা দেওয়া হয়। এ লাইনে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা বলেন, একজন দক্ষ প্যারাট্রুপার বহু অসাধ্য সাধন করতে পারে। কথাটা যে কত বড় সত্য, আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা বুঝতে পেরেছি। এই ট্রেনিংটা আমার মনের মতোই হয়েছিল। এবং খুবই দ্রুতগতিতে আমি এ বিদ্যাটা আয়ত্ত করে নিচ্ছিলাম। কিন্তু এই ট্রেনিং-যে একদিন মুক্তি-সংগ্রামের মতো মহৎ কাজে লেগে যাবে, সেটা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আজ আমি এজন্য নিজেকে বিশেষভাবে ভাগ্যবান বলে মনে করি।
মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ তাদের মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু দিয়ে দিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের এই বীরযোদ্ধা কিছুদিন হয় শত্রুদের গুলিতে আহত হয়ে বর্ডারের এপারে এক হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়েছেন। লোকের মুখে এই খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে গিয়েছিলাম, ইচ্ছা ছিল তাঁর নিজের মুখে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী শুনব। কিন্তু মনে মনে একটু ভয়ও ছিল। আমি অচেনা অজানা মানুষ, কে জানে হয়তো তিনি মন খুলে আমার সঙ্গে আলাপ করবেন না।
একটু দ্বিধা ও সংশয়ের ভাব নিয়েই আমার এক বন্ধু আর আমি হাসপাতালে তাঁর বেডের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক, বর্তমানে আমাকে বাধ্য হয়ে নিজের দেশের মাটির মায়া ছেড়ে বর্ডারের এপারে চলে আসতে হয়েছে। যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে তবে আপনার মুখে মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী শুনতে চাই।
আপত্তি! আপত্তি কেনো থাকবে? শিশুর মত সরল হাসি হেসে উঠলেন তিনি। আমরা এসব কথা দেশের লোকের কাছে শোনাতেই তো চাই। শোনাবার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি। তবে এখানে ঘরের মধ্যে বড্ড লোকের ভীড়। বাইরে চলুন, একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে আপনি যা শুনতে চান তা আপনাকে শোনাব। বলতে বলতে মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ উঠে দাঁড়ালেন।
অপরাহ্নের শেষ আলোয় তাঁর দীর্ঘ ছিপছিপে দেহটি একটি তীক্ষè তলোয়ারের মতো আমার চোখের সামনে ঝল্সে উঠল। সাধারণ বাঙালির মতো নয়, বরঞ্চ পাঞ্জাবীদের চেহারার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। গায়ের রঙ ফর্সা। চোখ, মুখ, নাক সবকিছুর মধ্যে একটা তীক্ষèতার ছাপ। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললেন, বয়সের পাকা হিসাবটা আমার জানা নেই তবে বছর তিরিশেক হবে। বাইরে একটা পছন্দ মতো জায়গা বেছে নিয়ে আমরা তিন জন বসে পড়লাম। আমাদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে চললেন। সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এমন প্রতিকূল পরিবেশে একটা মানুষের পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব? মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগছিল, নিজের বাহাদুরির কথা ফলাও করে প্রচার করবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে বলে চলেছেন না তো? কিন্তু পরে বিভিন্ন সূত্রে অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছিলাম আমার এ সন্দেহটা ঠিক নয়। তখন তাঁর সম্পর্কে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্য নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত বোধ করেছি।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হবার ঠিক অল্প কিছু কাল আগেই সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাঁর স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে তিনি যশোর ক্যান্টনমেন্টে বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলভুক্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে গর্জন করে উঠেছে। স্বাধীনতার এই দুর্বার কামনাকে দমন করবার জন্য সামরিক সরকার ২৫-এ মার্চ রাত্রিতে ঢাকা শহরের বুকে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রদেশময় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জনতা, দিকে দিকে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠতে লাগল।
যশোর ক্যান্টনমেন্টে তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক ব্যাটেলিয়ান বাঙালি সৈন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্টিয়ার ও বেলুচ বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যের মধ্যে তারা একেবারেই সংখ্যালঘু। তাই ভেতরে ভেতরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও তারা প্রথম দিকে কোনো অসন্তোষ বা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করে নি।
কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা তাদের বিশ্বাস করতে পারে নি। ২৯-এ মার্চ তারিখ পর্যন্ত মানুষের মনের অবস্থা যা’ই থাক না কেনো, যশোরের নাগরিক জীবন স্বাভাবিকভাবেই বয়ে চলেছিল। কিন্তু ৩০-এ মার্চ তারিখে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে অবাঙালি ও বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটল। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্ত্রাগারের চাবি কেড়ে নিয়ে সমস্ত বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করে ফেলল। তার মিনিট কয়েক পরেই বিক্ষুব্ধ বাঙালি সৈন্যরা মরীয়া হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং জোর করে তাদের নিজেদের অস্ত্রাগার দখল করে নিল।
এবার দু’পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সংখ্যা বাঙালিদের চেয়ে বহুগুণে বেশী। তা ছাড়া কামান মর্টার ইত্যাদি ভারী অস্ত্রশস্ত্র, সবকিছুই তাদের হাতে; ফলে এই যুদ্ধের পরিণতি যা ঘটা স্বাভাবিক তা’ই ঘটল। ঘণ্টাকয়েক ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। এই সংঘর্ষের ফলে ক্যান্টনমেন্টের দু-তিন শো বাঙালি সৈন্য মারা গেল। অবশিষ্ট বাঙালি সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে গেল। যশোর জেলার মুক্তিসংগ্রামের এইটাই হলো সূচনা।
এই পালিয়ে আসা বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না, যে যেদিকে পারল সে সেই দিকে পালালো। আবদুর রউফ আর তাঁর সাথী দুইজন সৈন্য তাদের সবার মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও তাঁরা তাদের মনোবল হারান নি। তাঁরা এই তিন জনে মিলে নিজেদের একটা ইউনিট গঠন করলেন এবং শপথ নিলেন যে, তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাবেন। এই সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা যশোর শহরে ফিরে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করলেন। তখন যশোর শহর মুক্তিবাহিনীর অধিকারে এসে গেছে। মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের পর থেকে আবদুর রউফ ও তাঁর দুইজন সাথী একই সঙ্গে লড়াই করে এসেছেন এবং আবদুর রউফ আহত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসার আগে পর্যন্ত তাঁরা এক সঙ্গেই ছিলেন।
৩রা এপ্রিল তারিখে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাক-সৈন্যরা যশোর শহর পুনর্দখল করে নিল। মুক্তিবাহিনী শহর ত্যাগ করে নড়াইলে গিয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করল। কিন্তু যশোর শহর ছেড়ে গেলেও মুক্তিবাহিনীর একটা অংশ শহর থেকে মাত্র মাইল দেড়েক দূরে দাইতলা ফতেহপুরে পাক-সৈন্যদের প্রতিরোধ দেবার জন্য তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের সঙ্গে ছিল তিনটা মেসিনগান। এই তিনটা মেসিনগানের মধ্যে একটা ছিল আবদুর রউফ আর তাঁর দুই জন সাথীর হাতে। ই. পি. আর. বাহিনীর ৮/১০ জন যোদ্ধা বাকী দুইটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এঁদের সাহায্য করবার জন্য জনা পঞ্চাশেক ছাত্রও তাদের সঙ্গে ছিল। এই প্রতিরোধের দলটি দাইতলার যেখানে ঘাঁটি করেছিল, সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল।
আবদুর রউফ বলছিলেন : ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত শত্রুপক্ষের কারও সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। ১২ই এপ্রিল তারিখে বেলা ১টার সময় আমরা যখন খেতে বসেছি, এমন সময় লক্ষ্য করলাম শহরের দিক থেকে একটা কাল রং-এর জিপ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু দূরে থাকতেই জিপটা থেমে গেল। মনে হলো, জিপের আরোহীরা আমাদের দেখতে পেয়েছে, তাই ওখানে থেমে গিয়েছে। আমরা দেখা মাত্রই খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। সাথে সাথে আমাদের তিনটা মেসিনগান একই
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



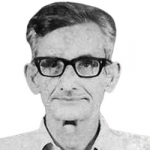
















Comments