নাচোল কৃষক বিদ্রোহ
দেশ বিভাগের পর মালদহ জেলার ৫টি থানা পূর্ববাংলার রাজশাহী জেলার সঙ্গে এসে যুক্ত হলো। এই পাঁচটি থানা, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নাচোল ও গোমস্তাপুর। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই নাচোল, নবাবগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি থানার আধিয়ার বর্গাচাষীদের মধ্যে যেই অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল তা আমাদের কাছে ‘নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত। এ যুগের তরুণ তরুণীদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে কোনো কথাই জানে না, কিন্তু সেদিন এই অভ্যুত্থানের কাহিনী উভয় বঙ্গের সর্বসাধারণের মধ্যে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে তুলেছিল।
নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে কোনো কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে গতশতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। ব্রিটিশ সরকার সাঁওতাল পরগণার বিক্ষুব্ধ সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিল।
নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ও তার মর্মান্তিক পরিণতি যেন তারই একটি ছোট সংস্করণ। এই অভ্যুত্থানের মধ্যে সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের কৃষকরা যুক্ত থাকলেও এটা ছিল প্রধানত সাঁওতাল কৃষকদের অভ্যুত্থান।
গত শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থতায় ভেঙ্গে যাওয়ার পর বিদ্রোহী সাঁওতালদের মধ্যে বহু লোক সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাদের জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবত সেই সময়ই তারা বাংলাদেশের মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। বহুদিন আগেকার কথা হলেও সেই বিদ্রোহের স্মৃতি তাদের মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি। বংশ পরম্পরাগত কাহিনী ও লোক সংগীতের মধ্য দিয়ে তা প্রবাহিত হয়ে আসছিল এবং অতি বড় দুঃসময়ে সেই স্মৃতি তাদের রক্তের মধ্যে ঝংকার জাগিয়ে তুলত। ১৯৩২ সালে মালদহ জেলার সাঁওতাল কৃষকরা স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য গঠনের জন্য যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তার মধ্য দিয়ে আমরা তার পরিচয় পাই।
এক সময় সাঁওতালরা তাদের আদি-জন্মভূমিতে স্বাধীন ভাবে বসবাস করত। যেই জমিকে তারা জন্মসূত্রে পেয়ে এসেছে, তারা জানত তারা নিজেরাই সেই জমির মালিক। সেই জমিতে মেহনত করে তারা যেই ফসল ফলাত, তারা নিজেরাই তা ভোগ করত, বাইরে থেকে আর কেউ এসে তার উপর ভাগ বসাতে পারত না। তারপর এক সময় কোথা থেকে নেমে এলো সরকার, জমিদার, জোতদার। যাদের হাতে কাগজপত্র, তারাই নাকি জমির মালিক। কিন্তু তাদের নিজেদের হাতে কোনো কাগজ নাই, তাই তাদের সব কিছু থেকেও কিছুই নাই। যদি জমি চাষ করতে হয়, তবে তাদের কাছ থেকে জমি নিতে হবে, আর ফসল ফললে তার একটা মোটা ভাগ তাদের গোলা-ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। এইটাই নাকি আইন। এই আইন না মানলে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তাড়িয়ে দেয়, ধরে বেঁধে জেলখানায় আটক করে রাখে, এমন কি খুন করেও ফেলে। এইটাই নাকি বিচার!
কিন্তু এ কেমন আইন? এ কেমন বিচার? বাইরে থেকে এলো যারা তাদের শান্তির সংসারের উপর হামলা করেছিল, জবরদস্তি করে তাদের উপর তাদের এই সমস্ত আইন চাপিয়ে দিয়েছিল, তাদের কথা তারা সহজে মেনে নেয় নি। এই নিয়ে মাঝে মাঝেই তাদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়েছে। কিন্তু ওদের শক্তি তাদের চেয়ে অনেক বেশী, ওরা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বন্দুক নিয়ে লড়াই করে, ওদের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠা যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পোষ-মানা হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু তা সত্বেও কখনও কখনও ভুল হয়ে যায়, আদিম রক্ত গর্জন করে ওঠে।
এখানকার তথাকথিত সভ্য জাতির মানুষেরা এই ‘অ-সভ্য’ সাঁওতাল আর তাদেরই মতো অন্যান্য সম্প্রদায়ের আদিবাসী লোকদের ভাগ্য নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেলে এসেছে! যে সব জায়গা নিবিড় বন-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, যেখানে বাঘ-ভালুক আর সাপ-ক্ষোপের ভয়ে কেউ প্রবেশ করতে চাইত না, জমিদার আর জোতদার নামে পরিচিত ভদ্র লোকেরা সেই সমস্ত জায়গায় এদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে নিয়ে আসত। আর এই সরল প্রাণ মানুষগুলি অনেক আশা বুকে নিয়ে আসত, জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলকে আবাদ করে সোনার ফসল ফলিয়ে তুলত। ‘কিন্তু বছর কয়েক’ বাদে তাদের জানিয়ে দেওয়া হতো, এই জমির উপর তাদের কোনো স্বত্ব নাই। তাদের হাতে তৈরী জমি দিয়ে আর তাদেরই মজুর খাটিয়ে সেই সমস্ত ভদ্র মানুষদের উপস্বত্ব দিন দিন বেড়ে চলে, আর এই হতভাগ্য ভূমিহারার দল একপেট ক্ষুধা নিয়ে মজুরী খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।
১৯৩০-৩২ সালে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্লাবন উথলে উঠেছে। মালদহ জেলার সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যেও সেই আন্দোলন সাড়া জাগিয়ে তুলল। তারা সঙ্কল্প করল, তারা স্বাধীন হবে, তাদের নিজেদের স্বাধীন রাজ্য গঠন করবে। স্বাধীন রাজ্য বলতে তারা বুঝেছিল, সেই রাজ্য তাদের জমির ক্ষুধা মিটবে, তাদের জমির উপর তাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, এর পর থেকে ভদ্র বেশধারী কোনো জমিদার, কোনো জোতদার, কোন মহাজন তাদের উপর কোনো রকম জুলুম আর শোষণ চালিয়ে যেতে পারবে না। জিতু সরদার ছিল তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। তার ডাকে মালদহের সাঁওতাল কৃষকরা দলে দলে লড়াই করবার জন্য এগিয়ে এলো। শহর থেকে আট মাইল দূরে আদিনা মসজিদের কাছে তারা তাদের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিল। অহিংস সংগ্রাম কাকে বলে, তা তারা জানতও না, বুঝতও না। সংগ্রাম বলতে একটা জিনিসই তারা জানত, যার নাম সশস্ত্র সংগ্রাম। আর এই সংগ্রাম করবার জন্য লাঠি, বল্লম, তীর-ধনুক ইত্যাদি হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে এসেছিল। অপরপক্ষে তাদের দমন করবার জন্য সরকারের পুলিশ বাহিনীও রাইফেল নিয়ে তৈরী হয়ে এলো। এই যুদ্ধের পরিণতি কি হতে পারে? যা হবার তাই হলো। এই সংঘর্ষে বহু সাঁওতাল মারা গিয়েছিল। তাদের সেদিনকার স্বাধীনতার সংগ্রামের এইখানেই হলো ইতি।
এ হলো ১৯৩২ সালের কথা। নাচোলের কৃষকদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। মাঝখানে ষোলটি বছর কেটে গেছে। কিন্তু নাচোল কৃষক বিদ্রাহের সংগ্রামী কৃষকরা ১৯৩২ সালের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা কি একেবারেই ভুলে গিয়েছিল? ভুলে যাওয়ার কথা নয়। এই দুইটি সংগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করবার মতো একজন লোক ছিলেন। তার নাম রামু সরকার। তিনি ১৯৩২ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামীদের মধ্যে একজন। জিতু সরকারের অন্যতম বিশিষ্ট সহকর্মী এই বৃদ্ধ রামু সরকার এবারকার এই বিদ্রোহে ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।
উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ীর মতো এই অঞ্চলেও বিরাট বিরাট জোতদারদের প্রাধান্য। জোতদারদের মধ্যে অধিকাংশই দু-চার হাজার বিঘার জমির মালিক। কৃষকদের হাতে জমি নাই বললেই চলে। এদের মধ্যে সবাই প্রায় ভাগ-চাষী। এরা শুধু নামেই কৃষক, জোতদারদের কাছ থেকে জমি না পেলে ক্ষেত মজুরী করা ছাড়া এদের আর কোনো উপায় ছিল না। ফলে জোতদারদের অনুগ্রহের উপর এদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো। জোতদার খুশী হলে জমি দিত, আবার যে কোনো সময় যে কোনো কারণে তাদের হাত থেকে এই জমি ছুটিয়ে নিতে পারত। শুধু সাঁওতাল কৃষকদের কথা বলছি না, হিন্দু ও মুসলমান ভাগচাষীদের অবস্থাও ছিল এই একই রকম। জোতদারদের বলতে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। ধর্মের দিক দিয়ে পৃথক হলেও শ্রেণী-চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই ছিল না। হিন্দু-মুসলমান সাঁওতাল নির্বিশেষে সকল ভাগ চাষীদের উপরেই তারা একই নির্মম শোষণের রাজত্ব চালিয়ে আসছিল।
অথচ এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ও এখানকার কৃষকরা এমনভাবে সর্বহারা হয়ে পড়ে নি। তখনও তাদের অনেকের হাতে নিজস্ব জমি ছিল। কোথায় গেল সেই সব জমি? এই অঞ্চলের কৃষকরা এখনও সে কথা ভুলে যায় নি। আজ যারা বৃদ্ধ তাদের মধ্যে অনেকে একসময়ে সুখের দিন দেখেছে। তখন তারা নিজেদের জমি নিজেরা
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



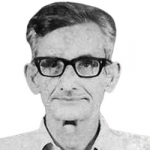

















Comments