রহমত আলী জাকারিয়া
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৪-১৫ সাল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পূর্ণ স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা শেষ পর্যন্ত সার্থকতায় পরিণত না হলেও সেই বিপুল কর্মোদ্যোগ ও আত্মত্যাগের জন্য আমরা গর্ববোধ করে থাকি। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা এই তিন মহাদেশে বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবের সৈনিকরা এই অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিল। সে এক উদ্দীপনাপূর্ণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ।
এই পরিকল্পিত বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলির মধ্যে দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল অন্যতম। দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বয়ং মাহমুদ আল হাসান এই কেন্দ্রের নেতৃত্ব করছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপ্লবীরা দেওবন্দের গোপন কেন্দ্রে এসে বিপ্লবের প্রস্ততি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতেন। মাহমুদ আল হাসানের আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর উপযুক্ত শিষ্য ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সরকারের শ্যেণ দৃষ্টি এড়িয়ে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অদ্ভুত কর্ম-তৎপরতার সঙ্গে গোপন সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়কার ঘটনাবলী ও বিপ্লবী-চরিত্রগুলি অধিকাংশই বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে গেছে। তা হলেও এই সমস্ত প্রদেশের তরুণদের মধ্যে এই উপলক্ষে যে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না।
লাহোরের যে ১৫ জন মুসলমান ছাত্র এই সংগ্রামে যোগ দেয়ার জন্য দেশত্যাগ করে আফগানিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন উপলক্ষে, তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীই তাদের মনে এই সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই ১৫ জন ছাত্রের মধ্যে কেবল কয়েকজনের নাম জানা গেছে।
১৯১৯ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রহমত করিম এলাহি জাকারিয়া নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাকারিয়া বা রহমত আলী নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। আবার ভারত সরকারের কাগজ-পত্রেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় জাকারিয়া বা রহমত আলী নামেই।
এই ১৫ জন ছাত্র যখন আফগানিস্তান যায় তখন সেখানকার আমীর ছিলেন হাবিবউল্লা। আমীর হাবিবউল্লাহ প্রথমদিকে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভুতির ভাব দেখালেও কার্যকালে বেঁকে বসলেন। ব্রিটিশ সরকারকে চটাবার মত শক্তি বা সাহস কোনটাই তাঁর ছিল না। ফলে এই ১৫ জন ছাত্র কাবুলে এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জেলখানায় আটক করে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এর বেশ কিছুকাল আগেই কাবুলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁকে জেলে আটক না করা হলেও নজরবন্দী অবস্থায় তাঁর দিন-যাপন করতে হচ্ছিল। ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে বার্লিন থেকে ইন্দো-জার্মান মিশন কাবুলে এসে পৌঁছাবার পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। এই ইন্দো-জার্মান মিশন জার্মানীর সম্রাট কাইজার এবং তুরস্কের ধর্মীয় নেতাদের শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে এসেছিল। সেই কারণেই আমির হাবিবউল্লা এই মিশনের অমর্যাদা করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। এই মিশনের ভারতীয় সভ্য রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের অনুরোধে সেই কারারুদ্ধ ১৫ জন মুসলমান ছাত্র শুধু যে মুক্তি পেলেন তাই নয়, তাদের নাকি রাজ-অতিথির মর্যাদাও দেওয়া হয়েছিল। ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীও স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও কাজকর্ম করার সুযোগ লাভ করলেন।
কিন্তু এই ১৫ জন ছাত্র অতঃপর কোথায় গেলেন, কি করলেন, তাদের জীবনের কি পরিণতিইবা ঘটল একমাত্র রহমত আলী জাকারিয়া ছাড়া, আর কারো সম্পর্কে কোনো কথাই জানতে পারা যায়নি।
জাকারিয়ার জন্ম ১৮৯৪ সালে, তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এটা পরিস্কার ভাবেই জানা গেছে যে তিনি কয়েক বছর বাদে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে কমিউনিজমের আদর্শকে গ্রহণ করেন। তিনি তার নবলব্ধ মতাদর্শের টানে কি করে ও ঠিক কবে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছেছিলেন তা জানা যায়নি এখনো। তবে এটা জানা গেছে যে, তিনি ১৯১৯ সালের ৯ই জুন তাসখন্দে তুর্কিস্থান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা করেছিলেন আর বক্তৃতার শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ তাকে অভিনন্দিত করেছিল ‘ভারত দীর্ঘজীবী হোক’ ধ্বনি তুলে। কিন্তু মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিতLenin Through the Eyes of the Worldসংকলনে প্রকাশিত তাঁর একটি লেনিন বিষয়ক পাদটিকা থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৯২০ সালেই কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন।
তারপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে তিনি ইরান প্রভৃতি নানা দেশে ঘুরেছেন। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যবিদ্যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন। উর্দুভাষায় ভারতবর্ষের কৃষকদের সম্পর্কে তাঁর বহু লেখাও নাকি প্রকাশিত হয়েছিল।
লেনিন সম্পর্কে লিখিত তাঁর একটি রচনায় এই ধরনের কথা ছিল: ‘‘এ কথা বলা চলে যে, লেনিনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এ সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করতেন। এইভাবেই তারা বিপ্লবের সমৃদ্ধতম ভাণ্ডার থেকে তাঁদের রসদ সংগ্রহ করতেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে লেনিনের যে ছবিটি আঁকা ছিল, তাঁরা এইভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন—“লেনিন গরীব মানুষের পক্ষে, লেনিন চান সকলেই সুখী হোক।”
১৯২৪ সালে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল মস্কোর ‘লেনিন প্রসঙ্গে প্রাচ্য প্রতীচ্যের রাজনীতিবিদ ও লেখকবৃন্দ’ নামক সংকলনে।
জাকারিয়া সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালের শেষদিক নাগাদ বার্লিন যান। কারণ ভারত সরকার ঐ সময় জার্মানীর যেসব ভারতীয় বিপ্লবীদের বহিস্কারের প্রশ্ন নিয়ে জার্মান সম্রাটের সঙ্গে চিঠি-পত্র লেখালেখি করছিলেন, তাদের তালিকায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চম্পক রমন পিল্লাই, প্রতিবাদী আচার্য ও মহম্মদ আলীর নামের সঙ্গে দেখা যায় তাঁরও নাম। পরের চিঠিপত্রে তাঁর নামের আর উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা চলে যে হয়ত পরে তিনি অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন বার্লিন ছেড়ে।
ভারতের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা গোপেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানা গেছে যে, বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশন্যাল গানের জাকারিয়াই নাকি উর্দু তর্জমা করেছিলেন। তার শেষ ক’লাইন হচ্ছে
ইয়ে জঙ্গ হামারি আখরি
ইস পর হ্যায় ফয়সালা।
সারে জাঁহা কি মজলুঁমো
উঠো কি বক্ত আয়া।
মুজফ্ফর আহমদ সাহেব তার পুর্বোল্লিখিত বইয়ে লিখেছেন জাকারিয়া নাকি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পান, মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের হিন্দু মুসলিম সমস্যা নিয়ে নিবন্ধ পেশ করে। কিন্তু জাকারিয়া এখন জীবিত আছেন কিনা জানা যায়না। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে তার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের। তখন তার খুবই দুঃস্থ অবস্থা। মুজফফ্র সাহেব লিখেছেন, “ফ্যাসিস্ট অধিকৃত ফরাসী দেশে ডক্টর রহমত আলী কি করছিলেন কোথায় ছিলেন তার কোনো খবর আমি জানি নে। তিনি ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন কিনা তাও আমরা জানিনে”। (আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি)
ড. দেবেন্দ্র কৌশিকেরCentral Asia in Modern Timesগ্রন্থের পাদটিকা থেকে জানা যায় যে ১৯৬৭ সালেও জাকারিয়া জীবিত ছিলেন এবং বাস করতেন প্যারিসে।
ছবি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাপ্রসূত
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



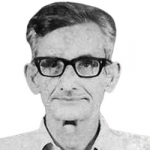
















Comments