স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাম্যবাদের কবি—কাজী নজরুল ইসলাম
যে কোনো মুক্তি আন্দোলন, গণ আন্দোলন বা শ্রেণী আন্দোলনের পেছনে তার অনুকূল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমি থাকলে তা উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে যে তার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে তা নয়। সময় সময় বর্হিজগতের আন্দোলনের তরঙ্গও তার উপরে এসে ঘা মারে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, ইতালী ও আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি আন্দোলন এবং সর্বশেষে রুশিয়ার সর্বহারা বিপ্লব, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলো।
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে সর্বভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তার প্রাথমিক প্রেরণা লাভ করেছিলো, এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই। বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী হয়ে উঠেছিলো, একথা অবশ্যই বলা চলে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ বহু কবির, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতায় নতুন ঊষালগ্নে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিলো।[১]
দ্বিতীয় অধ্যায়ে এক নতুন ও অভিনব ভূমিকা নিয়ে দেখা দিলেন চারণ কবি মুকুন্দদাস। তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচারের জন্য যে মাধ্যমটির সৃষ্টি করলেন তার নাম ‘মুকুন্দ দাশের যাত্রা’। প্রচলিত যাত্রাভিনয়ের মতই তা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে হাজার হাজার জনসাধারণের মনকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলো। কিন্তু প্রচলিত যাত্রাভিনয় থেকে তাঁর প্রয়োগ পদ্ধতি ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ তাঁর নিজস্ব আবিস্কার। মুকুন্দদাসের দল যে কোনো যাত্রাই অভিনয় করুন না কেন, মুকুন্দদাস নিজেই সেই অভিনয়ের কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী গান, মৃদু নৃত্যভঙ্গী এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ একটানা বক্তৃতা, এদের সবকিছুই শ্রোতা বা দর্শকদের আকর্ষণের মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াতো।
তৃতীয় অধ্যায়টি বিশেষভাবে কবি নজরুল ইসলামের অধ্যায়। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধূমকেতুর মতই নেমে এসেছিলেন। তাঁর এই আর্বিভাবের জন্য কেউ যেন প্রস্তুত ছিলোনা। রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর অসংখ্য গান, কবিতা ও গদ্যরচনা অজস্র ধারায় নেমে এসেছে। তাঁর নানা জাতীয় গানের মোট সংখ্যা তিন হাজার। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তিতে লিখিত রচনাগুলি এই প্রসঙ্গে আমাদের মূল আলোচ্য। তাঁর গানগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে তুলেছিলো। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা তাঁর ক্ষিপ্র, তীক্ষè হাতিয়ার রূপে কাজ করে এসেছে। তাদের সেই ভূমিকা আজও অব্যাহত আছে।
বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান। মুসলমান সমাজে কাজী পরিবার অভিজাত পরিবার বলেই গণ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অথবা সৌভাগ্যবশত অভাব অনটনক্লিষ্ট এক দরিদ্র পরিবারে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়েই তাঁকে বড় হয়ে উঠতে হয়েছিলো। তা না হলে তাঁকে বালক বয়সেই ‘লেটোর’ দলে গান গাইতে অথবা আসানসোলের রুটির দোকানে ছোকরা মজুরের কাজ করতে যেতে হতো না।
বাস্তব জীবনের এইরূপ কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি শোষিত মেহনতি মানুষের ব্যথা-বেদনা ও লাঞ্ছনাকে গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। আর এই অনুভূতির মধ্য দিয়েই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গানগুলি শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছিলো। এই গভীর আকর্ষণের ফলেই তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের ঘনিষ্ট সংস্পর্শের মধ্যে থেকেও মাটির মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেননি। যে কারণেই হোক তিনি স্কুলের দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র জীবন-যাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের সীমা শিক্ষায়তনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলোনা। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ইতিহাস তিনি সমানভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ফার্সী ভাষার উপরেও তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিলো। তাঁর বহু কবিতার মধ্যে এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।
সৈনিক জীবনে কাজী নজরুল ইসলাম
১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এই যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগ দেয়ার জন্য বহু তরুণ বাঙালীর মনে গভীর আগ্রহের ভাব দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনা ক্রমশই জাগ্রত হয়ে উঠেছিলো বলে ব্রিটিশ সরকার বাঙালিদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না। তবে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলার উপায় ছিলোনা। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে বাঙালিদের একটি স্বতন্ত্র রেজিমেন্ট গড়ে তুলতে হয়েছিলো।
নজরুল সৈন্য বিভাগে ভর্তি হলেন।[২]সে সময় বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে ডবল্ কোম্পানী নামে একটি কোম্পানী গঠন করা হয়েছিলো। নজরুলকে প্রথমে সামরিক শিক্ষা নেবার জন্য পেশোয়ারের নিকটবর্তী নৌশহরাতে পাঠানো হয়েছিলো। পরে এই ডবল্ কোম্পানীটিকে ৪৯ নম্বর রেজিমেন্টে পরিণত করা হয়েছিলো। তার সদর দফতর ছিলো করাচিতে।
নজরুল ও শৈলজানন্দ বালক বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চা করে আসছিলেন। করাচি সেনানিবাসে থাকার সময় নজরুল গল্প ও কবিতা রচনা করতেন এবং তা কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পাঠাতেন, সে সময় ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। কমরেড মুজফফর আহমেদের উপর এই পত্রিকাটি পরিচালনার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো। এই পত্রিকায় তাঁর ‘মুক্তি’ নামক কবিতাটি এবং ‘ব্যথার দান’ ও ‘হেনা’ এই দুটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিলো। সম্ভবতঃ এই তিনটিই তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা। এই তিনটি রচনা থেকেই লেখক হিসাবে তিনি যে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা বহন করছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তিনি ১৯১৮ সালে তাঁর প্রথম লেখাটি এই পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন।
যুদ্ধের পর ৪৯ নম্বর রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেবার সময় এসে গেল। ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’র পরিচালকরা বিশেষ করে তার মূল প্রাণশক্তি কমরেড মুজফফর আহমদ এ সর্ম্পকে সুনিশ্চিত ছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে নজরুল ইসলাম বাঙলার সাহিত্য গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে আবির্ভুক্ত হবেন। সেই কারণেই তাঁরা মনে করেছিলেন যে সৈনিক জীবন অবসানের পর নজরুল ইসলামের কলকাতায় এসেই থাকা উচিত। তদনুসারে তাঁকে চিঠি লেখা হয়েছিলো যে পল্টন ভেঙ্গে দেবার পর তিনি যেন সোজা কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি অফিসে এসে উঠেন।
তরুণ নজরুল সর্বপ্রথম কোন সময় এবং কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়না। তবে করাচি সেনানিবাসে বসে তিনি ‘ব্যথার দান’ নামে যে গল্পটি লিখেছিলেন তা থেকে আমরা এ কথা বুঝতে পারি যে, করাচিতে আসার পর অথবা তার আগে থেকে তিনি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন।
এ কথা সত্য স্বাধীনতার ভাবধারা সে যুগে যে কোনো রূপ নিয়েই হোক, ভারতের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তবে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে ও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাঁর ‘ব্যথার দান’ গল্পটি থেকে আমরা তা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি। সে সময় ব্রিটিশ সরকার এবং তার এজেন্টরা সোভিয়েত বিপ্লবের বিরুদ্ধে নানা-রূপ কল্পিত মিথ্যা কুৎসা রচনা করে চলেছিলো। তাদের আদর্শ এবং সেখানকার প্রকৃত তথ্যগুলি যাতে এদেশে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ভারতকে ঘিরে লৌহ বেষ্টনী (ওৎড়হ ঈঁৎঃধরহ) সৃষ্টি করে তোলা হয়েছিলো। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সেই লৌহ বেষ্টনীর রন্ধ্র-পথ দিয়ে কিছু কিছু সত্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছিলো।
করাচির সেনানিবাসের বাঙালী সৈনিকরা নানারূপ পত্র-পত্রিকা রাখতেন। কিন্তু এদেশে প্রকাশিত পত্রিকায় সোভিয়েত বিপ্লব সম্পর্কে কোনো সত্য সংবাদ প্রকাশের সুযোগ ছিলো না। সে জন্যই তাঁরা নানাভাবে সীমান্তের পরপারে সোভিয়েত এলাকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে কিছু কিছু প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতেন।
‘ব্যথার দান’ গল্পের উপর যে বাস্তব ঘটনাটির ছায়াপাত ঘটেছিলো এবার সেই কাহিনীটির বর্ণনা করছি। সেই ঘটনাটি ১৯১৮ সালে ঘটেছিলো। এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ ফৌজের
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



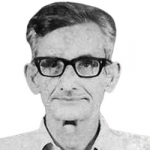

















Comments