আবদুল গফফার খান
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আবদুল গফফার খানের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। সেই কারণেই তিনি ভারতের সর্বত্র ‘সীমান্ত গান্ধী’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। শুধু ভারতেই নয়, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বীর দেশপ্রেমিকের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঠানদের হৃদয়রাজ্যের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র রাজা। এই দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় পাঠান জাতিকে তিনি কি করে কোন্ মন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অহিংস সংগ্রামের সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, দেশ বিদেশের লোকের মনে তা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল।
তাঁর জন্ম ১৮৯০ সালে, পেশোয়ার জেলার চরসদ্দার তহশীলের অন্তর্গত উৎমন্জাই গ্রামে। তিনি এক বিশিষ্ট ভূস্বামী খান-পরিবারের সন্তান। সীমান্ত প্রদেশের পাঠান জাতির এই সমস্ত খান বা সমাজপতিরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ অফিসারদের তাঁবেদারী করতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল। সরলমতি ও ধর্মান্ধ পাঠান জনসাধারণকে তারা নানাভাবে শাসন ও শোষণ করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করত। কিন্তু আবদুল গফফার খানের পরিবারের ঐতিহ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রিটিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। সমাজের লোকের কল্যাণের দিকে তাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁর পিতা বেহরাম খান অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক ছিলেন। প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকারের শুভেচ্ছা সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি তাঁর পুত্র গফফার খানকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা যুগিয়ে এসেছেন। আবদুল গফফার খান এই পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেন।
ভারতের সীমান্ত অঞ্চল হিসাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার চিরদিনই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বোধ করে এসেছেন। তাছাড়া এই প্রদেশ ছিল তাদের সৈন্যদের যোগানদার। সেজন্য পাঠান জাতি যাতে কোনো দিনই রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠতে না পারে, সে বিষয়ে তারা প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। এই কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও এই প্রদেশের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এখানে ওখানে দুটি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিক্ষা বিস্তারের কাজটা সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন। ফলে সমগ্র জাতি অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বোঝা বহন করে চলেছিল। ফলে তারা সামাজিক কু-সংস্কার, অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস ও নানাবিধ কুপ্রথার চিরন্তন শিকারে পরিণত হয়ে চলেছিল।
মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান পরিবারের সন্তান হিসাবে আবদুল গফফার খান আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। সারা উৎমন্জাই গ্রামে তাঁর বড় ভাই ডা: খান সাহেবই সর্বপ্রথম উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। তিনি লাহোর মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য লণ্ডনে গিয়ে পড়েছিলেন। বয়সে তিনি তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড়। আবদুল গফফার খান বাল্যজীবনে তাঁর মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ‘এডোয়ার্ড মিশন’ স্কুলে ভর্তি হলেন।
এডোয়ার্ড স্কুলের শিক্ষাজীবন তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই স্কুলে পড়ার সময় তিনি এখানকার অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড উইকরাম ও তাঁর ভাই ডা. উইকরাম-এর গভীর সংস্পর্শে আসেন। তাদের পশ্চাৎপদ পাঠান সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষার বিস্তারই যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পথ এই সত্যটা তিনি তাঁদের সাহায্যে প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পরে এই আদর্শই তার জীবনের দ্রুবতারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে কোনো কারণেই হোক দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েই তাঁর এখানকার শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর পর শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে আলীগড়ে পাঠান হয়। মাত্র বছর খানেক তিনি সেখানে ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য লণ্ডনে পাঠাতে চেয়েছিলেন। এজন্য বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মার তাতে ভীষণ আপত্তি। তার ফলে মাতৃভক্ত আবদুল গফফার খান তাঁর মার মুখের দিকে চেয়ে শেষ মুহূর্তে বিলেত যাওয়ার আকাক্সক্ষা ত্যাগ করলেন। এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্কে তুরস্ককে ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করতে হয়। ফলে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় জগতের কেন্দ্র খিলাফতের পতন ঘটল। তার ফলে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে দিয়েই খিলাফত আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারত থেকে হাজার হাজার মুসলমান দেশ ত্যাগ করে আফগানিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল এই সমস্ত মুসলিম শক্তির সাহায্য নিয়ে তারা ভারতের বুক থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করতে পারবে। এই আন্দোলন হিজরত আন্দোলন নামে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময় আবদুল গফফার খান রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে সচেতন ছিলেন। তাহলেও ধর্মীয় আন্দোলনের স্রোতের টানে তিনিও তাঁদের সঙ্গে দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল।
এই হিজরত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর দেশে ফিরে এসে নিরক্ষর পাঠান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এই উপলক্ষে তিনি সীমান্ত প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন এবং তাঁর উদ্যোগে প্রদেশের নানা স্থানে কতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্য দিয়েই তিনি সমগ্র প্রদেশের পাঠানদের মধ্যে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য একথা তিনি ভাবতেও পারেন নি যে এর মধ্য দিয়েই তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের প্রস্তুতি চলেছে।
ব্রিটিশ সরকারের এজেণ্টরা কিন্তু তাঁর এই শিক্ষা বিস্তারের অভিযানকে সুনজরে দেখতে পারেন নি। তাঁদের সন্দেহ ছিল যে এর মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তিনি যাতে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ পরিত্যাগ করেন, সেজন্য সরকার পক্ষ থেকে কঠোর ভাবে হুঁশিয়ারী দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি তাঁদের এই আপত্তিজনক প্রস্তাবে মাথা নোয়াতে রাজি হলেন না। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে এক মামলা আনা হলো। সীমান্ত প্রদেশের আইন ব্যবস্থা ছিল সারা দেশ থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বেচ্ছামূলক। সেখানকার বিচিত্র বিধানে এই অভিযোগে তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এইখান থেকেই শুরু হলো তাঁর দীর্ঘ কারাবাসের পালা।
এই দীর্ঘ কারা-জীবনে তাঁকে রাজ বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এ এক ভীষণ পরীক্ষা। তখনকার দিনের সাধারণ কয়েদীদের মত কঠিন ক্লেশভোগের মধ্য দিয়ে তাকে কারাবাসের দিনগুলি যাপন করতে হয়েছিল। অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের মতো তাঁর গলায় ঝুলত লোহার হাঁসলী, পায়ে বেড়ী। তাঁকে দিনরাত নির্জন সেলের মধ্যে আটক থাকতে হতো। সাধারণ কয়েদীদের মতো তাঁকেও দিনে ২০ সের করে গম ভাঙ্গতে হতো।
এই দীর্ঘ কারাবাসের পর তাঁকে পেশোয়ার জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো।
এ পর্যন্ত পাঠানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারের কাজই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত। কিন্তু সে কাজ শুরু করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, ব্রিটিশ সরকার সেই পথের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাধাকে অপসারিত করতে না পারলে পাঠান সমাজের সত্যিকার কল্যাণ সাধন কোনোমতেই সম্ভব নয়। এই কঠিন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার মনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার হয়ে উঠবে এটা খুবই স্বাভাবিক কথা।
১৯২১ সালে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে সারা ভারত টলমল করে উঠেছিল। সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরাও এই আন্দোলনের প্রভাব থেকে দূরে সরে থাকতে পারেনি। কিন্তু সংগঠনের দিক দিয়ে কি কংগ্রেস, কি খিলাফত কমিটি উভয়ই ছিল দুর্বল। এখানে প্রধানতঃ আবুদল গফফার খানকে কেন্দ্র করেই এই আন্দোলন গড়ে উঠল। আবদুল গফফার খান ৬ই এপ্রিল তারিখে তাঁর স্ব-গ্রাম উৎমনজাইতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসামাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঠিক এই সময় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আফগানিস্তানের যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। এই উপলক্ষে ভারত সরকার সমগ্র পেশোয়ার জেলায় সামরিক শাসনের ব্যবস্থা জারি করলেন। এই পরিস্থিতিতে আবদুল গফফার খানকে মর্দান জেলে নিয়ে আটক করে রাখা হলো।
ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



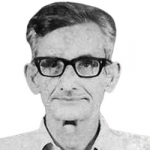

















Comments