কবি গানের দল
লোক মারফৎ নির্দেশ চলে এল। একটি চিঠি নিয়ে এসেছে ছেলেটি। চিঠির মধ্যে জরুরী নির্দেশ, আমাকে অবিলম্বে ১ নং ঢাকেশ্বরী মিলের কবির দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। শুধু বেরিয়ে পড়া নয়, সেই দলের নেতৃত্বও নাকি আমাকেই করতে হবে। একবার ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। কবি গানের সঙ্গে আমার কোনো কালেই তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। আর বেছে বেছে সেই দলের অধিকারী মনোনীত করা হয়েছে আমাকে! অতি বড় বীরপুরুষও অনুরূপ অবস্থায় আতঙ্কিত না হয়ে পারে না-আমি তো কোনো ছার।
১৯৪৬ সালের কথা। সাধারন নির্বাচন আসন্ন। তখন কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল না, অন্যান্য পার্টির মতো তারাও প্রকাশ্যে কাজ করবার অধিকারী ছিল। নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ও ঢাকা সদর মহকুমার কতকটা অংশ নিয়ে একটা নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ শহরের বিশিষ্ট জননেতা কমরেড ব্রজেন দাস সেই আসনে কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন একজন কংগ্রেসী। উভয় পক্ষের কর্মীরা নিজ নিজ প্রচার কার্য শুরু করে দিয়েছেন। ১নং ঢাকেশ্বরী মিলের এই কবির দলটি কমরেড ব্রজেন দাসের পক্ষে প্রচার অভিযানে যাত্রা করবে। তাদের প্রচার চলবে কবি গানের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন কেন্দ্রে এরা গান গেয়ে ফিরবে। আর তাদের পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে।
ভয় পেয়ে আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সেই আপত্তি টেকে নি। চিঠিতে বলা হয়েছে, সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই ব্যাপারে আমাকেই না কি যোগ্যতম পাত্র বলে বাছাই করা হয়েছে। ওদিকে নির্বাচনের সময় সন্নিকট। অতএব সমস্ত আপত্তি তাকে তুলে রেখে আমাকে অবিলম্বে আমার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা দিতে হবে।
দলটি যে পেশাদার কবির দল নয়, আশা করি সে কথা বুঝতে পারছেন। আবার একমাত্র নির্বাচনের প্রচারকার্য চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত একটি এড-হক কবি গানের দলও নয়। মিলের শ্রমিকরা নিজেদের উদ্যোগে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে দলটিকে গড়ে তুলেছিল। এদের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, এরা কখনোই সাধারণ কবি গানের দলের মতো পৌরানিক বা মামুলী বিষয় নিয়ে গান গাইত না। রাজনৈতিক ও সামাজিক, বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যাপার ও ঘটনাবলী ছিল এদের গানের বিষয়বস্তু। মালিক বনাম শ্রমিক, জমিদার বনাম কৃষক, জোতদার বনাম ভাগচাষী, কংগ্রেস বনাম কমিউনিষ্ট-এই ধরনের বিষয়গুলিই ছিল এদের কাছে সব চেয়ে বেশী প্রিয়।
শ্রোতাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। একই ধরনের গান এবং একই ধরনের যুক্তি ও প্রতিযুক্তি ক্রমাগত শুনে শুনেও তাদের শুনার তৃষ্ণা মিটতেই চাইত না। আর যাঁরা গান করতেন তাঁরা নানা জায়গা থেকে নতুন নতুন তথ্য, ঘটনা ও ভাব সংযোগ করে তাদের গানকে সমৃদ্ধতর করে তুলতেন।
এ সম্পর্কে কোনোই সন্দেহ নাই যে, এ বিষয়ে চট্টগ্রামের স্বনাম ধন্য কবিয়াল রমেশ শীল ছিলেন তাঁদের পথ প্রদর্শক। তাঁর কাছ থেকে অনুুপ্রেরণা পেয়েই এরা এদের এই রাজনৈতিক কবি গানের দলটিকে গড়ে তুলেছিলেন। এখানকার শ্রমিকরা কত দূর সচেতন হয়ে উঠেছিল, তা এই কবি গানের দল থেকে আর এই সমস্ত গান শুনবার জন্য সাধারণ শ্রমিকদের আগ্রহ থেকে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেত।
কবিগানের দলটা ছিল ১নং ঢাকেশ্বরী মিলে, কিন্তু ২নং ঢাকেশ্বরী, লক্ষ্মীনারায়ণ, চিত্তরঞ্জন-এই গান শুনবার জন্য ভিড় জমাতেন। এটি ছিল যেন তাদের সকলেরই সম্পত্তি, সকলেরই গর্ব ও আদরের জিনিস। মিলগুলো আলাদা হতে পারে, কিন্তু শ্রমিকরা ছিলেন এক মন, এক প্রাণ। তাদের সবাইকে নিয়ে যেন একটি বৃহৎ পরিবার গড়ে উঠেছিল। এই পরিবারের জঙ্গী মানুষগুলি এক সঙ্গে উঠত বসত, এক পথ ধরে চলত, আর একের বিপদে আর সবাই এসে বুক পেতে দাঁড়াত। আন্দোলনের বেলায়ও তাই, গানের বেলায়ও তাই। বিভিন্ন মিলে হিন্দু আর মুসলমান শ্রমিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা যে কোনো সাধারণ সমস্যার সামনে বজ্র-দৃঢ় ঐক্য নিয়ে দাঁড়াত। এই একতা মিল সমূহের কর্তৃপক্ষের হৃৎকম্প জাগিয়ে তুলত। বহু চেষ্টা করে তারা তাদের ইংরাজ প্রভুদের কাছ থেকে শেখা “ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি” অনুসারে নানা রকম কলা-কৌশল প্রয়োগ করেও তাদের এই একতার মধ্যে ফাটল ধরাতে পারে নি।
প্রসঙ্গ ছেড়ে একটু বাইরে চলে এসেছি। একটু প্রশ্রয় আমাকে দিতেই হবে। স্বচ্ছন্দ মনে গল্প বলতে বসলে মাত্রাজ্ঞান সব সময় ঠিক থাকতে চায় না। অতি সাধারণ এই সমস্ত মেহনতী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এই সমস্ত কাহিনী ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাবেন না। অন্তরের দরদ দিয়ে অভিষিক্ত করে পুরানো দিনের এই সব গল্প শোনাবার মতো লোকের বড় অভাব। যারা বলতে পারত, তাদের মধ্যে প্রায় সবাই মরে গেছে। দেশ ত্যাগ করে গেছে, হারিয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে।
মানুষের স্মৃতিশক্তি অমর নয়। যে সকল কাহিনী এক সময় অতি অন্তরঙ্গভাবে জানতাম, এমন কি যাদের মধ্যে আমার নিজেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, এখন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, সেগুলো রাত্রির আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে। কাহিনীগুলোর যোগসূত্র মাঝে মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না,-বিস্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে টুকরো টুকরো দুটো একটা ছবি ঝলসে উঠে। তাই গল্প বলতে বলতে মাঝে মাঝে আমাকে বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে এ পাশে ও পাশে পথ হাতড়ে হাতড়ে বেড়াতে হয়। আজকের দিনের উৎসুক শ্রোতা যারা, তারা যদি আমার সঙ্গে এই ছন্দ-ভাঙ্গা পথে চলতে রাজী থাকেন, তা হলে আমার গল্প বলার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।
এই কবি গানের দলÑআমি কেমন করে এদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লাম? আমার বন্ধুরাই বা এই দল পরিচালনার জন্য আমাকে মনোনীত করলেন কেন? একেবারে অকারণে নয় তো। আমি যদিও তখন ঢাকা শহরের অধিবাসী, তবু এই অঞ্চলের শ্রমিদের সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগের সূত্র ছিল। ট্রেড-ইউনিয়নের কর্মী হিসাবে নয়, জনসংস্কৃতির একজন সেবক হিসাবে। সেই হিসাবেই মাঝে মাঝে তাদের দেখবার, শুনবার এবং তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশবার কিছু কিছু সুযোগ পেতাম। সে জন্য আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম। এখনও তাই মনে করি। তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হতো, আমার মনের ধমনীতে ধমনীতে যেন নতুন রক্তের সঞ্চার শুরু হয়ে যেতো। আর যখন চলে আসতাম, তখন নতুন প্রেরণা নিয়ে নতুন মানুষ হয়ে ফিরে আসতাম।
সেদিন কাপড় কলের সেই আমলের একজন শ্রমিক, যিনি এখনও কাপড় কলেই কাজ করেন, দুঃখ করে বলছিলেন, সে সব দিন কোথায় গেল! এখন শ্রমিকদের ইউনিয়নও আছে, আন্দোলনও আছে, ধর্মঘটও আছে, সবই আছে, কিন্তু কি যেন নাই!
কি নাই? প্রশ্ন করলাম আমি।
কি নাই?-তিনি একটু সময় ভাবলেন, তারপর বললেন, দেখুন না, এখনকার এরা আমাদের সেই আমলের শ্রমিকদের মতো অমন দল বেঁধে আর প্রাণ খুলে গান গায় না। তখনকার দিনে একটু সচেতন যারা তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এমন কি এতো খাটুনির পর রাত জেগেও শ্রমিক আন্দোলন বা রাজনীতির বইপত্র পড়াশোনা করত। নেতারা নিয়মিতভাবে তাদের নিয়ে ‘ক্লাশ’ করতেন। রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা আর তর্ক-বির্তক লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটিও বেঁধে যেত। তখন সব কাজেই ‘জিয়ট’ ছিল, মানুষগুলো এমন ‘মেন্দামারা’ ছিল না। এখন সে সব কিছুই নাই। কি যে হয়ে গেল! দাদা, আপনি তো পুরানো দিনের মানুষ, সেই সময়কার অনেক কিছুই আপনি দেখেছেন। বলতে পারেন, এমন হলো কেন?
অনেক দিনের পুরানো মানুষ আমি-সব কথাই সত্য। কিন্তু এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব, সেই কথাই ভাবছিলাম। ইনি যে কথা বলছেন, তার একটুও মিথ্যা নয়। সে সময় শীতলক্ষ্যার এই
লগইন করুন? লগইন করুন
Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).



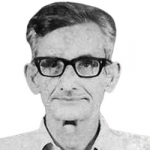
















Comments